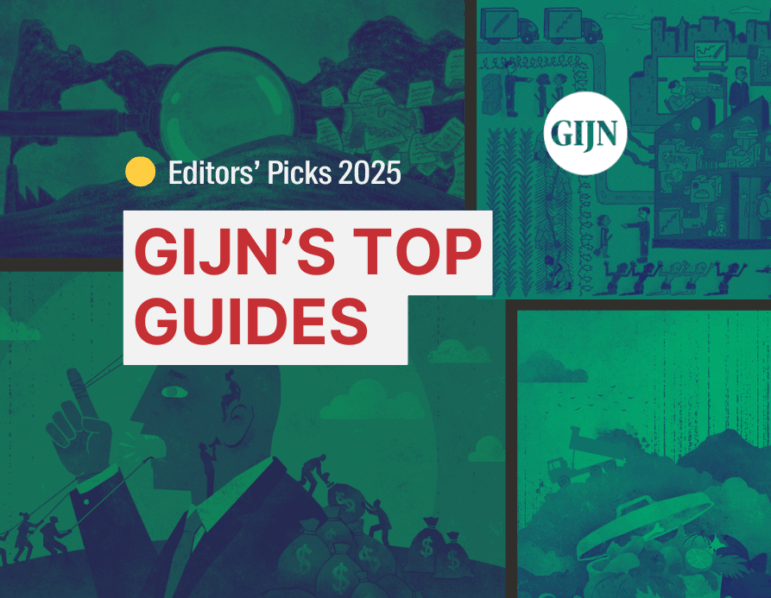অলংকরণ: মার্সেল লু
অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য নির্বাচন গাইড: ভোটের জন্য প্রস্তুতি
আর্টিকেলটি পড়ুন এই ভাষায়:
সম্পাদকের নোট: এই গাইডটি ২০২৪ সালের নির্বাচন ঘিরে পরিমার্জন ও হালনাগাদ করা হয়েছে। এটি মূলত ২০২২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। আগের সংস্করণের অধ্যায়টি এখানে পাবেন।
গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন দেশের অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা নির্বাচনের ঠিক আগেভাগে যার যার বার্তাকক্ষের হোয়াইটবোর্ডে কিছু শব্দ লিখে রাখছেন। যেমন প্রচারণা তহবিল জালিয়াতি, স্বজনপ্রীতি, স্বার্থের সংঘাত, ব্যালট বাক্সে জাল ভোট দেওয়া কিংবা ভুয়া দাবি।
তবে যখন জনতুষ্টিবাদী নেতা, দুর্নীতিগ্রস্ত মিত্র আর কট্টর-ডানপন্থী আন্দোলনের সহযোগীরা পরস্পরের কৌশল নকল করে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগের দুর্বলতাগুলোকে কাজে লাগায়—রাজনৈতিক সহিংসতা ও ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়—তখন অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের নজর রাখার মতো অগণতান্ত্রিক ঘটনার সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।
ভোট গ্রহণের মাসখানেক (বা এমনকি বছরখানেক) আগে থেকেই নির্বাচন বিটের সাংবাদিকদের উচিত বিদেশি প্রভাব বিস্তারের ঘটনা, জনসাধারনের ধারণাকে ভুল তথ্য দিয়ে প্রভাবিত করা (ডার্ক পিআর), ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া, ভুয়া ভাষণ তৈরি (ডিপফেক), ভোটার দমন আইন, কৃত্রিম জনসমর্থন , জিরো-ক্লিক নজরদারি, এবং রাষ্ট্রীয় মদদে চালানো মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর মতো বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিনিধিরা রাজনীতিবিদ বা সাংবাদিকদের ওপর গোপন নজরদারির তথ্য তাদের মিত্র গণমাধ্যমগুলোর কাছে পৌঁছে দেয়। সার্বিয়াতে যেমনটা ঘটেছে।
তাই নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসতে থাকে, সাংবাদিকদের উচিত কৌশলগত দুর্নীতির ঘটনা অনুসন্ধানের পরিবর্তে আরও পরিকল্পিত অনিয়মের দিকে মনোযোগ দেওয়া। যেমন: ভোটার জালিয়াতি ঠেকানোর নামে স্বেচ্ছাসেবীদের হস্তক্ষেপ, সাইবার আক্রমণের মাধ্যমে সার্ভার অচল করে দেওয়া, সামরিক বাহিনীর ভয়ভীতি প্রদর্শন, দলীয় স্বার্থে ভোটকেন্দ্র বন্ধ করে দেওয়া, নির্বাচনী কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস (ডক্সিং) কিংবা সোয়াটিংয়ের ঘটনা। (২০২৪ সালের নতুন নির্বাচনী হুমকি হলো সোয়াটিং। যেমন গুলি চালানো হয়েছে—এহেন ভুয়া বার্তা দিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের বাড়িতে বন্দুকধারী পুলিশ পাঠানো হয়। এ ধরনের ঘটনা মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করে এবং পত্রিকার পাতায় নেতিবাচক শিরোনামের জন্ম দেয়। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ও ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রে এভাবে ভুয়া তথ্য দিয়ে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তার বাড়িতে সশস্ত্র পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো আরও বাড়বে এবং ঝুঁকিপূর্ণ অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে দলীয় কর্মীরা এটি নকল করতে পারে।)
তাই প্রস্তুতি হিসেবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের উচিত নির্বাচন ঘিরে অনুসন্ধানের তালিকা বিস্তৃত করা, একই সঙ্গে নির্বাচনী প্রতিযোগিতার বিদ্যমান আইনগত সীমাবদ্ধতা এবং নিজেদের ও সোর্সদের নতুন ডিজিটাল হুমকি সম্পর্কে ধারণা রাখা।
জনগণের শাসনের অধিকার নির্ধারণের লক্ষ্যে জাতীয় নির্বাচনে হওয়া উচিৎ সুষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য প্রতিযোগিতা। যেন ভোটের মাধ্যমে ভোটারদের সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত হয়। তাই অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা খতিয়ে দেখেন—যেমনটা হওয়া উচিত এবং বাস্তবে যা ঘটছে তার মধ্যে ফারাক কোথায়, এবং জনগণের ইচ্ছাকে ব্যাহত করার প্রচেষ্টার পেছনে কারা রয়েছে। এই গাইডের ভূমিকায় যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে: অনেক স্বৈরাচারী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই দমনমূলক আইন ও হুমকি ব্যবহার করে প্রহসনমূলক নির্বাচন আয়োজন করে। এসব নির্বাচন নাগরিকদের ইচ্ছার প্রতিফলনের বিপরীতে মূল্যহীন হলেও, প্রচারণা ও অতিরিক্ত দমন-পীড়নের হাতিয়ার হিসেবে মারাত্মক বিপজ্জনক।
বিশেষজ্ঞরা বলেন, নির্বাচনী প্রচারণায় যা হওয়া উচিত এবং যা বাস্তবে ঘটে তার মধ্যে পার্থক্যগুলো অনুসন্ধানের প্রস্তুতি নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন নিয়ম-কানুন ও আইনগুলো সম্পর্কে জানা ও বোঝাপড়া তৈরি করা; নিজেকে, নিজের তথ্য এবং নিজের সোর্সকে নিরাপদ রাখতে কার্যকর কৌশল নেওয়া; এবং অনুসন্ধানকে উসকে দিতে পারে এমন প্রবণতা, সোর্স ও হুমকিগুলোর তালিকা প্রস্তুত করা।
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি ঝুঁকি হলো—বৈধ নাগরিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি অংশ ইচ্ছাকৃতভাবেই স্বৈরশাসক নেতাকে বেছে নিতে পারে। এতে ভবিষ্যৎ ভোটাররা গণতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ হারাতে পারে। যদিও ভোটার হিসেবে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া তাদের অধিকার। তাই সাংবাদিকদের দায়িত্ব হলো শক্ত প্রমাণ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য দিয়ে দেখানো যে স্বৈরতন্ত্র বেছে নেওয়ার ঝুঁকি কতটা ভয়াবহ। তাছাড়া এর ফলে সংবিধান, প্রতিষ্ঠান ও আইন কতটা দুর্বল হয়ে যেতে পারে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে দি অ্যাটলান্টিক তাদের পুরো সংখ্যাটি করেছিল ২৪ জন অভিজ্ঞ সাংবাদিকের গভীর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন দিয়ে। সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখানো হয়, আবার ক্ষমতায় এলে যুক্তরাষ্ট্রের সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে কী প্রভাব পড়তে পারে। এই ধরনের দূরদৃষ্টিমূলক প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরা যায় যে, গণতান্ত্রিক দেশে তথাকথিত নির্বাচিত স্বৈরশাসকেরা কীভাবে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরতে পারে। এবং আইন যতই ভালো উদ্দেশ্যে তৈরি হোক না কেন, দলীয় কর্মকর্তারা যদি নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন তবে তার পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সম্পাদকদের জন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের অগ্রাধিকার ঠিক করার সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গণতান্ত্রিক “সংকটবিন্দু” চিহ্নিত করা—অর্থাৎ যখন কোনো ক্ষমতাসীন দল বিরোধী মত সহ্য করতে চায় না, কিংবা বড় কোনো রাজনৈতিক দল একেবারেই নতুন ভোটারদের বোঝানোর চেষ্টা ছেড়ে দেয়। দ্বিতীয় অবস্থায় দলগুলো বরং প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সমর্থন ও ভোটাধিকার দমন করতে অনৈতিক বা বেআইনি কৌশল ব্যবহার করে, এবং নিজেদের ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করতে বিভ্রান্তিকর বা আতঙ্কজনক প্রচারণার আশ্রয় নেয়।
এমনটি সাধারণত তখন ঘটে, যখন কোনো রাজনৈতিক দল বুঝতে পারে যে তাদের নীতিগত অবস্থান জনসংখ্যার পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সঙ্গে আর তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। ভোট পরিচালনা যদি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের পরিবর্তে রাজনৈতিক দলগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাহলে এই “প্ররোচনা না করার কৌশলটি” আরও কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। (প্ররোচনা না করার কৌশল—এমন একটি রাজনৈতিক কৌশল যেখানে কোনো দল নতুন ভোটারদের দলে টানার জন্য ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে প্ররোচনা চালানো বন্ধ করে দেয়। বিপরীতে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার, ভয়ের বার্তা ছড়ানো বা জনগণের ভোটাধিকারের বিষয়গুলোকে জটিল করে তোলে।)
এই অধ্যায়ে আমরা তুলে ধরছি নিয়মকানুন ও প্রযুক্তিগত প্রবণতা—যেগুলো সাংবাদিকদের জানা প্রয়োজন, যেমন বিভিন্ন অঞ্চলে ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া কীভাবে বদলাচ্ছে এবং বিদেশি হস্তক্ষেপের প্রমাণ কীভাবে শনাক্ত করা যায়। পাশাপাশি আমরা নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ, দরকারি টুলস, এবং সাংবাদিকরা কীভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকা স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করা। আরও থাকছে স্বৈরশাসকেরা কীভাবে নির্বাচনে নিজেদের পক্ষে ফল আনতে ক্রমবর্ধমানভাবে অগণতান্ত্রিক কৌশল ব্যবহার করে, তার একটি তালিকাও।
ভিত্তি তৈরি করা
নিয়ম সম্পর্কে জানা
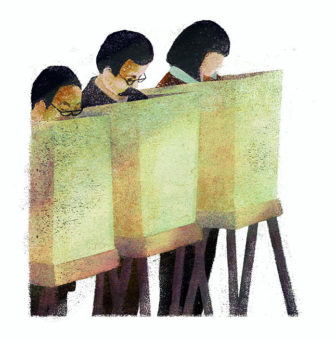
জিআইজেএনের জন্য এই অলংকরণটি করেছেন মার্সেল লু
যেসব দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, প্রায় অর্ধেকই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি ব্যবহার করে। এতে রাজনৈতিক দলের মোট ভোটের শতকরা হারের ভিত্তিতে সংসদের আসন বণ্টন করা হয়, ফলে ছোট দলগুলোরও নতুন আইন প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ থাকে। তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর প্রায় এক-চতুর্থাংশে উইনার-টেক-অল পদ্ধতি চালু রয়েছে—যেখানে একটি নির্বাচনী এলাকায় কেবল একজন প্রতিনিধি থাকেন এবং সর্বাধিক ভোট পাওয়া প্রার্থী নির্বাচিত হন। বাকি এক-চতুর্থাংশ দেশ এই দুটি মৌলিক পদ্ধতির সংমিশ্রণ অনুসরণ করে। (এই ডেটাবেসে বিভিন্ন সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা যাবে।) তবে উল্লেখ্য: কিছু দেশ দাবি করে যে তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির যে কোনো একটি অনুসরণ করে, কিন্তু বাস্তবে তারা প্রকাশ্যে প্রহসনের নির্বাচন আয়োজন করে, যেখানে আগে থেকেই ফলাফল সাজানো থাকে।
প্রতিটি নির্বাচনে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের এসব ভিন্ন নিয়ম ও ক্রমাগত পরিবর্তিত নিয়ম অনুসরণ করে কাজ করতে হয়। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দেওয়া হলো, যা স্থানীয় নির্বাচনী নিয়ম বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।
- প্রতিটি দেশের স্থানীয় নির্বাচন ব্যবস্থাপনা, সাংবিধানিক বিধান এবং নাগরিক সংগঠনগুলোর আইন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভালোভাবে জানুন। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র ও নির্বাচনী সহায়তা ইনস্টিটিউট (ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ) প্রণীত ও হালনাগাদ করা ইলেকটোরাল সিস্টেম ডিজাইন ডেটাবেস ওয়েবসাইটটিও দেখুন। এই প্ল্যাটফর্মে ২১৭টি দেশ ও অঞ্চলের নির্বাচনী কাঠামো সম্পর্কিত বিস্তারিত ও তুলনামূলক তথ্য পাওয়া যায়।
- এসিই ইলেকটোরাল নলেজ নেটওয়ার্ক ২০০টিরও বেশি দেশ থেকে নির্বাচনী তথ্য সংগ্রহ করে, যেখানে ভোটগ্রহণ সম্পর্কিত ১১টি বিষয়ের ওপর তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- দেশভিত্তিক নির্বাচন বিষয়ক হ্যান্ডবুক ব্যবহার করুন। যেমন: নাইজেরিয়ার জন্য তৈরি ডেটাফাইট হ্যান্ডবুক অন ডেটা-ড্রিভেন ইলেকশন রিপোর্টিং, অথবা জিম্বাবুয়ে মিডিয়া কমিশন প্রকাশিত জিম্বাবুয়ের নির্বাচন কাভারেজের নতুন নির্দেশিকা। নির্বাচনী প্রচারণা কভার করতে আসা আফ্রিকার নতুন তরুণ সাংবাদিকদের জন্য জ্যামল্যাব-এর সাধারণ টিপসশিটও সহায়ক হতে পারে।
- ওপেন ইলেকশন ডেটা ইনিশিয়েটিভ নির্বাচন প্রক্রিয়ার কার্যপ্রণালী বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে এবং লাতিন আমেরিকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী তহবিল সংক্রান্ত কেস স্টাডিও তুলে ধরে। আপনার এলাকার নির্বাচনী প্রক্রিয়াগুলো যেসব নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হওয়ার কথা, সেসবের সর্বশেষ তথ্য জানতে স্থানীয় একাডেমিক, গণতন্ত্র-পন্থী এনজিও, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থাগুলোর—যেমন এখানে উল্লেখিত ২৫১টি সংস্থা—সঙ্গে যোগাযোগ করে হালনাগাদ লিংক সংগ্রহ করুন।
- আসন্ন নির্বাচনে ব্যবহৃত ভোটিং সরঞ্জাম ও সেগুলো সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জেনে নিন। ভেরিফায়েড ভোটিং নামের অলাভজনক সংস্থার তৈরি দ্য ভেরিফায়ার ডেটাবেস মূলত যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হলেও এটি সহজে অনুসন্ধানযোগ্য একটি টুল, যেখানে ভোটের জন্য ব্যবহৃত বাণিজ্যিক ব্যালট-মার্কিং ডিভাইস, ইন্টারনেট ভোটিং সিস্টেম, অপটিক্যাল স্ক্যানার, এবং ইলেকট্রনিক ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অসংখ্য বিস্তারিত তথ্য রয়েছে—যার অনেকগুলোই অন্যান্য দেশেও নির্বাচনে ব্যবহৃত হয়।
- গুরুত্বপূর্ণ সব নির্বাচনগুলোর ইতিহাস সম্পর্কে জানুন। এই অসাধারণ বৈশ্বিক ভোটার টার্নআউট ডেটাবেস থেকে আপনার দেশের ভোটাদের অংশগ্রহণের ইতিহাস খুঁজে দেখুন। স্থানীয় নির্বাচন কমিশনের আর্কাইভ এবং লেক্সিসনেক্সিস-এর মতো গণমাধ্যম গবেষণা টুলের পাশাপাশি বেসরকারিভাবে সংকলিত অ্যাডাম কার’স ইলেকশন আর্কাইভ-ও দেখতে পারেন। যদিও এখানে সবকিছু নেই, তবুও এতে বৈশ্বিক নির্বাচনের ফলাফল ও পরিসংখ্যান মানচিত্রসহ একত্রিত করা হয়েছে এবং কিছু ঐতিহাসিক তথ্য সংরক্ষিত রয়েছে যা অনেক সময় নির্বাচনী সংস্থার ওয়েবসাইট থেকে মুছে ফেলা হয়।
সরকারি প্রতিনিধিদের সম্পর্কে জানুন
- আন্তর্জাতিক আইডিইএ-এর ইলেকটোরাল ম্যানেজমেন্ট ডিজাইন ডেটাবেস-এর মতো সাইটে নির্বাচন পরিচালকদের ক্ষমতা এবং কার্যাবলী সম্পর্কে দেখুন। এতে নির্বাচন সংস্থা ও কমিশন, দায়িত্বকাল, নির্বাচন কর্মকর্তা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত অনুসন্ধানযোগ্য তথ্য থাকে।
- নির্বাচনের শুরুর দিকে কিছু সময় ব্যয় করুন দুই থেকে তিনজন মূল নির্বাচনী কর্মকর্তার সঙ্গে পরিচিত হতে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে এবং ফোন নম্বর বিনিময় করতে। রাজনৈতিক বিটের অভিজ্ঞ প্রতিবেদকরা বলেন, নির্বাচনের সক্রিয় ভোট গ্রহণের সময়ে নির্বাচন কর্মকর্তারা অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। যদি তারা আপনাকে আগে থেকে না চেনেন তাহলে তাদের কাছে পৌঁছানো কঠিন। এছাড়া, এই ব্যক্তিরাই নিয়ম ও সমস্যাগুলো বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে কাজ করবেন।
- নির্বাচনী কর্মকর্তাদের জন্য টুইটার/এক্স অ্যাকাউন্ট লিস্ট তৈরি করুন। আমেরিকার ৫০টি রাজ্যের মধ্যে ৪৭টি রাজ্যের সচিবদের টুইটার ফিডের হালনাগাদ তালিকা সংকলন করেছেন ফার্স্ট ড্রাফটের প্রতিবেদক ডায়ারা টাউনস, যারা ওই রাজ্যগুলোর প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। এই রিসোর্স ব্যবহার করে প্রতিবেদকরা এই কর্মকর্তাদের তৎকালীন উদ্বেগ ও সিদ্ধান্তগুলো দেখতে পারেন। বিশেষজ্ঞরা আরও সুপারিশ করেন, ভালো রাজনৈতিক প্রতিবেদকদের—বিশেষ করে দূরবর্তী প্রদেশ বা রাজ্যের—টুইটার লিস্ট তৈরি করতে। যেমন, একই মার্কিন নির্বাচনে দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট প্রতিটি রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক সাংবাদিকদের অনুসরণের জন্য একটি টুইটার লিস্ট তৈরি করেছে।
- জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির মিডিয়া অ্যান্ড ইলেকশনস গাইড দেখুন, নির্বাচনে গণমাধ্যমের ভূমিকা কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এবং বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রচারণা থেকে মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মানগুলো কী।
প্রচারণা শুরুর সঙ্গে জড়িতদের বিষয় খতিয়ে দেখুন

অলংকরণটি করেছেন মার্সেল লু
নির্বাচনের শুরুর দিকেই অনেক জনপ্রিয় দল, তাদের সহযোগী বা বিদেশি স্বৈরশাসক সরকারগুলো গোপন বা “ডার্ক পিআর এজেন্সি” ভাড়া করে। এই এজেন্সিগুলোর কাজ হলো প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নেতা ও কর্মীদের বদনাম করা। সাংবাদিকরা দেখেছেন, এসব এজেন্সি অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের টাকা দিয়ে গুজব ও ইঙ্গিতপূর্ণ তথ্য ছড়ানোর কাজ করায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই প্রচারণার অর্থের উৎস খুঁজে বের করাই অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য বড় খবরের সূত্র হতে পারে।
জিআইজেএন-এর “রিপোর্টারস গাইড টু ইনভেস্টিগেটিং ডিজিটাল থ্রেটস”-এ গুয়াতেমালার সাংবাদিক লুইস আসার্দো উল্লেখ করেছেন, এখন অনেক দেশে কিছু পিআর এজেন্সি নিজেরাই সোস্যাল মিডিয়া ট্রল ফ্যাক্টরি তৈরি করছে—যেখানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের জন্য বিশেষভাবে মানুষ নিয়োগ দেওয়া হয়, যাতে তারা নির্বাচনের সময় গুজব ও প্রচারণা চালাতে পারে।
মেক্সিকোর সাম্প্রতিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় এল পাইস পত্রিকার অনুসন্ধানেও দেখা গেছে, ফিলিপাইনে অনেক নির্বাচনী প্রচারণা দল মার্কেটিং এজেন্সি ভাড়া করে, যারা ভাড়াটে ট্রল ব্যবহার করে প্রচারণা ছড়ায় এবং বিরোধীদের আক্রমণ করে।
আসার্দো সাংবাদিকদের সতর্ক করে বলেছেন—যে কোনো ভুয়া নির্বাচনী বয়ানের পেছনে জনপ্রিয় সমর্থন দেখালে ধরে নিবেন তা হয়তো আসল নয়; বরং এটি হতে পারে “অ্যাস্ট্রোটারফিং” নামের একটি কৌশল, যেখানে অনেক ভুয়া অ্যাকাউন্ট একসঙ্গে ব্যবহার করে মিথ্যা জনসমর্থন দেখায়।
পরামর্শ: ট্রল প্রচারণা শনাক্ত করতে আসার্দো ব্র্যান্ডওয়াচ, মেল্টওয়াটার, ব্র্যান্ড২৪ এবং টকওয়াকার–এর মতো “লিসেনিং টুলস” ব্যবহারের পরামর্শ দেন। এসব টুল দিয়ে নির্দিষ্ট হ্যাশট্যাগ ও কিওয়ার্ড ট্র্যাক করে ভুয়া প্রচারণা ধরা যায়।
নির্বাচনী প্রচারণার শুরুতেই উন্নত সার্চ কৌশলগুলো সম্পর্কে জানুন
নির্বাচনের শেষ সপ্তাহগুলোতে ব্যস্ত সময় বা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের চাপে কার্যকর অনলাইন অনুসন্ধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই যারা এখনও শেখেননি, তাদের জন্য নির্বাচনী সময়ের শুরুতেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনলাইন সার্চ কৌশল শেখা ও অনুশীলন করা জরুরি — এগুলো এমন শক্তিশালী পদ্ধতি, যেগুলো ব্যবহারে কোনো জটিল নেই, কম্পিউটার দক্ষতারও প্রয়োজন হয় না। অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের পরামর্শ অনুযায়ী, বিবিসি অনলাইন অনুসন্ধান বিশেষজ্ঞ পল মায়ার্সের লেখা জিআইজেএনের অ্যাডভান্সড সার্চ টেকনিকস টিপশিট একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু কার্যকর গাইড, যেখানে অনুসন্ধানের পরিধি ও ফলাফল নির্ভুলভাবে নির্ধারণের টিপস রয়েছে — যা প্রায় সব ধরনের অনুসন্ধানী কাজে সহায়ক। আরও গভীরভাবে জানতে চাইলে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও সোশ্যাল মিডিয়া অনুসন্ধানের জন্য হেঙ্ক ফন এসের লেখা জিআইজেএনের নতুন অনলাইন রিসার্চ গাইডটি পড়ে দেখতে পারেন।
নির্বাচন নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির সময়গুলোতে নিরাপত্তা
সত্য প্রকাশকারী সাংবাদিকরা, তাদের সংগৃহীত তথ্য ও সূত্র—সবই নির্বাচনী অসৎ প্রভাবশালীদের টার্গেটে পরিণত হতে পারে, যারা চায় না ভোটাররা আসল তথ্য জানুক। তাই সাংবাদিকদের জন্য সঠিক ডিজিটাল হাইজিন চর্চা এবং স্মার্ট সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা চর্চা উল্লেখ করা হলো যা অনুসরণ করা উচিত।
- আপনার আইফোনের “লকডাউন মোড” সক্রিয় করুন। ১৩তম গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম কনফারেন্সে টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের সিটিজেন ল্যাবের সাইবার সিকিউরিটি রিসার্চ ইউনিটের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক রন ডেইবার্ট তার মূল বক্তব্যে এমন বহু গোপন নজরদারি হুমকির কথা বর্ণনা করেছেন যা বর্তমানে স্বাধীন সাংবাদিকদের সারা বিশ্বে বিভ্রান্ত করেছে । ডেইবার্ট সতর্ক করেছেন, পেগাসাসের মতো নতুন জিরো-ক্লিক হ্যাকিং প্রযুক্তি সাংবাদিকদের ফোনে কোনো লিংক ক্লিক না করেই ঢুকে পড়তে পারে, এবং ফোনের মেসেজ, ক্যামেরা ও মাইক্রোফোনে প্রবেশাধিকার নিতে পারে, কোনো চিহ্ন না রেখেই। তবুও তিনি বলেন, আইফোন ব্যবহারকারীরা “লকডাউন মোড” চালু করলে অনেকটা নিরাপদ থাকবেন, কারণ এখন পর্যন্ত পেগাসাস সেই মোডে চলা কোনো ফোনে প্রবেশ করতে পারেনি।
- লিঙ্গভিত্তিক হয়রানি সম্পর্কে সচেতন থাকুন, তা প্রকাশ করুন এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর জার্নালিস্টস (আইসিএফজে)-এর এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে ভারতের সাংবাদিক রানা আয়ুবের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়াবহ হয়রানির ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে—যেখানে ইসলামবিদ্বেষী গালাগাল, ধর্ষণ ও হত্যার হুমকি থেকে শুরু করে মিথ্যা মামলাসহ নানা রকম নির্যাতন চালানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবেই তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা, নজরদারি, এবং সংগঠিত অনলাইন হয়রানি অভিযান চালানো হয়। আইসিএফজের প্রতিবেদনে এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রানা আয়ুবের ঘটনার সঙ্গে ফিলিপাইনের সাংবাদিক ও নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মারিয়া রেসার ওপর চালানো রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের ভয়ানক মিল রয়েছে। প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়, এখন স্বৈরাচারী শাসকরা নারী সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণের একই “প্লেবুক” অনুসরণ করছে। গার্ডিয়ানের এক অনুসন্ধানে আরও দেখা গেছে, অনেক দেশে যেমন ভারতে, নারী সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাকেও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আইসিএফজের প্রতিবেদনের ভাষায়, আয়ুবের ঘটনা দেশটির নারী সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণের প্রতীক—যেখানে অনলাইন “লিঞ্চ মব” ক্ষমতাসীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নারীবিদ্বেষী ও ভুয়া তথ্যনির্ভর হামলা চালায়।

ছবি: স্ক্রিনশর্ট, ইউনেস্কো
- ইউনেস্কোর প্রতিবেদন দ্য চিলিং: হোয়াট মোর ক্যান নিউজ অর্গানাইজেশন্স ডু টু কমব্যাট জেন্ডার্ড অনলাইন ভায়োলেন্স?-এ অনলাইন সহিংসতার সংকট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নারী সাংবাদিকরা চাইলে এই প্রতিবেদন ছাড়াও জিআইজেএনের রিসোর্সেস ফর উইমেন রিপোর্টার্স গাইডের সেফটি চ্যাপ্টার-এ এমন অনেক কার্যকর উৎস খুঁজে পাবেন, যা এসব হুমকি কমাতে সহায়তা করবে। এছাড়া ঝুঁকিগ্রস্ত সাংবাদিকদের সহায়তার জন্য নিরাপত্তা নির্দেশিকা এবং সহায়তাকারী সংগঠনগুলোর তালিকাসহ একটি সাধারণ রিসোর্স পেজও তৈরি করেছে জিআইজেএন।
- সাইবার নিরাপত্তা ড্যাশবোর্ড: নির্বাচনকালীন সাইবার ঝুঁকিকে মাথায় রেখে তৈরি জিসিএ সাইবারসিকিউরিটি টুলকিট ফর জার্নালিস্টস-এ সাংবাদিকদের জন্য বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যের বিভিন্ন টুল পাওয়া যায়—যেমন পাসওয়ার্ড ম্যানেজার, ম্যালওয়্যার প্রোটেকশন ও এনক্রিপশন সফটওয়্যার। এছাড়া নিজের অবস্থান বা দক্ষতার স্তর অনুযায়ী কোন ধরনের ডিজিটাল সুরক্ষা পদ্ধতি সবচেয়ে উপযোগী হবে তা জানতে জিআইজেএনের ডিজিটাল সিকিউরিটি গাইড থেকে সহায়তা নিতে পারেন।
- ডিভাইস এনক্রিপশন: এখানে অনেক ভালো এবং বিনামূল্যের টুল পাওয়া যায়, তবে বিশেষজ্ঞরা সাধারণত কয়েকটি নির্ভরযোগ্য বিকল্পের পরামর্শ দেন—যোগাযোগের জন্য সিগন্যাল, ইমেইলে নথি পাঠানোর জন্য প্রোটনমেইল , কাগজপত্রের জন্য পোস্ট অফিস বক্স, এবং আপনার ব্যবহৃত ডিভাইস জব্দ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে ভেরাক্রিপ্ট ব্যবহার করতে বলেন।
- শারীরিক নজরদারি: যদি মনে হয় রাজনৈতিক প্রচারণা, স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা উগ্রপন্থীরা আপনাকে বা আপনার সোর্সকে অনুসরণ করছে, তাহলে জিআইজেএনের এই প্রতিবেদনে দেওয়া পরামর্শ ও পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করুন। তবে যদি সন্দেহ হয় যে পুলিশ বা রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা আপনাকে অনুসরণ করছে, তাহলে মানবাধিকার বিষয়ক আইনজীবী বা সিটিজেন ল্যাব, ইলেকট্রনিক ফ্রন্টিয়ার ফাউন্ডেশন–এর মতো অলাভজনক মানবাধিকার নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আর পরিস্থিতি যদি খুব খারাপ হয়, তাহলে দেশ ছাড়ার বিষয়টিও ভেবে দেখতে পারেন। এছাড়া, যদি আশঙ্কা থাকে যে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো আপনার বাসায় অভিযান চালাতে পারে, তাহলে সেই ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য এই প্রতিবেদনের পরামর্শগুলো পড়ে নিন।
- নির্বাচন কাভার করার সময় শারীরিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত সাধারণ পরামর্শ: সিপিজের জার্নালিস্ট সেফটি কিট ফর ইলেকশনস গাইড দেখুন। এই গাইডে রয়েছে এডিটর্স’ সেফটি চেকলিস্ট, সংহিস সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে কাজ করার পরামর্শ, এবং যোগাযোগ ও ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতিমূলক নির্দেশিকা। এছাড়া সিপিজে ২০২১ সালের মেক্সিকো নির্বাচনের জন্যও একটি সেফটি গাইড প্রকাশ করেছে, যা ২০২৪ সালেও প্রাসঙ্গিক।
- রাজনৈতিক বিক্ষোভ কাভার বিষয়ক নিরাপত্তা: রাজনৈতিক বিক্ষোভ কাভার করতে গিয়ে নিরাপদ থাকার জন্য সিপিজের গাইড দেখুন। এতে বলা আছে কীভাবে পোশাক বাছাই করবেন এবং টিয়ার গ্যাসের ঝুঁকি থেকে বাঁচবেন।
- দাঙ্গা বা নির্বাচনী বিক্ষোভে ডিজিটাল নিরাপত্তা: যেসব অনুষ্ঠানে নজরদারি, গ্রেপ্তার বা ফোন জব্দের ঝুঁকি থাকে, সেখান থেকে আপনার ডিভাইস ও তথ্য রক্ষা করার জন্য পেন আমেরিকার গাইডটি দেখুন।
- গুগল ভয়েস। নির্বাচনের সময় চরমপন্থী বা অতি-সমর্থকদের হয়রানি, বিশেষ করে নারী সাংবাদিকদের জন্য একটি বড় সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে, আপনার দেশে যদি সম্ভব হয়, নিরাপদ ও বিনামূল্যের গুগল ভয়েস অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। এটি একটি ভয়েস-ওভার-ইন্টারনেট প্রোটোকল (VoIP) ফোন সার্ভিস, যা একাধিক ফোন নম্বরকে একত্রিত করে “ভার্চুয়াল বার্নার ফোন” হিসেবে কাজ করতে পারে। এছাড়া এর মাধ্যমে ভয়েসমেইল সার্চও করা যায়।
নির্বাচনের সময় ও পরিধিগত চ্যালেঞ্জ সামলানোর উপায়
নির্বাচনকে ঘিরে থাকে একের পর এক নির্দিষ্ট সময়সীমা—ভোটার নিবন্ধন, প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিল, ভোটগ্রহণের দিন-ক্ষণ। এসব সময়সীমার আগে-পরে অসংখ্য পরিবর্তনশীল তথ্য জমা হয়। নিচে এমন কিছু টুল বা উপায় দেওয়া হলো, যা এই চাপ কমাতে সাহায্য করবে।
- ক্ল্যাক্সন অ্যালার্ট ব্যবহার করুন। সংবাদকর্মীদের পক্ষে নানা নির্বাচনী ওয়েবসাইট—যেমন ভোটার তথ্যের সরকারি সাইট, প্রার্থী বা বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীর সাইট—নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা প্রায় অসম্ভব। এই কাজটি সহজ করতে ব্যবহার করুন ওপেন-সোর্স ক্ল্যাক্সন অ্যাপ। নিরপেক্ষ মার্কিন সংস্থা দ্য মার্শাল প্রজেক্ট তৈরি করেছে এই টুলটি, যা আপনার বুকমার্ক করা ওয়েবসাইট বা নির্দিষ্ট ওয়েবপেজে কোনো পরিবর্তন ঘটলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত করে এবং ইমেইল, ডিসকর্ড বা স্ল্যাকের মাধ্যমে আপনাকে সতর্কবার্তা পাঠায়।
- অবশ্যই আর্কাইভিং করুন। দলীয় বা পক্ষপাতদুষ্ট ওয়েবপেজগুলো প্রায়ই মুছে ফেলা হয়—আর জনসমালোচনার পর তাদের প্রকাশিত কন্টেন্ট বা তথ্য অস্বীকার করাও খুব সাধারণ ঘটনা। তাই নিজের অনলাইন অনুসন্ধানগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষণ করতে ব্যবহার করুন হাঞ্চ.লি প্লাগইন। পরিবর্তিত বা মুছে ফেলা ওয়েবপেজ পুনরুদ্ধার করতে ওয়েবব্যাক মেশিন ব্যবহার করুন। এই টুলের আপডেট ফিচার সম্পর্কে জানতে ওয়েবব্যাক মেশিন ম্যানেজার পাঠানো জিআইজেনের এই লেখা দেখুন।
- ইন্টারভিউ অটো–ট্রান্সক্রিপশন ব্যবহার করুন। নির্বাচনী সাক্ষাৎকার ট্রান্সক্রাইব ও কীওয়ার্ড সার্চ করার জন্য ট্রিন্ট বা অটার–এর মতো পরিষেবা ব্যবহার করতে পারেন। যদিও এই কোম্পানিগুলো দাবি করে যে রেকর্ডিং ও ট্রান্সক্রিপ্ট নিরাপদ এবং তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে শেয়ার করা হয় না, তবে ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসের ডেটা নিরাপত্তা সম্পর্কিত এই বিষয়গুলো যাচাই করা গুরুত্বপূর্ণ। অপতথ্য নিয়ে কাজ করেন বিশেষজ্ঞ জেন লিটভিনেনকো। তিনি বলেন, স্ক্রিনশট প্রমাণ সংরক্ষণের জন্য যথেষ্ট নয়—সাংবাদিকেরা তাই এই অটো-আর্কাইভিং টুল ব্যবহার করে ডিজিটাল প্রমাণ নিশ্চিত করুন। “স্ক্রিনশট সহজেই পরিবর্তনযোগ্য, পেজের মেটাডেটা সংরক্ষণ করে না, এবং সবসময় আদালতে গ্রহণযোগ্য নয়,” তিনি উল্লেখ করেন।
- সহিংসতার আশঙ্কা ঘিরে রিপোর্টিং পরিকল্পনা করুন। নির্বাচনের সময় সহিংসতা প্রতিরোধ ও বিশ্লেষণে স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের তথ্য অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। তাদের সূত্রে সম্ভাব্য সংঘাতপ্রবণ এলাকার তথ্য পাওয়া যায়। পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমে নির্দিষ্ট কীওয়ার্ড দিয়ে অনুসন্ধান করলে অনেক সময় সমাবেশে সহিংসতার পরিকল্পনার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। লিটভিনেনকো বলেন, টেলিগ্রাম প্ল্যাটফর্মে সার্চ করা—গুগলে site:t.me (প্লাস কীওয়ার্ডস) দিয়ে চ্যানেল খুঁজে এবং tgstat.com দিয়ে বিশ্লেষণ করা— অনেক দেশে পরিকল্পিত ভয়ভীতি ঘটনার চিহ্নিতকরণে বিশেষভাবে কার্যকর। এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল আইডিয়া–এর তৈরি ইলেকটোরাল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট টুল দেখুন।
- নির্বাচন বিষয়ক সোশ্যাল মিডিয়া চ্যাট গ্রুপ সার্চ করুন। ফেসবুক গ্রুপের জন্য গুগলে এই সিকোয়েন্স ব্যবহার করুন: site:facebook.com/groups “কীওয়ার্ড”।
- পুলিশ চ্যাটার মনিটর করুন। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় সম্ভাব্য নির্বাচনি সহিংসতার খবরের জন্য নির্বাচন সংক্রান্ত স্থাপনার কাছাকাছি রিয়েল-টাইমে পুলিশ ও ইএমএস রেডিও স্ক্যানার অ্যাপগুলো দেখুন—যেমন ব্রডকাস্টিফাই, ওপেনএমএইচজেড বা ৫-০ রেডিও প্রো।
- নির্বাচন সম্পর্কিত বুলিয়ান সার্চের জন্য স্প্রেডশীট তৈরি করুন। এনওয়াইইউ সাইবারসিকিউরিটি ফর ডেমোক্রেসি প্রজেক্টের সাংবাদিক-পরামর্শক ন্যান্সি ওয়াটজম্যান বলেন, পুরো নির্বাচনী সময়ে যে অস্বাভাবিক, অতিপক্ষপাত বা “ডগ হুইসেল” শব্দগুলো সামনে আসে, সেগুলো সংগ্রহ করা একটি ভালো অভ্যাস। তিনি পরামর্শ দেন, সাংবাদিকরা বিষয়ভিত্তিক বিভাগে ভাগ করে যেন এসব তথ্য একটি স্প্রেডশিটে রাখেন। পরে নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে এলে সেই স্প্রেডশিট থেকেই তারা বুলিয়ান সার্চ পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালাতে পারবেন। বুলিয়ান টার্ম বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করলে গুগল সার্চকে আরও নির্ভুলভাবে কাজে লাগানো যায়। (ওয়াটজম্যান যুক্তরাষ্ট্রে ৬ জানুয়ারির ক্যাপিটল দাঙ্গার পর এমন একটি স্প্রেডশিট ব্যবহার করে সম্ভাব্য হুমকির সন্ধান করেছিলেন।)
- নির্বাচন নিয়ে কথা বলবেন এমন হুইসলব্লোয়ারদের জন্য নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করুন। অনুসন্ধানী সম্পাদকরা জোর দিয়ে বলেন, উঁচুমানের, সাহসী এবং নন-হর্স-রেস রাজনৈতিক প্রতিবেদক হিসেবে পরিচিতি থাকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—এটি যে কোনো প্রার্থীর অভ্যন্তরীন সূত্র থেকে ফাঁস হওয়া তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক। যদিও, কোনো প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষেবর কাছ থেকে পরিচালিত “অপো” দাবি বা প্রচারণামূলক বা রাজনৈতিক প্রভাবিত কৃত্রিম অভিযোগের অভাব থাকে না, তবে প্রার্থীর কর্মীদের বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার ভেতরের সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য প্রায়ই অনেক বড় নির্বাচনী খবরের সূত্র হয়ে ওঠে।
নির্বাচন ট্রেন্ডগুলো পর্যবেক্ষণ করুণ
প্রতিটি নির্বাচনী পরিস্থিতিতে স্থানীয় স্বতন্ত্র বিষয় ছাড়াও বৈশ্বিক প্রবণতা (ট্রেন্ড) থাকে, যা অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। এই ট্রেন্ডগুলো তৈরি হয় জনসংখ্যার পরিবর্তন, নতুন প্রযুক্তি বা ডিজিটাল হুমকি, এবং সরকার ও নির্বাচনী কর্তৃপক্ষের একে অপরের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ থেকে। কিছু ট্রেন্ড নতুন চুক্তি ও সরকারি ব্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত; কিছু ভোটের অখণ্ডতার জন্য সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে কাজ করতে পারে; আবার কিছু গণতন্ত্র প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে আসে, কিন্তু ভোটারদের বিভ্রান্তও করতে পারে—এবং সবই সম্ভাব্য প্রতিবেদন বা লিড স্টোরি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
সম্ভবত সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রবণতাটি হলো স্বৈরশাসকদের প্লেবুক, যেখানে ক্রমশ স্বৈরশাসক নেতারা একে অপরের থেকে দমনমূলক নির্বাচনী কৌশল অনুকরণ করছেন। (এই কৌশলগুলো আমরা নীচে বিশ্লেষণ করেছি।)
তবে অ্যালায়েন্স ফর সিকিউরিং ডেমোক্রেসি-এর নির্বাচনী অখণ্ডতা বিষয়ক ফেলো ডেভিড লেভিন এবং ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকটোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স (ইন্টারন্যাশনাল আইডিয়া)-এর ইউরোপ প্রোগ্রামের প্রধান স্যাম ভ্যান ডার স্ট্যাক নজরদারির জন্য অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রবণতার কথাও উল্লেখ করেছেন।
- রাজনৈতিক মিডিয়ার একচেটিয়া মালিকানা। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে মিডিয়ার মালিকানায়—বিশেষ করে টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে—বর্তমান ক্ষমতাসীন রাজনীতিক, অলিগার্ক এবং স্বৈরশাসকদের ব্যবসায়িক সহযোগীদের প্রবণতা তীব্রভাবে বেড়েছে। এর ফলে নির্বাচনী কভারেজ পক্ষপাতমূলক হয়ে যায় এবং স্বাধীন মিডিয়ার প্রতি মিথ্যা বা প্রভাবিত সমালোচনা ছড়িয়ে পড়ে। “মিডিয়ার মালিকানা সম্পর্কে আমাদের জানা খুবই কম,” বলেন ভ্যান ডার স্টাক। “কিন্তু আমরা দেখছি টিভি চ্যানেলগুলো বড় ধরনের রাজনৈতিক স্বার্থের হাতে চলে যাচ্ছে, এবং এমন আইন তৈরি হচ্ছে যা এতই জটিল যে পক্ষপাত নিয়ে যারা লড়াই করে, তাদের বছরের পর বছর মামলা করতে হয়—এবং আদালতে জেতার সময় পর্যন্ত নির্বাচন শেষ হয়ে গেছে, তখন অনেক দেরি হয়ে যায়।” তিনি আরও যোগ করেন: “পূর্ব ইউরোপ এবং পশ্চিমী বালকান অঞ্চলে দেখা যায়, বেশিরভাগ চ্যানেল অত্যন্ত রাজনৈতিক হয়ে গেছে, এবং সরাসরি রাজনীতিক বা অফশোর কোম্পানির মালিকানায় রয়েছে।” পরামর্শ: মিডিয়ার মালিকানা ও রাজনৈতিক সংস্থার সংযোগের ওপর ৪০টি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে তৈরি এই নতুন ডেটাবেসটি দেখে নিন।.
- বিদেশি হস্তক্ষেপ। অ্যালায়েন্স ফর সিকিউরিং ডেমোক্রেসি কর্তৃক তৈরি অথরিটারিয়ান ইন্টারফেয়ারেন্স ট্র্যাকার দেখুন। এটি ২০০০ সাল থেকে ৪০টি দেশের বিরুদ্ধে বিদেশি দাতা, সাইবার আক্রমণ এবং ভুয়া তথ্য প্রচারের ঘটনা বিশদভাবে তালিকাভুক্ত ও মানচিত্র আকারে উপস্থাপন করে। এছাড়া, ফরেন ইন্টারফেয়ারেন্স অ্যাট্রিবিউশন ট্র্যাকার এবং ফ্রেঞ্চ ইলেকশন ড্যাশবোর্ড অন ফরেন ন্যারেটিভস-এর মতো ডেটাবেসের সঙ্গে ফলাফল ক্রস-চেক করাও কার্যকর। তবে লক্ষ্য করুন, রাশিয়া, হাঙ্গেরি, আজারবাইজান থেকে ভারত পর্যন্ত অনেক দেশ “বিদেশি এজেন্ট” এবং “বিদেশি হস্তক্ষেপ” শব্দগুলোকে প্রপাগান্ডার অংশ হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এছাড়া, স্বাধীন মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখার এবং সমালোচনামূলক, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে প্রেসে বিদেশি তহবিলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে।
- পশ্চিমে ম্যানুয়াল ভোটিং ব্যবস্থা ফিরে আসা। লেভাইন জানান, সাম্প্রতিক রাশিয়ার হস্তক্ষেপ এবং হ্যাকিং প্রচেষ্টা অনেক উন্নত দেশকে—যেমন নেদারল্যান্ডস—ডিজিটাল নির্বাচনের নিরাপত্তা পুনর্বিবেচনা করতে এবং ম্যানুয়াল ব্যালটিং ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার দিকে প্রভাবিত করেছে।
- নতুন গণতন্ত্রে ডিজিটাল নির্বাচনী অবকাঠামোর ঝুঁকি। ভ্যান ডার স্টাক বলেন, অতীতের দমননীতির প্রভাব অনেক নতুন গণতন্ত্র এবং প্রাক্তন কমিউনিস্ট ব্লকের দেশে স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটেড) ভোটিং সিস্টেমের ব্যবহার বাড়িয়েছে—সঙ্গে দুর্নীতির সম্ভাবনাও। তিনি ব্যাখ্যা করেন, “মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশে মানুষ এখনও যন্ত্রের তুলনায় মানুষকেই বেশি বিশ্বাস করে, কারণ তাদের প্রতিষ্ঠানের ওপর বিশ্বাস কম।” যদিও কিছু ব্যবস্থা নির্ভরযোগ্য, ভ্যান ডার স্টাক বলেন, অনেক ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল নির্বাচনী সিস্টেম এখনও কৌশলগত হস্তক্ষেপ এবং দুর্নীতির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষত যেসব দেশ কম পাসপোর্ট বা ড্রাইভিং লাইসেন্সের কারণে বায়োমেট্রিক পরিচয় পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, তাদের ক্ষেত্রে দুর্নীতির ঝুঁকি বেশি—কারণ এর ক্রয় খরচ অনেক বেশি। তিনি বলেন, “একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি দেখতে চাই এসব কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং ক্রয় করা হয়েছে; প্রায়শই বড় কেলেঙ্কারিগুলো এখান থেকেই বের হয়।”
- অপ্রচলিত আরও অন্যান্য ভোটিং পদ্ধতি। ২০২০ সালে করোনা মহামারী অনেক দেশের ভোটিং সিস্টেমকে ব্যাহত করেছে। এর ফলে বিশেষ ভোটিং ব্যবস্থাগুলো যেমন পোস্টাল, ইলেকট্রনিক, প্রক্সি ভোটিং এবং প্রবাসী জনগণের জন্য ভোটিং পদ্ধতি আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ভ্যান ডার স্টাক বলেন, “নতুন প্রযুক্তির কারণে দেশগুলো এই নতুন ভোটিং পদ্ধতিগুলো গ্রহণের দিকে এগোচ্ছে, কিন্তু সাংবাদিক এবং পর্যবেক্ষকদের জন্য এগুলো মনিটর করা কঠিন হয়ে পড়েছে।” মোলডোভা, বুলগেরিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো আরও বেশি ইলেকট্রনিক ভোটিং বিবেচনা করছে, আর আলবেনিয়া প্রবাসী নাগরিকদের জন্য অনলাইন ভোটিং পরীক্ষা করছে।
- ডেটা প্রাইভেসিকে আড়াল হিসাবে ব্যবহার করে প্রচারণার স্বচ্ছতা এড়ানো। ভ্যান ডার স্টাক বলেন, ইউরোপের বাইরে কিছু রাজনীতিক এবং আইনপ্রণেতা নির্বাচনী তহবিল সম্পর্কিত স্বচ্ছতা কমানোর জন্য অঞ্চলের কঠোর জিডিপিআর ডেটা সুরক্ষা নিয়মকে একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে। তিনি ব্যাখ্যা করেন, “ডেটা সুরক্ষা ইতিবাচক খ্যাতি পেয়েছে, কিন্তু আমি কিছু দেশেই দেখছি তারা এটিকে বড় তহবিল দাতাদের সত্যিকারের পরিচয় লুকানোর অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা বলে: ‘ডেটা প্রাইভেসির কারণে আমরা দাতাদের নাম প্রকাশ করতে পারি না।’” তিনি যোগ করেন, “তারা জিডিপিআর-এর কিছু অংশ নিজেদের ক্ষমতার স্বার্থে পরিবর্তন করে ব্যবহার করছে। সাংবাদিকরা এই দাবিগুলো যাচাই করতে পারেন।”
- সরকারি নির্বাচনী ওয়েবসাইটে ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়াল অফ সার্ভিস (DDoS) আক্রমণ। ডিনায়াল অফ সার্ভিস ধরনের সাইবার আক্রমণের মাধ্যমে ওয়েবসাইটের ওয়েব সার্ভারকে ভারী ট্রাফিক দিয়ে প্যারালাইজ করা হয়। যা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে ক্রমেই বেশি ব্যবহার হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, সাইন-আপের শেষ সময়ের আগে লক্ষ্যভিত্তিকভাবে ভোটার নিবন্ধন সাইটগুলোকে বিঘ্নিত করা যেতে পারে। ভ্যান ডার স্টাক বলেন, সাংবাদিকদের উচিত এসব আক্রমণ নির্বাচনের অখণ্ডতার ওপর যে বড় হুমকি সৃষ্টি করে তা নজরে রাখা। তিনি বলেন, “আমরা সাধারণত সাইবার হুমকিকে রাশিয়ার হ্যাকিং হিসেবে দেখি, কিন্তু সবচেয়ে সাধারণ সাইবার হস্তক্ষেপ হচ্ছে নির্বাচনী কমিশনের ওয়েবসাইটে DDoS আক্রমণ। এটি প্রায়ই কেবল ইঙ্গিত দেয় যে নির্বাচন সংস্থার কার্যপরিচালনা সঠিক নেই। এতে মানুষ ভাবতে শুরু করে পুরো নির্বাচনটি বৈধ কিনা। নির্বাচন যত কাছে আসবে, এর প্রভাব তত বেশি হবে।” তিনি আরও যোগ করেন, “জটিল সাইবারআক্রমণগুলো অপরাধী গোষ্ঠী থেকেও আসতে পারে—যেমন মেক্সিকোর নির্বাচনী কমিশনের ক্ষেত্রে এটাই ভয়ের বিষয়—বা এমনকি ১৬ বছর বয়সী কোনো হ্যাকারও এটা করতে পারে, যিনি নিজের দক্ষতা দেখাতে চান।”
কর্তৃত্ববাদীদের কৌশল চিনতে কিভাবে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করবেন
আগে একটি গণতন্ত্রের পতন চিহ্নিত করা সহজ ছিল—সেনা অভ্যুত্থান বা একাধিক দলীয় নির্বাচনের ওপর নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে। কিন্তু আজ কর্তৃত্ববাদের দিকে সরে যাওয়াটা বোঝা কঠিন। এখন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও তা প্রায়শই আইনি আবরণে বা জরুরি অবস্থার অজুহাতে ঢেকে রাখা হয়, আর রাষ্ট্রসমর্থিত নির্বাচনী সহিংসতার বিষয়গুলো মামুলি হিসেবে দেখা হয় বা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
গবেষকরা দেখেছেন, নির্বাচিত স্বৈরশাসকরা ক্রমেই একে অপরের কাছ থেকে কূট-কৌশল শিখছে, এবং কখনও কখনও তারা একই ধরনের তথ্য-উপাত্ত এবং নোংরা কৌশল বিষয়ক পরামর্শদাতাদেরও ভাগাভাগি করে নেয়। যেমন, একটি মার্কিন থিঙ্কট্যাংক সম্প্রতি বিশদভাবে দেখিয়েছে যে নিকারাগুয়ের সাইবারসিকিউরিটি ও “বিদেশি এজেন্ট” আইনগুলোর সঙ্গে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সরকারের প্রয়োগ করা একই ধরনের দমনমূলক আইনের উল্লেখযোগ্য মিল রয়েছে।
হাঙ্গেরীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আন্দ্রাস বিরো-নাগির মতে, কিছু পরীক্ষিত কৌশলের সমন্বয়ের কারণে ২০২২ সালের এপ্রিলে ভিক্টর ওরবান ধারাবাহিকভাবে চতুর্থবারের মতো নির্বাচনে জয়ী হন: কাল্পনিক “জনপ্রিয় শত্রু” দিয়ে অসচেতন ভোটারদের ভয় দেখানো; পক্ষপাতদুষ্ট নির্বাচনী নিয়ম ও মিডিয়ার কভারেজের মাধ্যমে বিরোধী দলগুলোকে অপসারণ করা; এবং নির্বাচনের কয়েক মাস আগে সরকারি তহবিল থেকে টেকসই নয় এমন ভাতা বিতরণ করা।

ছবি: স্ক্রিনশট, দ্য ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর
পুরনো পদ্ধতির কৌশল—যেমন ব্যালট বাক্সে ভোট ভরা বা বিরোধী সমর্থকদের ওপর সহিংসতা চালানো—থেকে শুরু করে নতুন কর্তৃত্ববাদী শাসকদের কৌশলের দারুণ একটি উদাহরণ দিয়েছেন জিম্বাবুয়ের রবার্ট মুগাবের সরকার। ২০০৮ সালে, মুগাবের দলের এজেন্টরা দেরিতে বুঝতে পারেন যে জেলা অঞ্চলগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণ দ্রুততার সঙ্গে ব্যালট বাক্স ভরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম কিস্তি জেতার মতো যথেষ্ট সক্ষমতা তাদের নেই। এরপর বিরোধীদের ওপর নির্মম সহিংসতার মাধ্যমে “জয়” নিশ্চিত করা হয়—যা আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র সমালোচনার জন্ম দেয়। তবে, ২০১৩ সালের নির্বাচনের আগে মুগাবে রীতিমতো নতুন কৌশলের একটি সিরিজ গ্রহণ করেন, যার মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়কে পরাজিত করা সম্ভব হয় এবং খেলার মাঠ তার দখলে থাকে। সাংবাদিকদের উচিত এই ধরনের নির্বাচনী হেরফের পরিচালনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা এবং এগুলো আগে থেকে অনুমান করার জন্য সতর্ক থাকা।
নিরপেক্ষ প্রোটেক্ট ডেমোক্রেসি সংস্থার তৈরি অথরিটেরিয়ান প্লেবুক রিপোর্টটি দেখুন। এতে রয়েছে বিভিন্ন পরামর্শ, যা দেখায় কিভাবে সাংবাদিকরা স্বৈরশাসনের হুমকিকে সাধারণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে আলাদা করে প্রাসঙ্গিকভাবে কভার করতে পারেন, পাশাপাশি ভারতের, নিকারাগুয়া, হাঙ্গেরি, আর্জেন্টিনা, ফিলিপাইন ও যুক্তরাষ্ট্রের কেস স্টাডি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এই কৌশলগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকুন:
- মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপ নিয়ন্ত্রণ। হাঙ্গেরিতে ভিক্টর ওরবানের নতুন সরকার দ্রুত একটি মিডিয়া কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করে সেলফ-সেন্সরশিপ প্রচার করেছিল, আর সমালোচনামূলক প্রতিবেদনের জন্য কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করেছিল। সার্বিয়াতে অলিগার্ক এবং স্বৈরশাসক রাষ্ট্রপতির সহযোগীরা প্রায় সব বাণিজ্যিক টেলিভিশন চ্যানেলে নিয়ন্ত্রণ করার মতো অংশীদারিত্ব অর্জন করেছে, যেগুলোকে সরকারি তহবিল দিয়ে সমর্থন করা হয় এবং তারপর রাষ্ট্রীয় মিডিয়ার মতো প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করানো হয়।
পরামর্শ: মিডিয়া মালিকানা ডেটাবেস থেকে সম্পর্কগুলো আগে থেকেই খুঁজে দেখুন এবং বিশ্বাসযোগ্য অন্যান্য নিউজরুমের সঙ্গে যোগ মেলিয়ে শক্তিশালী আইনি প্রতিরক্ষা দল নিয়োগ করুন।
- সাংবাদিক কিংবা বিরোধী দলের ওপর একই ধরনের নির্বাচনী অপরাধের অভিযোগ চাপানো।
অনেক স্বৈরশাসক প্রার্থী শিখেছে যে প্রমাণভিত্তিক অভিযোগ—তা সেটা নির্বাচনী দুর্নীতি হোক বা ব্যক্তিগত অপরাধ—এর উত্তর হিসেবে তারা নির্দ্বিধায় একই ধরনের অপরাধে অভিযুক্ত করতে পারে। আর এগুলো যখন দলীয় সমর্থকদের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত হয়, স্বৈরশাসকরা এই কৌশল ব্যবহার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে এবং মূল অভিযোগের প্রভাব কমায়।
পরামর্শ: ‘বিরোধী’ পক্ষের অভিযোগের সময়কাল এবং প্রমাণগুলো তুলনা করার জন্য ভিজুয়ালাইজেশন ব্যবহার করুন, এবং আপনার মূল অনুসন্ধানকে আরও দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নিন।
- নির্বাচনী সহিংসতা আউটসোর্স করা—এবং চোখের সামনের পর্দা সরানো। “পুরনো ধাঁচের” কর্তৃত্ববাদী শাসক বা স্বৈরশাসকরা মূলত দেশের স্বাধীনতা যে হুমকির মুখে এমন বয়ান ছড়ানোর জন্য রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে নিয়োজিত করে। কেআরআইকের সম্পাদক স্টেভান ডোজচিনোভিচ বলেন, “নতুন যুগের স্বৈরশাসকরা” বিপরীত কৌশল ব্যবহার করে: রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোকে স্থবির রেখে, এর পরিবর্তে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান এবং স্বৈরশাসক নেতার সহযোগীদের নিয়ন্ত্রিত রাস্তার গ্যাংগুলোকে ব্যবহার করে।
পরামর্শ: রাস্তার দুষ্কৃতিকারী এবং নির্বাচনী প্রচারকদের শনাক্ত করতে ফেসিয়াল রিকগনিশন এবং রিভার্স ইমেজিং টুলস ব্যবহার করুন—তবে রাস্তার রাজনৈতিক গ্যাং নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির সময় সাংবাদিক হিসেবে কিভাবে নিজেকে ঝুঁকিমুক্ত রাখবেন তা নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা গাইডগুলো গুরুত্বসহকারে অনুসরণ করুন।
- সামাজিক ছোটখাটো ঘটনা নিয়ে ভয় ছড়ানো।
জনতুষ্টবাদী প্রচারণার সময় দেখা গেছে ভয় ও দোষারোপের কৌশল এতই কার্যকর যে তারা নীতি-নৈতিকতার বিষয়গুলো পুরোপুরি পরিত্যাগ করে।
পরামর্শ: “সাংস্কৃতিক বিপ্লব” ধরনের বিষয়ে ঘোড়ার দৌঁড়ে লিপ্ত হওয়া কিংবা জনমত জরিপ এড়িয়ে চলুন। বরং ভোটারদের জীবন ও ভোটকে প্রভাবিত করছে এমন আক্রমণমূলক বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দিন।
- স্বাধীন মিডিয়াকে প্রান্তিক বা আস্থাহীন করে গড়ে তোলা।
রাশিয়ার ২০১২ সালের মূল “ফরেন এজেন্ট” আইন—যা যে কোনো আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়া এনজিও এবং সংবাদ সংস্থাকে কার্যত গুপ্তচর হিসেবে ঘোষণা করতে বাধ্য করে— কর্তৃত্ববাদী বা স্বৈরশাসকদের জন্য অনুসরণ করার মতো অন্যতম জনপ্রিয় কৌশল।
পরামর্শ: স্বাধীন মিডিয়া আউটলেটগুলোর সঙ্গে একতা গড়ে তুলুন, এবং নিশ্চিত করুন যে আপনার প্রকাশিত তথ্য প্রতিবেশী দেশের স্বাধীন মিডিয়ার সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রকাশিত হলে আপনাদের নীরব করিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।
- “আইন তৈরি, বিকৃত ও ভঙ্গ করা” নীতিগুলো পর্যবেক্ষণ করা। পোল্যান্ড এবং হাঙ্গেরিকে কেইস স্টাডি হিসেবে ব্যবহার করে গবেষক আন্দ্রিয়া পিরো এবং বেন স্ট্যানলি দেখিয়েছেন কীভাবে স্বৈরশাসক দলগুলো ক্ষমতা সংহত করার জন্য নীতি তৈরি করে। প্রথমে, তারা প্রায়ই নৈতিকতা বা ইতিহাসের সন্দেহজনক দাবির ওপর ভিত্তি করে “গুরুত্বহীন বা তুচ্ছ” নীতি প্রবর্তন করে, যা বিদ্যমান আইনের উল্লিখিত বিষয় বা মূলনীতিকে ভঙ্গ করে না। দ্বিতীয়ত, এমন নীতি প্রচার করে যা সাধারণ তাদের নির্বাহী ক্ষমতাকে বাড়ায়, তবে বিদ্যমান আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এমন নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা যা এই নিয়মভঙ্গকে বৈধতা দেয় এবং ”প্রচলিত রাজনৈতিক”সমালোচনার মাধ্যমে বৈধতা দেয়। তৃতীয়ত, সংবিধান ও আন্তর্জাতিক নীতি বিরোধী নতুন আইন প্রণয়ন করে যাতে তাদের শাসনামল অব্যাহত থাকে।
পরামর্শ: এই নেতাদের ক্রমবর্ধমান জবাবদিহিহীন বাস্তবতাকে মেনে নিবেন না—বরং প্রতিবেদন তৈরি করুন। এমনভাবে কাজ করুন যেন আপনার দেশটি পূর্ণ গণতন্ত্র ও সর্বোচ্চ দায়বদ্ধতার নীতির অধীনে চলছে। নির্বাহী ও আইনসভার মধ্যে লুকানো চুক্তিগুলো গভীরভাবে অনুসন্ধান করুন।
- দুর্নীতি উদ্ঘাটন করতে সক্ষম এমন স্বাধীন অনুসন্ধানী সংস্থাগুলোকে বিলুপ্ত করা। নতুন স্বৈরশাসকরা বিশেষ আইন বা পাবলিক ওয়াচডগ অনুসন্ধানী ইউনিটের মতো স্বাধীন সংস্থাগুলোকে নিষ্ক্রিয় বা বিলুপ্ত করে, এবং তাদের কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রিত বিভাগের (যেমন পুলিশ) নিয়োগ দেয়। ২০০৯ সালে, দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালিন প্রেসিডেন্ট জ্যাকব জুমা সাহসের সঙ্গে স্কর্ফিয়নস ইউনিটের বিলুপ্তি ঘটিয়েছিলেন। ইউনিটটি তার ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন দুর্নীতির জন্য অনুসন্ধান করছিল। বিপরীতে তিনি একটি নতুন ও সীমিত ক্ষমতার ইউনিট তৈরি করেছিলেন যা মূলত সংগঠিত অপরাধ অনুসন্ধান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল।
পরামর্শ: ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে বা শিথিল করা হয়েছে—এমন সরকারি তদন্তকারীদের মধ্য থেকে হুইসেলব্লোয়ারদের খুঁজে বের করুন, এবং নির্বাহী ক্ষমতার অপব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা যেখানে থেমেছিল সেই জায়গা থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে যান।
- বিচারব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সহযোগীদের বসানো। স্বৈরশাসকরা এই সম্পর্কগুলোকে কাজে লাগায়। যেমন, নির্বাচনের জন্য এমন সব সময় নির্ধারণ করে যা বিরোধীদলের ভোটার নিবন্ধনকে ব্যাহত করে, এবং সর্বশেষ সময় পর্যন্ত স্থগিত রাখে। পরামর্শ: বিচারক এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক অনুসন্ধান করলে সাংবাদিকরা পুলিশ কর্তৃক হয়রানি বা আদালতের পক্ষ থেকে শাস্তিমূলক আদেশের শিকার হতে পারেন—তবে স্বাধীন আউটলেট যেমন info–এর সাহসী রিপোর্টাররা দেখিয়েছেন এভাবে কাজ করা সম্ভব। এছাড়া, কীওয়ার্ড ব্যবহার করে আগের রায়গুলো খোঁজা যেতে পারে এবং তাদের সম্পর্কগুলো সামাজিক মিডিয়া ও রিভার্স ইমেজিং অনুসন্ধান দিয়ে অনুসরণ করা যায়।
- “স্বাধীন” নির্বাচন কমিশনকে পক্ষপাতদুষ্ট সহযোগীদের দিয়ে দখল করা।
২০১৩ সালে, জিম্বাবুয়ের নির্বাচন পরিচালনা সংস্থার চেয়ারম্যান হিসেবে যে ব্যক্তি নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তিনি শাসক দল জানু-পিএফ পার্টির সাবেক রাজনীতিবিদ ছিলেন।
পরামর্শ: আপনার নির্বাচন কমিশন বা পরিচালনা সংস্থার নিয়োগ ও মেয়াদকাল সংক্রান্ত নিয়মগুলো এই ডেটাবেসের মাধ্যমে পরীক্ষা করুন।
- দেশপ্রেম বা জাতিগত ভয়ের সুযোগ নেওয়া। গ্রাউন্ড ট্রুথের রিপোর্টারদের “ডেমোক্রেসি আনডাট” প্রকল্পটি নির্বাচনী প্রক্রিয়া বিকৃত করার সাতটি সাধারণ কৌশল তুলে ধরেছেন। তারা ভারত, ব্রাজিল, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, কলম্বিয়া, ইতালি ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনুসরণকৃত ধারাবাহিক কৌশলগুলো বিশ্লেষণ করেছেন—যা তাদের সমর্থকরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে।
পরামর্শ: বৈচিত্র্য ও অভিবাসনের সুবিধাগুলো তুলে ধরুন, এবং জেনোফোবিক (অভিবাসী বিরোধি) দলের কর্মকর্তাদের অভিবাসী পটভূমি উল্লেখ করুন।
- প্রয়োজনীয় ভোটের সংখ্যায় হেরে গেলে প্রতারণা বা বিদেশি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করা এবং ছোট–খাটো ভুলগুলোকে অতিরঞ্জিত করা। ২০২০ সালে কলম্বিয়া জার্নালিজম রিভিউতে উল্লেখ করা হয়েছে, সাংবাদিকদের উচিত গণনা ত্রুটি সংক্রান্ত ছোট ছোট উদাহরণগুলোকে স্বাভাবিক ও প্রাসঙ্গিকভাবে দেখানো, এবং পরিষ্কারভাবে গ্রাফিকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা। তারা বলেছেন: “কিছু ব্যক্তি প্রতিটি ছোট-খাটো ভুলগুলোকেও বাড়িয়ে দেখাতে চাইবে। নির্বাচনের দিনে স্বাভাবিকভাবে কিছু ভুল হয়; মেশিনগুলো কাজ না করে, ভোট কেন্দ্রে বিদ্যুৎ চলে যায় বা দেরিতে খোলে, ভোটার তালিকা ভুল জায়গায় পৌঁছে যায়।”
অ্যালায়েন্স ফর সিকিউরিং ডেমোক্রেসির লেভাইন বলেন, “গণতন্ত্র এখন এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদলের পর্যায়ে রয়েছে। সফল নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সাংবাদিকদের জিজ্ঞেসা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে – বিশেষ করে ভোটারদের কাছে সঠিক তথ্য আছে কিনা তা নিয়ে।”
দ্রষ্টব্য: যদি আপনার কাছে এমন কোনও দুর্দান্ত নতুন টুল বা ডেটাবেস থাকে যা সাংবাদিকদের নির্বাচন সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে, তাহলে দয়া করে hello@gijn.org ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।
রোয়ান ফিলিপ জিআইজেএনের গ্লোবাল রিপোর্টার এবং ইমপ্যাক্ট এডিটর। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সানডে টাইমসের প্রধান প্রতিবেদক ছিলেন। বিশ্বজুড়ে দুই ডজনেরও বেশি দেশে সংবাদ, রাজনীতি, দুর্নীতি এবং সংঘাত নিয়ে প্রতিবেদন করেছেন। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকার বিভিন্ন বার্তাকক্ষে অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর হিসেবেও কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার।