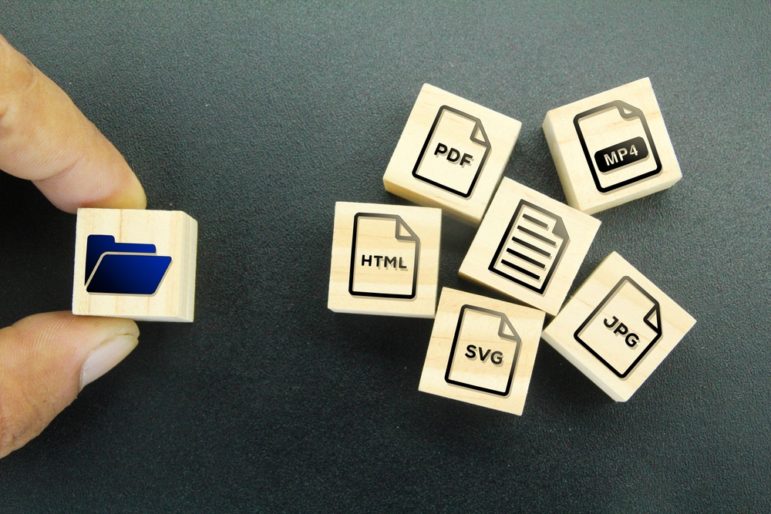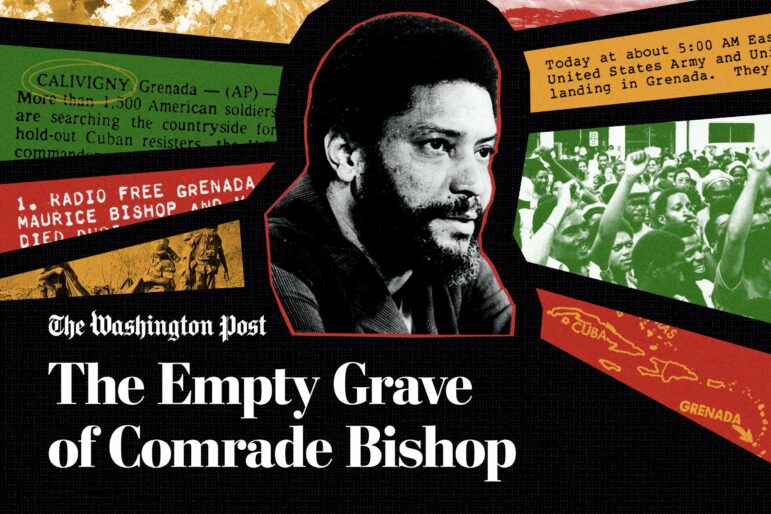كشف الفساد: تشاركنا ميراندا باتروشيك، المحررة الحائزة على جائزة شبكة الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد OCCRP، بعض نصائحها حول تَتبُّع الأموال عبر الحدود
টাকার খোঁজ: নিজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে অনুসন্ধান করবেন যেভাবে
আর্টিকেলটি পড়ুন এই ভাষায়:
দুর্নীতি উন্মোচন: মিরান্ডা প্যাট্রুচিচ, ওসিসিআরপির পুরস্কারজয়ী সম্পাদক। তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন, নিজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে কীভাবে অনুসরণ করতে হয় টাকার গন্তব্য।
অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্টের (ওসিসিআরপি) অন্যতম সম্পাদক মিরান্ডা প্যট্রুচিচ। তিনি মেকিং আ কিলিং নামের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্কের ২০১৭ সালের গ্লোবাল শাইনিং লাইট অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন। এই অনুসন্ধানে তিনি বলকান থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ১২০ কোটি ডলারের অস্ত্র ব্যবসার নেটওয়ার্ক উন্মোচন করেন।
ওসিসিআরপিতে যোগ দেয়ার আগে সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং (সিআইএন) এবং বসনিয়ায় বিবিসির হয়ে কাজ করেছেন মিরান্ডা। তিনি অসংখ্য ক্রসবর্ডার অনুসন্ধানে নেতৃত্ব দিয়েছেন; উন্মোচন করেছেন মুদ্রা পাচারের জটিল নেটওয়ার্ক, শত কোটি ডলারের ঘুষ কেলেংকারি এবং মধ্য এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের শাসক গোষ্ঠীর সন্দেহজনক ব্যবসায়িক লেনদেন। তার উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে আজারবাইজানী লন্ড্রোম্যাট, প্রডিগাল ডটার, এবং পানামা পেপারস।
এই প্রশ্নোত্তরে মিরান্ডা তুলে ধরেছেন, কীভাবে সাংবাদিকরা টাকার সূত্র ধরে বড় বড় ঘটনা উন্মোচন করতে পারেন।
কোনো কোম্পানির আর্থিক রেকর্ড হাতে পেলে আপনি সবার আগে কী করেন?
সবার আগে আমি নিজেকে তিনটি প্রশ্ন করি: ব্যালেন্স শিটে কী আছে? টাকা কোথা থেকে এসেছে? এবং তাদের ’নোট’ সেকশন কী বলছে?
কোম্পানির প্রাথমিক পূঁজি কী শেয়ারহোল্ডারদের বিনিয়োগ থেকে এসেছে, নাকি ঋণ বা অন্য সূত্র থেকে, সেটি জানা যায় ব্যালেন্স শিট পড়ে। জানা যায়, জমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যও। সবচেয়ে মজার জিনিস মেলে “নোট” সেকশনে। কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের মালিকানাধীন অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবসা করছে কিনা, তা জানা যায় এখান থেকে।
সাধারণত, আমি আগে একটি স্প্রেডশিট তৈরি করি। আর্থিক লেনদেনের ইতিহাস থেকে বুঝার চেষ্টা করি, পূঁজির অংকে বড় ধরনের ওঠানামা আছে কিনা। যদি দেখি কোম্পানিটির আয় নেই, কিন্তু বড় অংকের ঋণ আছে, তখন ধরে নিই তাদের ব্যবসায় গন্ডগোল আছে। বাজারে বড় অংকের ’পাওনা’ থাকাও সন্দেহজনক।
.
২০১৭ সালের গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম কনফারেন্সে শাইনিং লাইট অ্যাওয়ার্ড নিতে এসে প্যাট্রুচিচ, তার কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন।
বাইরে বড় অংকের টাকা “পাওনা” থাকার তাৎপর্য কী?
বড় অংকের পাওনা (High receivables) মানে হচ্ছে, কোম্পানিটি প্রচুর পণ্য বা সেবা বিক্রি করেছে, কিন্তু টাকা বকেয়া রয়ে গেছে। এর দুইরকম অর্থ হতে পারে। হয় তারা ব্যবসায় একেবারেই দক্ষ নয়, অথবা তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবসা দেখিয়ে সেই টাকা কোম্পানির বাইরে বা অন্য দেশে সরিয়ে নিচ্ছে। এদের অনেকেরই ছায়া কোম্পানী (shell companies) থাকে। তখন প্রকৃত কোম্পানিটি সেই ছায়া কোম্পানী থেকে ঋণ নেয় এবং সেই টাকা কখনোই শোধ করে না। (এভাবে প্রকৃত কোম্পানিটি নিজেকে দেনাগ্রস্ত দেখায়।)
রাষ্ট্রীয় মালিকানার যেসব প্রতিষ্ঠান বেসরকারিখাতের হাতে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে, সেখানে মালিকের অন্য কোম্পানিতে অবৈধভাবে পূঁজিপাচারের মত দুর্নীতির ঘটনা বেশি দেখা যায়। জ্বালানি বা খনিজ সম্পদের মত যেসব শিল্পে সরকার ভর্তুকি দেয়, সেখানে এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই চোখে পড়ে। দেখা যায়, মালিক নিজে একটি অফশোর কোম্পানি খুলে, প্রকৃত কোম্পানি থেকে কম দামে পণ্য নিচ্ছেন। কখনো কখনো পণ্য নিয়েও দাম শোধ করছেন না। তারপর সেই পণ্য অফশোর প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেশি দামে বিক্রি করে মুনাফা করছেন। এভাবে প্রকৃত কোম্পানিকে লোকসানি বা দেউলিয়া দেখানো হয়। তখন ভর্তুকি দিয়ে তাকে উদ্ধার করা ছাড়া সরকারের কোনো উপায় থাকে না। এই বিষয়গুলো হাই রিসিভেবলস বা “পাওনা” সেকশনে প্রতিফলিত হয়।
কোম্পানির সম্পদ (অ্যাসেট) থেকে কী দেখার আছে?
আমার আগ্রহ বেশি থাকে, ইনট্যানজিবল অর্থাৎ ভৌত নয় এমন সম্পদের দিকে — যেমন, লাইসেন্স। কোম্পানি কী লাইসেন্সটি বাজার দরের চেয়ে কম দামে বিক্রি করেছে নাকি বেশি দামে কিনেছে – আমি সেখানেই নজর দিই। কারণ, এখানেই দুর্নীতি হয় বেশি।
“অবশ্য প্রতিটি বড় স্টোরির জন্য অসাধারণ কিছু বের করে আনা লাগে। কখনো কখনো সেটি আসে পরিশ্রম থেকে, কখনো কপালগুণে। কিন্তু শেষপর্যন্ত হাল ধরে রাখাটাই আসল।”
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, অন্য দেশের প্রতিষ্ঠানের সাথে কোম্পানিটির কোনো যোগসূত্র আছে কিনা খতিয়ে দেখা। কারণ আপনার দেশে জমা দেয়া অডিট রিপোর্টে যে তথ্য দেখানো হয়নি, হয়ত আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে নেদারল্যান্ড বা অন্য দেশের হোল্ডিং কোম্পানির রিপোর্টে সেই তথ্য দেখানো হয়েছে। আর অডিট রিপোর্টে খুব ছোট এবং খুব বড় – দুই ধরনের টাকার অংকই, আমাকে টানে।
অডিট থেকে বড় বড় ঘটনা উন্মোচন করা যায়। যেমন, পানামা পেপার্স অনুসন্ধানের সময় আমরা আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট তনয়াদের মালিকানাধীন একটি খনির অডিট রিপোর্ট দেখছিলাম। সেখানে দেখা যায়, খনি ব্যবহারের অনুমতি বাবদ কোম্পানি থেকে ২০ লাখ ডলার পাওনা দেশটির সরকার। কিন্তু তারা সেটি পরিশোধ করছে না। অডিট রিপোর্টে তাদের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করা হয়, একারণে কোম্পানিটির লাইসেন্স বাতিল হওয়ার ঝুঁকি আছে কিনা। কর্তৃপক্ষের উত্তর ছিল, না। আর এখান থেকেই বেরিয়ে আসে আমাদের স্টোরি, আজারবাইজানের শাসক পরিবার সংশ্লিষ্ট কোম্পানির প্রতি সরকারের স্বজনপ্রীতি।
কোনো কোম্পানির কর্মকাণ্ড বুঝতে আর কী ধরনের গবেষণা কাজে আসতে পারে?
কোম্পানির প্রাথমিক তথ্য দেখেই আমি সিদ্ধান্ত নিই, বাড়তি তথ্যের জন্য জমি বা ব্যবসার রেজিস্ট্রি ঘাঁটাঘাটি করব কিনা। আমি সবসময় কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনও দেখি। এক বছরের সাথে আরেক বছরের তুলনা করি।
তাজিকিস্তান নিয়ে আমরা একটা স্টোরি করেছিলাম, নাম স্বর্ণ বিলাস। এই অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাদের হাতে একটি কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন আসে। সেখানে বলা হচ্ছে, কোম্পানিটি তাজিকিস্তানে কাজের লাইসেন্স পাবে কিনা, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে। ঠিক তার পরের বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, কোম্পানিটি লাইসেন্স পেয়েছে এবং এজন্য তাদেরকে “সাকসেস ফি” দিতে হয়েছে। এখান থেকে আমরা “সাকসেস ফি” বিষয়টির সাথে পরিচিত হই এবং দেখতে পাই দেশটির প্রেসিডেন্টের পরিবারের সাথে জড়িত কোম্পানিগুলোকে সেই ফি দিতে হয়নি।
অনেক সময় কোনো কোনো কোম্পানি অন্য দেশের শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত থাকে। কিছু বিকল্প স্টক মার্কেট আছে, যেখোনে রেগুলেটরের নিয়ন্ত্রণ কম। যেমন, লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জের এআইএম। বিকল্প বাজারে তালিকাভুক্ত এমন কোম্পানি নিয়েও খোঁজখবর করা উচিত।
অনেক সময় কোম্পানির শেয়ারের দাম দেখেও অনিয়ম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু শেয়ার যে অবমূল্যায়িত দামে বিক্রি হচ্ছে তা আমরা কীভাবে বুঝব?
এটা বলা খুব মুশকিল। আজারসেল নামের কোম্পানি নিয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা একটি নথি হাতে পাই। সেখানে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানটিতে সরকারের যত শেয়ার আছে তার মূল্য প্রায় ৬০ কোটি ডলার। কিন্তু সেটি বিক্রি হয়েছে ১৮ কোটিতে। পার্থক্যটা অনেক বড়। এখান থেকে আমরা আবিস্কার করি, আজারবাইজানের মানুষ থেকে তাদের সরকার কীভাবে কোটি কোটি ডলার হাতিয়ে নিয়েছে।
শেয়ারের হিসাব ছাড়াও আপনাকে জমি, অন্য সম্পদের দাম – এমন সব তথ্য খুঁজে বের করতে হবে। এই কাজে অনেক শ্রম দিতে হয়।
অনেক সময় “ভাগ্য” বড় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তাই না?
হ্যাঁ, তাতো বটেই। প্রতিটি বড় স্টোরিতেই অসাধারণ কিছু বের করে আনা লাগে। কখনো কখনো সেটি আসে পরিশ্রম থেকে, কখনো কপালগুণে। কিন্তু শেষপর্যন্ত হাল ধরে রাখাটাই আসল।
আমরা নথিপত্রে জার্মান পার্লামেন্টের এক সদস্যের নাম খুঁজে পাই, যিনি আজারবাইজানী লন্ড্রোম্যাটের মাধ্যমে ১০০, ০০০ ইউরো নিয়েছিলেন। অনেকটা কপালজোরেই হাজারো কাগজের ভিড়ে থাকা একটি ব্যাংক ট্রান্সফারের দলিলে তার নাম পাওয়া যায়। এরপর আমাদের কাজ ছিল শুধু তার পরিচয় নিশ্চিত করা।
স্থানীয়ভাবে নিবন্ধিত কোম্পানি আর অফশোর কোম্পানির মধ্যে পার্থ্যক্য কী?
অফশোরে নিবন্ধিত কোম্পানিগুলো তাদের মালিকানা বা আর্থিক হিসাবনিকাশ জমা দিতে বাধ্য নয়। এমনকি সভার বিবরণী এবং সংবিধির মত সাধারণ দলিলও থাকে না। কেউ তথ্য ফাঁস না করলে, তাদের সম্পর্কে জানা কঠিন। কিন্তু স্থানীয়ভাবে নিবন্ধিত কোম্পানীগুলোকে অনেক তথ্য প্রকাশ করতে হয়। সেই সূত্র ধরে, তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট অফশোর কোম্পানি সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যায়।
কোম্পানি নিয়ে অনুসন্ধানে সরকারি রেজিস্ট্রি কীভাবে কাজে আসে?
অশুভ জোট নামের সিরিজে আমরা একটি কোম্পানি নিয়ে অনুসন্ধান করছিলাম। এক বড় অপরাধীর সাথে যৌথ মালিকানায় তাদের একটি জমি ছিল। কিন্তু জমিটি যে অফশোর কোম্পানীর মাধ্যমে কেনা হয়, তার সম্পর্কে আমরা কোনো তথ্যই পাচ্ছিলাম না। কিন্তু স্থানীয় ভূমি অফিসের রেকর্ড ঘেঁটে আমরা একটা চিঠি পাই। চিঠিটি পানামার ঠিকানা থেকে একজন আইনজীবি পাঠিয়েছিলেন মন্টেনিগ্রোর অর্থমন্ত্রীর কাছে। সেই মন্ত্রী অফশোর কোম্পানিটির মালিক কিনা, আমরা তা নিশ্চিত হতে পারিনি। কিন্তু সরকারী কর্মকর্তারাও যে এই স্টোরির অংশ, তা এই চিঠিই প্রমাণ করেছিল।
বিজনেস রেজিস্ট্রি থেকেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়: কোম্পানির পুনর্গঠন, বিদেশী বিনিয়োগ, সরকারের সাথে অংশীদারিত্ব এবং কোম্পানির আইনজীবি কারা, ইত্যাদি।
প্রডিগাল ডটার নামের অনুসন্ধানে আপনা ঠিক কখন বুঝতে পেরেছিলেন, উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্টের মেয়ে গুলনারা কারিমোভা ১০০ কোটি ডলার ঘুষ নিয়েছেন? নথিপত্র থেকে কী সূত্র মিলেছিল?
এই ঘটনাটা বেশ মজার ছিল। আমাদের কাছে কিছু দলিল ফাঁস করা হয়। সেখানে দেখা যায়, ডজন ডজন কোম্পানি থেকে তার (গুলনারা কারিমোভা) কাছে টাকা যাচ্ছে। বিপণন সেবা, ইভেন্ট পরিকল্পনা, পরিবহন – এমন নানা খাত দেখিয়ে টেলিকম কোম্পানিগুলোকে তিনি টাকা দিতে বাধ্য করতেন। বলা বহুল্য, এসব সেবার কোনোটাই তিনি দিতেন না। কিন্তু নানা রকমের সেবার নামে টাকা আদায়ের উদ্দেশ্য ছিল ধোঁয়াশা তৈরি করা। ৫০ লাখ ইউরোর বিপণন সেবায় আসলে কী হয়, সেটি বুঝা মুশকিল। এসব সেবায় চোখে দেখা বা পরিমাপ করার মত কিছুই থাকে না। আমরা দেখেছি এই টাকা কীভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে তার অফশোর কোম্পানীর মাধ্যমে। প্রেসিডেন্টের মেয়ের আলাদা লোক ছিল, যারা টাকা আসার সাথে সাথে তা কখনো জমি কখনোবা বিলাসপণ্য কিনে খরচ করে ফেলতেন। এভাবে তিনি সন্দেহ এড়ানোর চেষ্টা করতেন।
শেষ প্রশ্ন: অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের ঝুঁকি ও সুরক্ষা নিয়ে কিছু বলবেন, ২০১৬ সালের সম্মেলনে পুরস্কার নিতে এসে আপনি এই বিষয়ে বেশ খোলামেলা কথা বলেছিলেন।
সবসময় সতর্ক থাকুন। আগেই বোঝার চেষ্টা করুন, আপনি যে বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করছেন, তা কত দূর পর্যন্ত গড়াতে পারে। আপনার স্টোরি কতটা গুরুতর বা গভীর, এটি বুঝতে দেরি হয়ে যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। যদি মনে করেন বিষয়টি বিপদজনক, তাহলে একা করবেন না, কাউকে সঙ্গে নিন। আপনার সম্পাদকের সাথে কথা বলুন, সাহায্য চান। গোপন সূত্রের সাহায্য নিলে, তাদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করুন।
ক্যাটারিনা সাবাডোস একজন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক এবং গবেষক। তিনি অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্টের (ওসিসিআরপি) সাথে কাজ করেন। আগে ছিলেন সার্বিয়ার ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং নেটওয়ার্কে (ক্রিক)। মিরান্ডার সাথে তিনি কাজ করেছেন, তাজিকিস্তানে খনিজ আহরণের রহস্যময় চুক্তি নিয়ে তৈরি “ লাস্ট ফর গোল্ড” নামের অনুসন্ধানে।