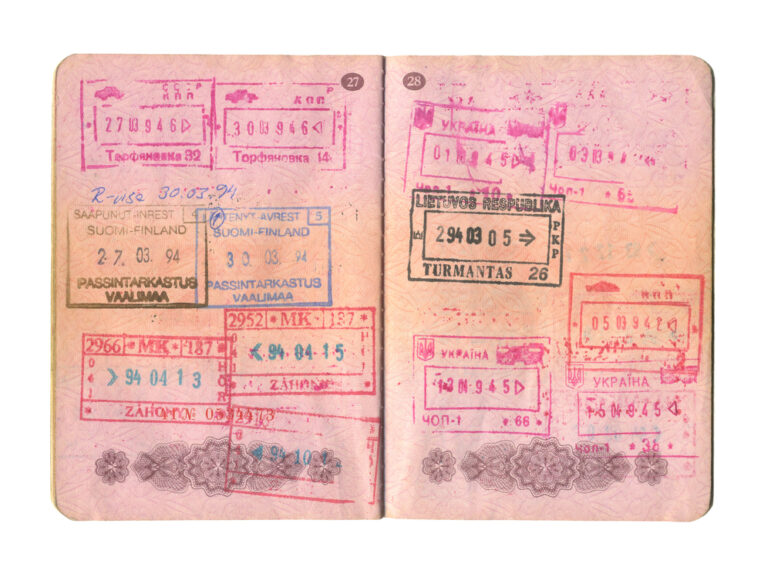নাগরিক অনুসন্ধান: অনুসন্ধান পরিকল্পনা ও পরিচালনা
আর্টিকেলটি পড়ুন এই ভাষায়:
গাইড রিসোর্স
নাগরিক অনুসন্ধান গাইড
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
নাগরিক অনুসন্ধান গাইড: ভূমিকা
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
নাগরিক অনুসন্ধান: অনুসন্ধান পরিকল্পনা ও পরিচালনা
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
নাগরিক অনুসন্ধান: নৈতিকতা ও সুরক্ষা
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
নাগরিক অনুসন্ধান: ইন্টারনেটে খোঁজ
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
নাগরিক অনুসন্ধান: ব্যক্তি নিয়ে গবেষণা
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
নাগরিক অনুসন্ধান: কর্পোরেশনের মালিক কারা
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
নাগরিক অনুসন্ধান: সরকারি নথিপত্র নিয়ে অনুসন্ধান
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
নাগরিক অনুসন্ধান: রাজনীতিবিদদের নিয়ে অনুসন্ধান
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
নাগরিক অনুসন্ধান: সম্পত্তির মালিকানার খোঁজ-খবর
অনুসন্ধান: যে কৌশল শেখা যায়
সাংবাদিকদের বিভিন্ন অনুসন্ধান পরিচালনার কৌশল শিখতে হয়। নাগরিকেরাও এটি শিখে নিতে পারেন।
নাগরিক অনুসন্ধানকারীদের প্রায়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সুবিধা থাকে। তা হলো: প্রেরণা। তারা এই কাজে নামতে পারেন নির্দিষ্ট কোনো ক্ষোভ-বিরক্তির জায়গা থেকে, বা কোনো সন্দেহ-সংশয়, বা বিশেষ আগ্রহ থেকে। যে কারণেই হোক, এরকম কোনো প্রেরণা বা লক্ষ্য সামনে থাকাটা অনেক বড় সুবিধা।
নাগরিক অনুসন্ধানকারীদের আরেকটি বড় সুবিধা: স্থানীয় বা কোনো বিষয়ের ওপর বিশেষ জ্ঞান থাকা। নিজের কোনো ভাবনা নিয়ে চিন্তা করা এবং লক্ষ্য যাচাই করার কাজটি জটিল। কোনো একটি প্রশ্ন মাথায় নিয়ে শুরু করলে গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়। এরপর আসে আরও কিছু মৌলিক ধাপ। যার মধ্যে রয়েছে:
- প্রশ্নটি থেকে উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা কেমন, তা যাচাই করা;
- বিভিন্ন জিনিস খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা;
- বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করা;
- খুঁজে পাওয়া বিষয়গুলি একজায়গায় করা এবং তা মূল্যায়ন করা
- একটি উপসংহার টানা
আমরা এই সবগুলো বিষয় নিয়েই পরামর্শ দেব। কিন্তু এটি আসলে একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। বিশ্বজুড়ে কাজ করা অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন গাইডবুক ও লেখাপত্র থেকে তৈরি করা একটি সারসংক্ষেপ এখানে তুলে আনা হয়েছে।
বিভিন্ন অনুসন্ধানী কৌশল সম্পর্কে আরও গভীরে জানতে, দেখুন জিআইজেএনের তৈরি করা ম্যানুয়ালের তালিকা। যেগুলি লেখা হয়েছে সাংবাদিকদের উদ্দেশে। তবে অন্য যে কোনো পেশার মানুষের জন্যও এগুলোর দরজা খোলা আছে।
এই গাইডজুড়ে যে একটি পরামর্শ বারবার দেওয়া হয়েছে, তা হলো: অনুসন্ধান পরিচালনার কোনো নির্দিষ্ট একক পদ্ধতি নেই, এবং প্রায়ই নতুন পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন পরিকল্পনার প্রয়োজন পড়বে।
মনস্থির ও প্রশ্ন প্রস্তুত করা
কোনো কিছু খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রশ্ন করতে পারাটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক প্রশ্ন করতে পারা একই সঙ্গে অনুপ্রেরণাও জোগায় এবং অনুসন্ধানী প্রক্রিয়াকে শৃঙ্খলায় রাখে। প্রশ্নটি যে একেবারে সঠিক হতে হবে– এমন নয়। কারণ আপনি তো অজানা একটি বিষয়ের খোঁজ করতে যাচ্ছেন। এটিকে খুবই যুৎসই-ও হতে হবে না। তবে খেয়াল রাখতে হবে এটি যেন একেবারেই সাধারণ না হয়ে যায়।
আপনি আসলেই কী জানতে যাচ্ছেন? আপনি কোন জিনিসটার খোঁজ করছেন?
প্রশ্নটিকে একটি তত্ত্ব, একটি অনুমান (হাইপোথিসিস) হিসেবে কাঠামোবদ্ধ করাটা জরুরি। এটি সংক্ষিপ্ত আকারে কোথাও লিখে রাখুন, বা এমনকি কোথাও পিন করেও রাখতে পারেন। কিছু সাংবাদিক তাদের প্রতিবেদনের শুরুটাও লিখে রাখতে পছন্দ করেন, যেন তাদের অনুমানটিই সত্যি।
কোনো একটি প্রশ্ন ধরে অনুসন্ধান শুরু করলে এটি আপনাকে আগে বাড়তে সাহায্য করবে। সামগ্রিক একটি প্রশ্ন থেকে আরও অনেক ছোটোখাটো প্রশ্ন তৈরি হবে। আপনি এমনকি বেশ কিছু বিকল্প হাইপোথিসিসও ভেবে রাখতে পারেন। হাইপোথিসিস তৈরি করা, কোনো পক্ষ নেওয়ার মতো বিষয় নয়। তবে কী ঘটে চলেছে, তা নিয়ে খুব সংকীর্ণ অনুমান/তত্ত্ব থাকলে, তা হয়তো আপনাকে অন্য আরও অনেক যুক্তি-তথ্য বিবেচনায় নেওয়া থেকে বিরত রাখবে। তথ্যপ্রমাণ যদি অন্য কিছুর দিকে ইঙ্গিত করে, তাহলে অবশ্যই আগের হাইপোথিসিস পর্যালোচনা করতে হবে। কারণ তথ্য দিয়েই প্রতিবেদন তৈরি হয়।
এটিই কোনো অনুসন্ধান পরিচালনার অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। সন্দেহ-সংশয় জারি রেখে সামনে এগোনো, এবং একইসঙ্গে যেকোনো তথ্যপ্রমাণকেই মুক্তভাবে গ্রহণ করতে পারা। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যদি আপনার কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে বা অনুসন্ধানের বিষয়টি নিয়ে ব্যক্তিগত কোনো ঘাত-প্রতিঘাত থাকে। যেসব প্রমাণাদি আপনার হাইপোথিসিসের বিপক্ষে যায়, সেগুলোকেও আপনার বিশ্লেষণে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। মনে রাখবেন: কোনো অনুসন্ধানের মাধ্যমে যেমনটা আশা করেছিলেন, তার চেয়ে ভিন্ন কোনো দিকে হয়তো আপনি চলে যাবেন। আরও মনে রাখুন: পৃথিবীটা খুব জটিল জায়গা। এখানে সব খারাপ মানুষেরাই ততটা খারাপ নন, আবার ভালো মানুষেরাও সবসময় ততটা ভালো নন।
গবেষণা শুরু করবেন যেভাবে

শুরুর এই পর্যায়ে চিন্তা করুন, আপনি কী কী জানেন না। এবং লিখে ফেলুন: কোন কোন জিনিস আপনি খুঁজে পেতে চান।
আরেকভাবে বলা যায়: কোন তথ্যগুলো আপনার হাইপোথিসিস যাচাইয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ?
বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা ফলপ্রসু হয়।
অনেক অনুসন্ধানকারীই মানুষ নিয়ে গবেষণা শুরুর আগে কাগজপত্রের গবেষণা (পেপার রিসার্চ) সেরে ফেলতে পছন্দ করেন। সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়ার আগে নথিপত্র দেখে নিন। তবে অনেক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও কার্যকর হতে পারে। যেমন, কোনো বিষয়ের ওপর মৌলিক ধারণা পেতে আপনি আগেই কথা বলতে পারেন কোনো বিশেষজ্ঞের সাথে।
অনুসন্ধানের বিষয়টি নিয়ে আগে থেকে কী কী লেখাপত্র আছে, সেগুলো ঘেঁটে দেখুন।
এভাবে পড়তে পড়তে জানার চেষ্টা করুন এসব বিষয়ে:
- বিষয়টির মৌলিক ঘটনাগুলো কী
- প্রাসঙ্গিক ইতিহাস ও পরিসংখ্যান
- অনুসন্ধানের জায়গাটিতে কোন ভাষায় কথা বলা হয়
- প্রধান চরিত্রগুলো কারা
মনে রাখুন এই ধ্রুপদী প্রশ্নগুলো: কে? কী? কোথায়? কখন? কেন?
যে প্রশ্নগুলো করতে হবে
এভাবে ক্রমাগত নিজেকে এই প্রশ্নগুলো করতে থাকুন:
- এ বিষয়ে কি কোনো উন্মুক্ত নথি/ডেটা আছে? থাকলে কোথায় আছে?
- সবার জন্য উন্মুক্ত অবস্থায় নেই, এমন কী ধরনের কাগজপত্র বা ডেটা থাকতে পারে?
- এসব কাগজপত্র ও ডেটা কোথায় রাখা আছে?
- এর সঙ্গে কারা জড়িত?
- তারা একে অপরের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত? (কিছু গবেষক ম্যাপও তৈরি করেন)
- সেখানে তাদের কী ধরনের স্বার্থ আছে?
- সাধারণ মানুষ আপনাকে এ বিষয়ে কী বলতে পারে?
- ঘটনাগুলো প্রত্যক্ষভাবে কোন জায়গায় ঘটেছিল?
- এগুলোর পরিণতি কী?
- কারা এখান থেকে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?
এভাবে আপনি যত গভীরে যাবেন, ততই আপনার লক্ষ্যকে সুনির্দিষ্ট করে তুলতে পারবেন।
পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কাজের প্রতিটি ধাপের জন্য সময় নির্ধারণ করুন। এবং অগ্রাধিকার তৈরি করুন।
অনেক গবেষকই আগে বিষয়টি সম্পর্কে জানাবোঝা করে নিতে চান। ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রধান মানুষদের মুখোমুখি হওয়ার আগে প্রমাণাদি সংগ্রহ করে নিতে চান।
আপনার সময়সূচি কেমন হবে, চিন্তা করে নিন। কোন কাজগুলোতে বেশি সময় লাগতে পারে? যেমন কোনো জায়গায় যাওয়া, বা কোনো নথিপত্রের জন্য আবেদন করা।
সাক্ষাৎকার গ্রহণ
অনুসন্ধানকারীর টুলবক্সের অন্যতম প্রধান কার্যকরী টুল হলো সাক্ষাৎকার।
সাক্ষাৎকারে সাফল্যের প্রধান বিষয় হলো ভালো প্রস্তুতি ও মনোযোগ দিয়ে শোনা। ভালো আলাপচারিতার মতো ভালো সাক্ষাৎকারও এক ধরনের শিল্প।
সাক্ষাৎকারের কিছু উপাদান এবার বিস্তারিতভাবে দেখা যাক। আরও গাইডলাইনের জন্য দেখুন সাক্ষাৎকার নিয়ে জিআইজেএনের রিসোর্স পেজ।
ভালো প্রস্তুতি: যার সাক্ষাৎকার নিতে যাচ্ছেন, তিনি কী কী বিষয় জানতে পারেন; তার মোটিভেশন কী? এবং আপনি কী জানতে চান- এই বিষয়গুলি বিবেচনায় নেওয়ার মাধ্যমে শুরু হয় এই প্রথম ধাপ। সাক্ষাৎকারদাতার জন্য সুবিধাজনক- এমন কোনো জায়গা বেছে নিন। তাকে স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিন, এবং আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলুন।
মৌলিক রীতিনীতি: আপনি কে, কেন আপনি বিষয়টি নিয়ে আগ্রহী, এবং এসব তথ্য নিয়ে কী করবেন- ইত্যাদি তাকে ব্যাখ্যা করুন। তথ্যগুলোর ব্যবহার নিয়ে দুই পক্ষকে একমত হতে হবে। তথ্যগুলো কার বরাতে যাবে? নাম উল্লেখ করা হবে কিনা? এতে তারা সুরক্ষা-ঝুঁকিতে পড়বেন কিনা; ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।
ভালো প্রশ্ন: প্রশ্নগুলো লিখে ফেলা এবং সেগুলো যৌক্তিকভাবে সাজিয়ে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হয়। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ ছোট, হালকা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে চান। নিরপেক্ষ, ওপেন এন্ডেড প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। তবে কোনো বিষয়ে খোঁজ করা বা অনুভূতির বিষয়ে প্রশ্ন করতে দ্বিধা করবেন না। “কীভাবে,” “কেন,” এবং “কী”- এ ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। ছোট, একটি বিষয়ের ওপর প্রশ্ন সবচেয়ে ভালো। উত্তরগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুরুন এবং সম্পূরক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।
কমবয়েসী বা ঝুঁকির মুখে থাকা মানুষদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় বিশেষ যত্ন নিন। এ বিষয়ে ভালো কিছু পরামর্শ পাবেন জিআইজেএনের মানবপাচার নিয়ে অনুসন্ধানের রিসোর্স পেজে।
যেসব জায়গায় সম্ভব, সাক্ষাৎকারগুলো রেকর্ড করুন। না হলে, ভালোভাবে নোট নিন।
কাছে একটি নোটবুক ও কলম রাখুন। ক্যামেরা ব্যবহার করুন। বিভিন্ন কাগজপত্রের ছবি তোলার ক্ষেত্রেও এটি কাজে লাগে।
গবেষণা সংক্রান্ত এসব ফলাফলের যথার্থ রেকর্ড রাখাই হবে আপনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
আপনি কত ভালোভাবে আপনার তথ্য ও নথিপত্র গুছিয়ে রাখতে পেরেছেন– তার ওপরই নির্ভর করবে আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা।
নানাবিধ বিপদআপদ থেকে কীভাবে নিজেকে ও সোর্সকে রক্ষা করবেন, সেগুলোও চিন্তা করুন। প্রাথমিক ধাপ হবে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা এবং এনক্রিপ্টেড ফোন কল করা। এ জাতীয় সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার জন্য দেখুন এই গাইডের ডিজিটাল নিরাপত্তার অধ্যায়।
গবেষণা: নথিপত্রের খোঁজ
অনুসন্ধানের বিষয়টি নিয়ে আগে থেকেই কী কী প্রকাশিত হয়েছে, তা শুরুতেই দেখে না নেওয়ার ভুল অনেক অনুসন্ধানকারীই করে থাকেন। আগের কোনো জিনিস নতুন করে তুলে আনবেন না। আগে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন, সরকারি নথিপত্র, স্থানীয় আর্কাইভ এবং অন্যান্য আরও যতো প্রকাশিত তথ্য পাওয়া যায়; সব কিছু ভালোমতো দেখে নিন। নিশ্চিত হয়ে নিন যে প্রকাশিত সব কিছু সম্পর্কে আপনার ভালো ধারণা আছে। এবার এই বোঝাপড়ার ওপর দাঁড়িয়ে কাজ শুরু করুন।

আধুনিক সময়ে শুরুতেই ইন্টারনেটে খোঁজ করার প্রবণতা দেখা যায়। যেটি খুবই যথার্থ।
কিন্তু মনে রাখতে হবে: সব কিছু অনলাইনে পাওয়া যাবে না। যেমন, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়: কিছু সরকারি নথিপত্র শুধু হাতে হাতেই নেওয়া সম্ভব, সরকারি অফিসে গিয়ে।
এছাড়াও, অনলাইনে পাওয়া কোনো তথ্য বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে। ফলে সোর্সটি বিশ্বস্ত কিনা এবং তথ্যটি কীভাবে যাচাই করা হয়েছে– তা মূল্যায়ন করুন।
কাঙ্ক্ষিত তথ্যটি কোথায় পেতে পারেন, তার বিকল্প কিছু জায়গাও ভেবে রাখুন:
- জাতীয় সরকারের বিভিন্ন সংস্থার নথিপত্র ছাড়াও কোনো আদালতের বা রাজ্য ও স্থানীয় পর্যায়ের নথি আছে কিনা?
- কারা এসব কাগজপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে রাখতে পারে? কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, শৌখিন মানুষজন, একাডেমিক ও পেশাগত অ্যাসোসিয়েশনগুলোতে খোঁজ করা ফলপ্রসূ হতে পারে।
- পুরনো সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন ঘাঁটাও অনেক কাজের হতে পারে।
- আপনার ভালো বন্ধু হতে পারেন লাইব্রেরিয়ান ও অ্যাক্টিভিস্টরা।
ভালো কোনো অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য চাই কল্পনাশক্তি।
যদি কোনো রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য অন্য সোর্সের খোঁজ করুন। যদি কাঙ্ক্ষিত নথিটি হাতে না পান, তাহলে খোঁজ করুন: অন্য কীভাবে তথ্যটি পেতে পারেন। হয়তো সেখানে দুইটি পক্ষ জড়িত আছে। যেমন সরকার ও ঠিকাদার। এসব কাজের জন্য আপনাকে সহনশীল, চটপটে, করিৎকর্মা হতে হবে।
সরকার কোনো তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে- এটিকেই শেষ বলে ধরে নেবেন না। তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সেই তথ্যের জন্য আবেদন করার কথা ভাবতে পারেন। তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করে- এমন স্থানীয় কোনো গ্রুপের সাহায্য নিয়ে এই আবেদন করতে পারেন।
এই গাইডের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে: ইন্টারনেটে কার্যকরী গবেষণা চালানোর উপায়-কৌশল এবং বিভিন্ন ব্যক্তি-কর্পোরেশন-সরকার সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের করার কিছু টুল পরিচিতি। সাংবাদিকেরা যখন “ওপেন সোর্স অনুসন্ধানের” কথা বলেন, তার অর্থ: সবার জন্য উন্মুক্ত থাকা তথ্য খুঁজে বের করার কলাকৌশল ব্যবহার।
নদীর পানি পরীক্ষা করে যা পেল এক কানাডিয় মেয়ে
১১ বছর বয়সী স্টেলাকে নিয়ে সংবাদ শিরোনাম হয়েছিল: একটি শিশু যেভাবে নদী দূষণ থামিয়েছে। কানাডার নোভা স্কশিয়ায়, নিজের বাড়ির পাশের লাহ্যাভ নদী থেকে পানির নমুনা সংগ্রহ করে সেটি পরীক্ষা করেছিল স্টেলা।
গভীরভাবে খতিয়ে দেখুন
গবেষণা করার সময়, সংশয়ী থাকুন। অর্থবাণিজ্যের ভাষায় যেমনটি বলা হয়, “ডিউ ডিলিজেন্স”-এর চর্চা করুন। সব নথিপত্র যে আসল– তা নিশ্চিত করুন। তথ্যগত অসঙ্গতি ও ধারাবাহিকতা না থাকার মতো বিষয়গুলো নিয়ে সতর্ক থাকুন।
গবেষণা প্রক্রিয়ার এই পুরো সময়জুড়ে, সতর্ক থাকুন। আপনি যা শুনছেন, তা ভুলও হতে পারে। সঠিক তথ্যটি নিশ্চিতভাবে যাচাই করে নিতে হবে। সোর্সের কাছ থেকে শোনা কোনো কথাকেও প্রশ্ন করা উচিৎ। কোনো ছবির সত্যতা হয়তো যাচাই করে নিতে হতে পারে। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে দেখা যেতে পারে: নথিটিই তৈরি করা হয়েছে জালিয়াতি করে। ফলে সব কিছুর সত্যতা নিশ্চিত করতে হবে এবং যাচাই করে নিতে হবে।
“প্রাইমারি” বা প্রাথমিক নথিপত্র হলো সেসব আসল নথিপত্র, যা আপনার অনুসন্ধানের বিষয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণ দেয়।
এরকম নথিপত্র থেকে তথ্য বের করার সময় এর আদি সূত্রের খোঁজ করুন। ফুটনোট অনুসরণ করুন। সোর্সের বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখুন। নথিটি কে লিখেছেন, তার খোঁজ করুন। সেই লেখকের বা গবেষণাটির কোনো সমালোচনা হয়েছে কিনা– খেয়াল করুন।
জটিল নথিপত্র বোঝার ক্ষেত্রে আপনার হয়তো অন্য কারো সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে। বিশেষত যেসব নথিপত্রের সঙ্গে যদি কারিগরী, আমলাতান্ত্রিক, আইনি ও অর্থনৈতিক বিষয়আশয় জড়িত থাকে। সেগুলো বোঝার জন্য কোনো বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করার সময়ও মনে রাখুন: তাদের কাছ থেকে শুধু প্রাসঙ্গিক জ্ঞান ও মতামতই পাওয়া যাবে না, একই সঙ্গে তারা আপনাকে অন্য কোনো নথি দেখার বা বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন। সোর্সকে সব সময় এ ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন: আর কোন কোন জিনিস আমার পড়া উচিৎ? আর কার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি? কে সত্যিই ঘটনাটি দেখেছিল?
“সেকেন্ডারি” বা আনুষঙ্গিক সোর্স বলতে ধরা হয় বিভিন্ন প্রকাশিত লেখাপত্র, ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট। এগুলো খুব বেশি নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে। এখানে আপনাকে অন্যের কাজের ওপর ভরসা করতে হচ্ছে। ফলে, সব কিছু যাচাই করে নিন।
প্রায়ই দেখা যায়, নাগরিক অনুসন্ধানকারীরা তথ্যের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে ঝুঁকছেন। এরকম “ক্রাউডসোর্সিং” বেশ কাজের হতে পারে, কিন্তু সেগুলোর সত্যতাও যাচাই করে নেওয়া প্রয়োজন।
গবেষণা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয় এবং অনুসন্ধানও হয়ে পড়তে পারে ক্লান্তিকর। কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় সামনে এগুনোর রাস্তা হতাশাজনকভাবে বন্ধ। এটিই এই কাজের ধারা।
শুরুতে স্থির করা লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে হয়তো আরও উদ্যমী হয়ে উঠতে পারেন। এই পর্যায়ে এসে আপনাকে হয়তো কিছু নতুন প্রশ্ন ও হাইপোথিসিস তৈরি করতে হবে। একই সঙ্গে, নতুন কী বিষয় ঘটে চলেছে, সেগুলোর দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুন।
এভাবে অতীত ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট নিয়ে গবেষণার পর আপনাকে তৈরি হতে হবে সাক্ষাৎকারের জন্য। গবেষণা থেকে আপনার কিছু নাম পাওয়ার কথা, যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
বিষাক্ত বর্জ্য নিঃসরণ যেভাবে নথিভুক্ত করেছে একটি মার্কিনী পরিবার
বিষাক্ত সব রাসায়নিকের কারণে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া কমিউনিটির মানুষের ওপর কেমন স্বাস্থ্যগত প্রভাব পড়ছে– তা লিপিবদ্ধ করার কাজ শুরু করেছিলেন আয়নি আমজাদের বাবা-মা। তিনিও কাজটি চালিয়ে গেছেন এবং পরবর্তীতে এ নিয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অ্যাডভোকেসি করেছেন। ওয়াশিংটন পোস্টে উঠে এসেছিল চিকিৎসক আমজাদের এই গল্প।
সূত্র
মোক্ষম কোনো নথিপত্র হাতে না থাকলে, বেশিরভাগ অনুসন্ধানেই প্রয়োজন হয় নির্ভরযোগ্য সূত্র ও বিশেষজ্ঞদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-জ্ঞান, এবং দৃষ্টিভঙ্গি।
ওপেন সোর্স গবেষণা ও মানুষের সঙ্গে কথা বলার মাধ্যমে, সম্ভাব্য সূত্রদের চিহ্নিত করুন। তারা হতে পারে এমন কেউ:
- বিশেষজ্ঞ, যারা এ বিষয়ে কথা বলেছেন বা লিখেছেন;
- কর্মকর্তা। কিন্তু শুধু উঁচু পদের কর্মকর্তাদের কথাই ভাববেন না;
- ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের পক্ষ;
- অ্যাডভোকেটস, যারা এই বিষয়টির ওপর কাজ করছেন, যেমন নাগরিক বা পেশাজীবী কোনো গ্রুপ
- “সাবেক”, যারা পূর্বে এই ঘটনার বা বিষয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, যেমন সাবেক কর্মী।
সম্ভাব্য সব সম্পর্কের কথা চিন্তা করুন:
- কারা এই ঘটনা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে? ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে?
- কে লাভবান হয়েছে?
- কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?
- কে এ ব্যাপারে কিছু শুনেছে বা দেখেছে?
- কারা এ নিয়ে কথা বলতে আগ্রহী হতে পারে?
কিছু অনুসন্ধানকারী এসব সম্পর্ক ভালোভাবে বোঝার জন্য ম্যাপ তৈরি করেন। সম্ভাব্য সূত্রদের তালিকা রাখার জন্য স্প্রেডশিট অনেক উপকারী হতে পারে।
তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য আপনি কতজন সূত্র ব্যবহার করছেন, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। সর্বনিম্ন বিবেচনা করা হয় দুজন সূত্রকে। তবে আরও বেশি হলেই ভালো।
বিস্তৃত পরিসরের সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হলে, তা শুধু তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতাই নিশ্চিত করে না, এর মাধ্যমে সাধারণত আরও বিস্তারিত তথ্যও পাওয়া যায়। এবং তথ্যে কোথাও ঘাটতি বা তারতম্য থাকছে কি না, তাও বোঝা যায়। আপনি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে কোনো কিছু দেখে থাকতে পারেন। সেটাও ব্যবহার করা যাবে।
সোর্স কারা, তা বিবেচনা করুন। তাদের নিয়েও গবেষণা করুন। এই “বিশেষজ্ঞের” কি সত্যিই এ বিষয়ে কথা বলার যোগ্যতা আছে? তার কি এখানে কোনো স্বার্থ জড়িত আছে? তারা কে? তাদের এজেন্ডা কী? “প্রত্যক্ষদর্শী” কি সত্যিই ঘটনাটি দেখেছে, নাকি অন্য কারো কাছ থেকে শুনেছে? তাদের দেওয়া ভাষ্যগুলোও যাচাই করুন।
একজন সোর্স গড়ে তুলতে হয়তো সময় লাগতে পারে, বিশেষভাবে যদি বিষয়টি সংবেদনশীল হয়। সোর্সদের ভয়-ভীতির প্রতি সংবেদনশীল হোন। কেউ সামনে এগিয়ে এসে কথা বলবে, এমন পরিস্থিতি তৈরির জন্য হয়তো আগে বেশ কয়েকবার সাক্ষাতের প্রয়োজন হতে পারে। এই সম্পর্কগুলো প্রায়ই গড়ে ওঠে বিশ্বাসের ওপর। এবং সেটি গড়ে তুলতে পারার বিষয়টি আপনার ওপরই নির্ভর করবে।
সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা নিয়ে আরও আলোচনার জন্য দেখুন, তৃতীয় অধ্যায়।
ভালোভাবে নোট নিন। যেখানে সম্ভব, সাক্ষাৎকারগুলো রেকর্ড করুন। কিন্তু তারপরও নোট নিন।
শুধু মানুষের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি, ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে জড়িত জায়গাগুলো ঘুরে দেখাও কাজের হবে। “মাঠ পর্যবেক্ষণ” থেকে কখনো কখনো অপ্রত্যাশিত সব ফলাফল বেরিয়ে আসতে পারে। কোনো সরকারি প্রতিবেদন যথার্থ কিনা, তা যাচাই করে দেখার জন্য সেই জায়গার বাস্তবতার সাথে সেটি মিলিয়ে দেখতে পারেন। আপনার হয়তো এমন কিছু মানুষের সঙ্গে আকস্মিক দেখা হয়ে যাবে, যারা সাহায্য করতে পারে।
গবেষণা লিপিবদ্ধ করুন
অনলাইন থেকে বা মানুষের সঙ্গে কথা বলার মাধ্যমে; তথ্য যেভাবেই পান না কেন, সেটি ভালোভাবে সাজিয়ে রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ।
তথ্যের সত্যতা এবং তথ্যটি কোন সোর্স থেকে পেয়েছেন– সেগুলো যেন যে কোনো সময় বের করতে পারেন, তা নিশ্চিত করুন। গবেষণা ও যোগাযোগ সংক্রান্ত সব কিছুর রেকর্ড রাখুন। এর অর্থ: কাগজপত্র সংরক্ষণ করা এবং সেটি কোথায় থেকে পেয়েছেন, তা লিপিবদ্ধ রাখা। অনলাইন থেকে পাওয়া অনেক নথিপত্র পরবর্তীতে আর নাও পাওয়া যেতে পারে। ফলে সেগুলো প্রিন্ট বা ডাউনলোড করে রাখলে এসব দিক দিয়েও সুরক্ষা পাওয়া যায়। সব কিছুর রেকর্ড রাখার অর্থ: কোন তথ্যটি কার কাছ থেকে, কোথায় শুনেছেন, তার সার্বিক ধারণা রাখা। এবং ভালোভাবে নোট নেওয়া।
এভাবে আপনার অনুসন্ধান সংক্রান্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার ফল পরবর্তীতে পাওয়া যাবে। সব কিছু ভালোভাবে লেবেল করে রাখা, ফাইলবদ্ধ করে রাখার (তা সে কাগজপত্রে হোক বা ডিজিটালি) চর্চা করা ভালো ব্যাপার। ভালোভাবে গুছিয়ে রাখা একটি আর্কাইভ আপনাকে এটি বুঝতে সাহায্য করবে যে: আপনি কী কী জানেন এবং কী কী এখনো জানেন না। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ একটি মাস্টার ফাইল তৈরির পরামর্শ দেন, যেটি বলে দেবে: কোন জিনিস কোথায় আছে।
শেষ কথা
সাংবাদিকেরা সাধারণত কোনো অনুসন্ধান শেষে একটি প্রতিবেদন লেখেন বা সম্প্রচারের জন্য ভিডিও তৈরি করেন। কিন্তু নাগরিক অনুসন্ধানকারীরা কোনো প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, ব্লগ পোস্ট, বা সম্পাদকের কাছে চিঠি; যে কোনো কিছুই লিখতে পারেন। অথবা অনুসন্ধান থেকে পাওয়া প্রমাণাদি নিয়ে আইনি বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছেও যেতে পারেন।
নির্দিষ্ট সেই মাধ্যমটি যা-ই হোক না কেন, আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন: এই যোগাযোগটি কার্যকরীভাবে করতে।
অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত ফলাফল স্পষ্টভাবে ও সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পারাটা সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ।
কীভাবে আপনি সব কিছু সাজিয়েছেন, তা চিন্তা করুন। সত্যিকারের এবং পরীক্ষিত কাঠামো হচ্ছে: গল্পটা পর্যায়ক্রমিকভাবে বলা। তবে অন্য কোনো পদ্ধতিও কাজ করতে পারে। লেখা শুরুর আগে, একটি আউটলাইন তৈরি করে নিন। এতে আপনার লেখার কাজে সাহায্য হবে। পরবর্তীতে অবশ্য এটি পরিবর্তনও করতে পারেন।
নতুন করে লেখার খসড়া তৈরির সময় চিন্তা করুন তথ্যগত কোনো ফাঁক থেকে যাচ্ছে কিনা। এবং আপনার সব তথ্য যে সঠিক ও সূত্র-নির্ভর, তা নিশ্চিত করুন। মানুষের ও জায়গার নাম সঠিকভাবে লিখুন। ছোটখাট কিছু ভুলও বিশ্বাসযোগ্যতা কমিয়ে দেয়। অন্য কোনো জায়গা থেকে লেখা হুবহু তুলে আনেননি তো? সোর্সের সঙ্গে কোনো সমঝোতার ব্যত্যয় ঘটেনি তো?
লেখার সময়, এবং পরবর্তীতে সম্পাদনার সময় নিজেকেই জিজ্ঞাসা করুন: নতুন যে পাঠক এটি প্রথমবারের মতো পড়বেন, তার জন্য সব কিছু স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা। প্রতিবেদনটি পাঠকের কাছে অর্থবহ হয়ে উঠবে কিনা।
অপ্রাসঙ্গিক শব্দ-বাক্য ও উপাদান বাদ দেওয়ার কথা বিবেচনা করুন। সম্পাদকরা প্রায়ই ফ্লো অ্যান্ড রিদমের কথা বলেন, যেখানে একটি “ভাষ্য” পাঠককে সামনে নিয়ে যায়। ছবি, চার্ট ও অন্যান্য ভিজ্যুয়ালাইজেশনও গল্পটি ভালোভাবে বলতে সাহায্য করবে।
লেখালেখির শেষপর্যায়ের দিনগুলোতে আপনাকে সব তথ্য বারবার যাচাই করে দেখতে হবে। এবং অনুসন্ধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে হবে যাদের সঙ্গে আপনি হয়তো আগে কথা বলতে চাননি।
বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত ও অপরিচিত; দুই ধরনের মানুষকেই বলুন আপনার প্রতিবেদনটি সমালোচকের দৃষ্টিতে পড়ে দেখার জন্য।
একজন সৎ আইনজীবী নানাবিধ উঁচু মাত্রার আইনি মানদণ্ড দিয়ে বাঁধা থাকেন। যেমন, “সব সংশয়ের উর্ধ্বে” প্রমাণাদি আছে কিনা, বা “সম্ভাব্যতার ভারসাম্য” কোনো এক পক্ষের দিকে হেলে যাচ্ছে কিনা। তবে অনুসন্ধানকারী হিসেবে আপনার এধরনের কোনো বাধাবন্ধন নেই। যদিও বিভিন্ন তথ্যের যথার্থতা নিশ্চিত করার জন্য এগুলো বেশ কাজের। এবং আপনি যদি অনুসন্ধানের ফলাফল কোনো আইনজীবীর কাছে বা আদালতে পেশ করতে চান, তাহলেও বিষয়গুলো মাথায় রাখতে পারেন।
এই রাস্তায় পরবর্তীতে কী আসতে যাচ্ছে, তা খেয়াল রাখুন। কোনো তথ্যের জন্য আপনার বিরুদ্ধে কি মানহানির অভিযোগ আসতে পারে? আপনার এই অনুসন্ধানের পরিণতি কী হতে পারে? নিজের ও সংশ্লিষ্ট মানুষদের নিরাপত্তার কথাও চিন্তা করুন।
সব মিলিয়ে, আপনি কি আপনার অনুসন্ধানের ফলাফল নিয়ে সন্তুষ্ট? আপনি কি এর পেছনে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন?
এই কাজের জন্য আপনার প্রশংসাও হতে পারে, সমালোচনাও হতে পারে।
অনুসন্ধান খুব কালেভদ্রে একেবারে চূড়ান্তভাবে শেষ হয়। ফলে, কীভাবে আপনি বিষয়টি ফলো-আপ করবেন, তাও ঠিক করে নিতে হবে। কাজটি কি আপনি অনুসন্ধানকারী হিসেবেই করবেন, নাকি একজন অ্যাডভোকেট হিসেবে?
অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার গাইড
অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কীভাবে করতে হয়, তা নিয়ে অনেক ভালো ম্যানুয়াল লেখা হয়েছে। নিচে আমরা সেরা কিছু ম্যানুয়ালের তালিকা দিয়েছি।
আরও অনেক ম্যানুয়াল-হ্যান্ডবুকের হদিশ পাবেন জিআইজেএন রিসোর্স সেন্টারের এই লেখায়।
অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণ নিয়েও লেখাপত্র আছে আমাদের। বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও, এর মূল উপাদানগুলো নিয়ে এক ধরনের ঐক্যমত্য আছে পেশাদার সাংবাদিকতার গ্রুপগুলোর মধ্যে। জিআইজেএনের নির্বাহী পরিচালক ডেভিড ই. কাপলান লিখেছেন, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হলো “সিস্টেমেটিক, ইন-ডেপথ এবং মৌলিক গবেষণা ও রিপোর্টিং, যেখান থেকে প্রায়ই নানাবিধ গোপন জিনিস বেরিয়ে আসে।” (অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কী?) (কাপলানের এই ব্যাখ্যার ভিডিও দেখুন এখানে)
কাপলান লিখছেন:
অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য হচ্ছে গোপন বা লুকিয়ে রাখা তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরা। সাধারণত ক্ষমতাবান কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এসব তথ্য গোপন রাখে; কখনো হয়তো তা বিপুল ও বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে থাকা তথ্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, যা চট করে খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই কাজের জন্য সাংবাদিককে সাধারণত প্রকাশ্য ও গোপন নানা উৎস (সোর্স) ব্যবহার করতে হয়, ঘাঁটতে হয় নানা ধরনের নথিপত্র।
তাহলে, শুরু করা যাক:
“হাইপোথিসিস-ভিত্তিক অনুসন্ধানকে” কেন্দ্রে রেখে লেখা হয়েছে স্টোরি বেজড ইনকোয়ারি: এ ম্যানুয়াল ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস। ২০০৯ সালে এটি প্রকাশ করেছে ইউনেস্কো। মোট সাতটি ভাষায় (আরবি, চীনা, ইংরেজি, ফরাসী, পর্তুগিজ, রাশিয়ান ও স্প্যানিশ) এটি পাওয়া যায়। এখানে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মৌলিক সব পদ্ধতি ও কৌশল আলোচনা করা হয়েছে।
ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম ম্যানুয়াল: এই উপকারী গাইডটি তৈরি করা হয়েছিল আফ্রিকান সাংবাদিকদের হ্যান্ডবুক হিসেবে। যেখানে অনেক কেস স্টাডি ও হাতে-কলমে চর্চার উপাদান আছে। এটি প্রকাশ করেছে জার্মান ফাউন্ডেশন কনরাজ অ্যাডেনাওয়ার স্টিফটুং। এটির সাম্প্রতিক সংস্করণটি প্রকাশ করা হয়েছে বৈশ্বিক প্রেক্ষিত মাথায় রেখে। বিশেষভাবে সেসব রিপোর্টারদের জন্য যারা দমনমূলক গণমাধ্যম আইন, স্বচ্ছতার অভাব ও স্বল্প রিসোর্সের মধ্যে কাজ করছেন। এটি বিভিন্ন ভাষায় ও একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এখানে সব কিছু পর্যায়ক্রমিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন: “ভালো একটি আইডিয়ার পর আপনাকে একটি হাইপোথিসিস তৈরি করতে হবে। অনুসন্ধানী রিপোর্টিং প্রক্রিয়ার পরের ধাপটি হলো: সোর্স ম্যাপিং।”
ফ্রম সিটিজেন রিপোর্টিং টু সিটিজেন জার্নালিজম নামের এই গাইডটি তৈরি করেছে মিডিয়া হেল্পিং মিডিয়া।
ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার্স হ্যান্ডবুক: এ গাইড টু ডকুমেন্টস, ডেটাবেজ এন্ড টেকনিকস। ব্রান্ট হিউস্টন ও যুক্তরাষ্ট্রের ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার্স অ্যান্ড এডিটর্স প্রণীত এই বই অনলাইনে কিনতে পাওয়া যায়।
সাংবাদিকতার মৌলিক কৌশল-দক্ষতা নিয়ে লিখিত অনেক বইয়ের মধ্যে অন্যতম আমেরিকান প্রেস ইনস্টিটিউটের জার্নালিজম এসেনশিয়ালস। এখানে সাংবাদিকদের কাজ, বস্তুনিষ্ঠতা ও যথার্থতা নিয়ে আলোচনা আছে।
দ্য ভেরিফিকেশন গাইড ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস নামের এই গাইডটি তৈরি করেছে ইউরোপিয়ান জার্নালিজম সেন্টার। এখানে আছে ১০টি অধ্যায় ও তিনটি কেস স্টাডি। অনলাইন গবেষণার টুল, ডেটা, ইউজার জেনারেটেড কন্টেন্ট ও নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে গাইডটিতে।
শুধুমাত্র নাগরিকদের উদ্দেশ্য করে তৈরি করা জিনিসপত্র খুব কমই আছে।
এক্সপোজিং দ্য ইনভিজিবল – দ্য কিট: ট্যাকটিকাল টেকনোলজি কালেকটিভের ২০১৯ সালের এই রিসোর্সের কয়েকটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে: কীভাবে একটি অনুসন্ধান পরিচালিত হয়; ইন্টারনেট সার্চিংয়ের অ্যাডভান্সড কৌশল, ওয়েবসাইটের পুরনো বা “হারিয়ে যাওয়া” তথ্য খুঁজে বের করার কৌশল; ওয়েবসাইটের মালিকানা অনুসন্ধান; ম্যাপ ব্যবহার, জিওগ্রাফিক ডেটা, ও তথ্য খুঁজতে ও ভিজ্যুয়ালাইজ করতে স্যাটেলাইট ইমেজের ব্যবহার; সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ থেকে তথ্য বের করা; এবং আরও অনেক কিছু। ট্যাকটিক্যাল টেক বার্লিন-ভিত্তিক একটি এনজিও, যারা মানবাধিকার অ্যাডভোকেটদের প্রশিক্ষণ দেয়।
রেইজিং হেল: এ সিটিজেন’স গাইড টু দ্য ফাইন আর্ট অব ইনভেস্টিগেশন। এটি বেশ পুরনো (১৯৮৩) এবং যুক্তরাষ্ট্র-কেন্দ্রিক। তবে পুরো গাইডজুড়েই পাবেন লড়াকু মনোভাব এবং দারুন সব পরামর্শ।
সিটিজেন জার্নালিজম (উপশিরোনাম: “এ রাফ গাইড টু টেলিং ইন ওয়ার্ড এন্ড ইমেজ”) অস্ট্রেলিয়ার “স্বাধীন অনলাইন ও ফটো সাংবাদিক” রুস গ্রেসনের লেখা বেশ কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন।
এথিকস ফর দ্য সিটিজেন জার্নালিস্ট। সাংবাদিক ইসাবেলা গুবাসের এই বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে: কীভাবে অনুসন্ধানে আগ্রহী যে কারো জন্য সাংবাদিকতার মৌলিক কিছু মানদণ্ড প্রযোজ্য হওয়া উচিৎ।
শিশুদের কথা কেন চিন্তা করা হবে না? এখানে থাকছে কিশোর-তরুন অনুসন্ধানকারীদের জন্য একটি গাইড। এটি তৈরি করেছে ফিলিপাইনের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রতিষ্ঠান, র্যাপলার।
ডেটার ব্যবহার
ডেটা দিয়ে কীভাবে গবেষণা চালাতে হয়, তা নিয়ে অনেক রিসোর্স পাওয়া যায়।
অনুসন্ধানে কীভাবে ডেটা ব্যবহার করবেন, তা নিয়ে খুবই বিস্তারিত একটি গাইড: দ্য ডেটা জার্নালিজম হ্যান্ডবুক।
ডেটা জার্নালিজম নিয়ে আরও অনেক তথ্য পাবেন জিআইজেএনের রিসোর্স পেজে।
জোটবদ্ধ অনুসন্ধান বাড়ছে
দলবদ্ধ হয়ে গবেষণা, এমনকি পুরো কমিউনিটি মিলে একসঙ্গে কাজ বা গবেষণা করা ক্রমেই সম্ভবপর হয়ে উঠছে। কখনো কখনো এ কাজে সহায়তা করছে বিভিন্ন অনলাইন ডেটা ও অ্যাপ্লিকেশন।
যেমন, কনস্টিটিউয়েন্সি প্রজেক্ট বাস্তবায়নের দিকে নজর রাখার লক্ষ্যে নাগরিকদের জন্য একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব টুল বানিয়েছিল আইনগত ক্ষেত্রের ওয়াচডগ, অর্ডারপেপার নাইজেরিয়া। কনসট্র্যাক নামের এই মোবাইল অ্যাপে এ সংক্রান্ত “অনেক যথার্থ ও যাচাইকৃত তথ্য আছে প্রকল্পটি সম্পর্কে। প্রকল্পগুলোর অবস্থান কোথায়, এটি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থাকে কী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, বাস্তবায়নের অগ্রগতি, এবং সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের প্রোফাইল।”
রাশিয়ান সাইট, টাক-টাক-টাক নাগরিক অনুসন্ধানকারীদের সাহায্য করে, বিনামূল্যে তাদের আইনি পরামর্শ দেয় এবং সাধারণ মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয় (দেখুন টাক-টাক-টাক ইনটেক পেজ)। টাক-টাক-টাক নেটওয়ার্কের যে কোনো নিবন্ধিত ব্যবহারকারীই নতুন কোনো অনুসন্ধান শুরু করতে পারেন বা চলমান কোনো অনুসন্ধানে যোগ দিতে পারেন। যিনি প্রথম একটি অনুসন্ধানের আইডিয়া ঘোষণা দেবেন, তাকে প্রধান অনুসন্ধানকারী হিসেবে উল্লেখ করা থাকবে। তাদের কর্মপ্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন, ওয়েবসাইটের এই অংশটি।
দিস ইজ প্লেস-এর রিপোর্টিং সূত্রে জানা যায়: ভারতে এমন একটি ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাপ বানানো হয়েছে, যেখানে কমিউনিটির সদস্যরা গাছের পরিমাণ, পুড়ে যাওয়া জায়গা, এবং এ ধরনের অন্যান্য পরিবর্তনের ডেটা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারবেন। এতে, গ্রামীন কমিউনিটিগুলো আরও ভালোভাবে তাদের ভূমি রক্ষা করতে পারবে।
ইতালিতে, জনগণের অর্থ বরাদ্দ ও খরচ সংক্রান্ত বিষয়গুলো যেন নাগরিকেরা চোখে চোখে রাখতে পারেন, সেজন্য নেওয়া হয়েছে মোনিথন নামের একটি উদ্যোগ।
কেনিয়ার নাইরোবিতে, তৈরি করা হয়েছে ম্যাপ কিবেরা নামের একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ কমিউনিটি-ভিত্তিক তথ্য প্রকল্প। যেখানে স্থানীয় কমিউনিটিগুলোর জন্য উন্মুক্ত ডিজিটাল ম্যাপ তৈরি করা যায়।
২০১৩ সালের বস্টন ম্যারাথনে বোমা হামলার পর, হাজারো রেডিট ব্যবহারকারী একইসঙ্গে ছবি ও তথ্য বিনিময় করেছিলেন হামলাকারীদের সনাক্ত করার জন্য। সবসময়ই অবশ্য তারা নির্ভুল ফলাফল পান নি।
রাশিয়ায়, নাগরিক অ্যাক্টিভিস্টরা কিছু ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়ম ভঙ্গকারী কর্মকর্তাদের সনাক্ত ও তাদের তথ্য এক জায়গায় করার জন্য। যেমন, বিঅ্যাওয়ার অব দেম এবং ওভিডিইনফো।
সুরক্ষা
অনুসন্ধান করতে গেলে নানাবিধ হুমকির সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি থাকে। ফলে কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন হতে পারে।
অবস্থা খুব চরম আকার ধারণ করলে তৈরি হতে পারে ২০১৮ সালে ভারতের এক গোয়ালার সঙ্গে যেমনটি হয়েছিল, তেমন ঘটনা। তিনি স্থানীয় এক নির্মান প্রকল্পের বিষয়ে তথ্য চেয়েছিলেন তথ্য অধিকার আইনের (আরটিআই) অধীনে আবেদন করে। এজন্য তাকে সশস্ত্র আততায়ীরা খুন করে বলে জানা গেছে একটি গণমাধ্যমের প্রতিবেদন সূত্রে।
জিআইজেএনের রিসোর্স সেন্টারের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিভাগে এ বিষয়ে আরও কিছু দিক-নির্দেশনা পাবেন। সেখানে অভিজ্ঞ সাংবাদিকেরা তাদের বার্তা দিয়েছেন অন্য সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে।
এখানে থাকছে কিছু দরকারী সোর্স:
কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট’স সেফটি কিট: সুরক্ষা সংক্রান্ত সিপিজের এই চার পর্বের সুরক্ষা কিটটি প্রকাশিত হয়েছে ২০১৮ সালে। এখানে অনেক দরকারি টুল ও রিসোর্সের সন্ধান আছে সাংবাদিক ও নিউজরুমের মৌলিক সব শারিরীক, ডিজিটাল ও মানসিক সুরক্ষা নিয়ে। এটি পাওয়া যায় ইংরেজি, স্প্যানিশ, ফরাসী, আরবি, রাশিয়ান, সোমালি, পার্সিয়ান, পর্তুগিজ, চীনা, তুর্কি ও বার্মিজ ভাষায়।
দ্য প্র্যাকটিক্যাল গাইড ফর দ্য সিকিউরিটি অব জার্নালিস্টস তৈরি করেছে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস ও ইউনেস্কো। ২০১৭ সালে এটি হালনাগাদ করা হয়েছে। এটি পাওয়া যায় ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ভাষায়।
ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট সেফটি প্রিন্সিপ্যালস: প্রধান প্রধান সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকতা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি জোটের মাধ্যমে এই নির্দেশনাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে। এটি পাওয়া যায় আরবি, ফরাসি, হিব্রু, পার্সিয়ান, রাশিয়ান, স্প্যানিশ ও তুর্কি ভাষায়।
আর সবশেষে, কোনো জায়গায় আটকে গেলে জিআইজেএনের রিসোর্স সেন্টার তো থাকছেই, যেখানে এক হাজারেরও বেশি টিপশিট ও টুলের খবর পাবেন। বিশ্বজুড়ে অনেক সাংবাদিক আমাদের হেল্প ডেস্কের সহায়তাও নিয়ে থাকেন। তো, শুরু করে দিন অনুসন্ধান! শুভ কামনা!