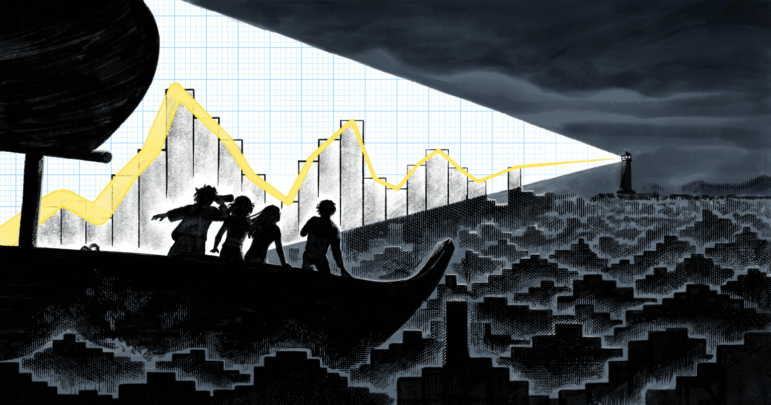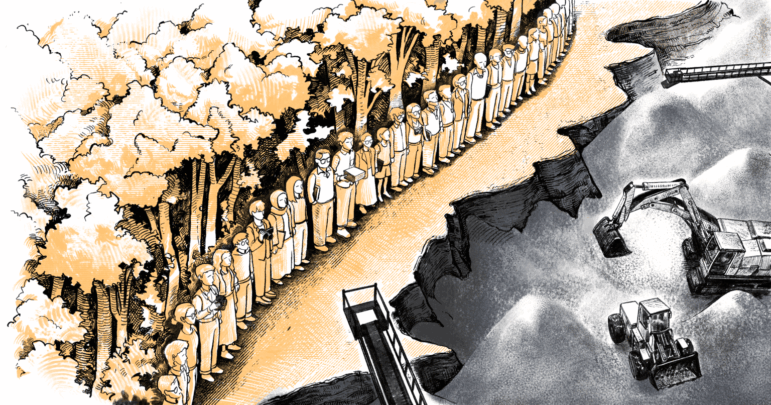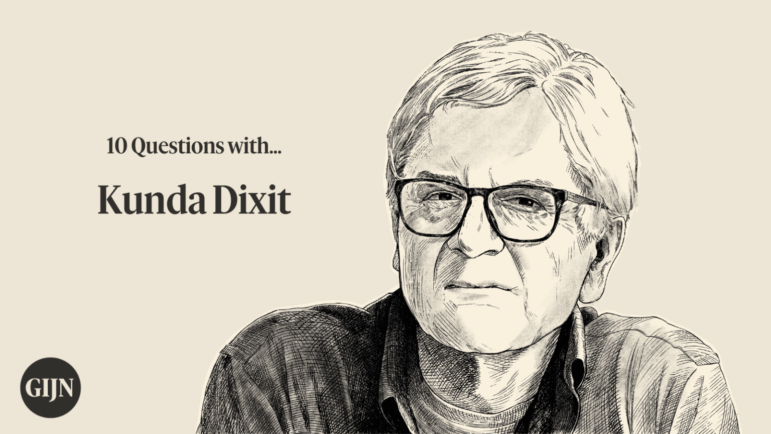নির্বাচন অনুসন্ধান গাইড: সাংবাদিকদের জন্য নতুন কিছু অনুসন্ধানী টুল
আর্টিকেলটি পড়ুন এই ভাষায়:
সম্পাদকের মন্তব্য: এই গাইডটি ২০২৪ সালের নির্বাচন ঘিরে পরিমার্জন ও হালনাগাদ করা হয়েছে। এটি মূলত ২০২২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। আগের সংস্করণের অধ্যায়টি এখানে পড়তে পারেন।
রিপোর্টারদের মধ্যে যারা পরবর্তী নির্বাচন কভার করবেন, নতুন কৌশল হিসেবে তাদের কিন্তু পুরানো বদ্ধমূল ধারণাগুলোকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে: রাজনীতিবিদ ও তাদের মিত্ররা মিলে ভোটারদের ধোকা দেওয়া কিংবা সমালোচকদের মুখ বন্ধ করিয়ে দেওয়ার মতো বিষয়গুলোকে মোটেও খাটো করে দেখা যাবে না।
২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে সুইডেনে অনুষ্ঠিত ১৩তম গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম কনফারেন্সে ভারতের ক্যারাভান ম্যাগাজিনের সাবেক নির্বাহী সম্পাদক বিনোদ কে. জোসি দুর্দান্ত একটি উদাহরণ তুলে ধরেন। ২০২৩ সালে কানাডায় একজন শিখ কর্মী হত্যার ঘটনা উল্লেখ করেন তিনি। অভিযোগ রয়েছে, এই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছিল ভারতের সরকারের নির্দেশেই।

গণতন্ত্র রক্ষার ওপর জিআইজেসি২৩-এর এই প্যানেল আলোচনাটি ইউটিউবে দেখতে পারেন। ছবি: জিআইজেএন, ইউটিউব
জোসি বলেন, “আমি মনে করি না ১০-১৫ বছর আগেও এমনটা ঘটতো। এখন যেমন অন্যায় করার পরও টিকে থাকা যায়—নির্বাচিত স্বৈরাচারী নেতারা পরস্পরকে দেখে এই আত্মবিশ্বাস অর্জন করছেন। এই ঘটনা তার প্রতিফলন।”
২০২৩ সালের শুরুর দিকে ব্রাজিলে যেমন, সাবেক প্রেসিডেন্ট জইর বলসোনারোর সমর্থকরা রাজধানীতে একটি পরিকল্পিত সহিংস বিদ্রোহে অংশ নেন। বছর দুয়েক আগে এর কাছাকাছি একটি ঘটনা আমরা দেখতে পাই। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি ট্রাম্প সমর্থকরা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল হিল ভবনে এ ধরনের তান্ডব চালায়। দুটি ঘটনার ক্ষেত্রেই পশ্চিম গোলার্ধের দুই বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাহী কর্মকর্তারা বিদ্রোহীদের উৎসাহিত করেছিলেন।
এই উদ্বেগজনক প্রবণতাগুলো কেবলমাত্র জননেতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্বের কিছু বৃহত্তম গণতন্ত্র এখন জনতুষ্টিবাদী রাজনীতির দ্বারা একধরনের হুমকির সম্মুখীন। কোথাও সংখ্যালঘুরা শাসন করছে, নয়তো বিপরীত ঘটনা ঘটছে। কোথাও আবার চরম সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন জারি আছে—যেখানে জাতীয়তাবাদী শাসক দলগুলো নির্মমভাবে সংখ্যালঘুদের অধিকার হরণ করছে।
জিআইজেসি২৩ এর একই প্যানেলে, পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক ডেভিড কে জনস্টন বলেন, নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা কাভার করার পাশাপাশি ওয়াচডগ সাংবাদিকদের উচিৎ নিরবে-নিভৃতে নাগরিকদের অধিকার গ্রাস করে এমন অদৃশ্য লোকেদের সক্রিয়ভাবে অনুসন্ধান করা। তিনি এদেরকে বলেছেন গণতন্ত্রের ভিত খেয়ে ফেলা “ঘুণপোকা” ।
পুলিৎজার জয়ী জনস্টন আরো বলেন, “আপনি কিভাবে সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন? ভোটার তালিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থকদের নিবন্ধনকে কঠিন করে। বা তাদের ব্যালটকে উপেক্ষা করে। কিংবা আলেচিত না হলেও কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলোতে নিজের লোকদের গোপনে বসিয়ে। অথবা রাজনৈতিক এলাকার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ আনার মাধ্যমে।”
এখানে তিনি যোগ করেন, “অনেক সময় এগুলো হয়তো খুব একটা আকর্ষণীয় গল্প নয়, কিন্তু অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের এদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।”
নির্বাচনী অনুসন্ধান পদ্ধতি নিয়ে পর্যালোচনা
এই অধ্যায়ে আমরা কিছু কার্যকর নির্বাচনী অনুসন্ধান কৌশল শেয়ার করছি। যেগুলো প্রায়ই উপেক্ষিত থেকে যায় বলে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন। এর পাশাপাশি থাকছে কিছু নির্ভরযোগ্য ওপেন সোর্স টুল এবং শক্তিশালী একটি কৌশল, যা দিয়ে বিপজ্জনক বা ঘৃণাত্মক প্রচারণামূলক সাইটের পেছনে কারা আছে তা চিহ্নিত করা সম্ভব। এসব উপকরণের মধ্যে বিশেষজ্ঞদের আগের মতামতগুলোও অন্তর্ভুক্ত আছে। যেমন রাজনৈতিক চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর নিয়ে কাজ করেন এমন শীর্ষ অনুসন্ধানী সাংবাদিক জেন লিটভিনেনকো এবং প্রোপাবলিকার মিডিয়া ম্যানিপুলেশন বিশেষজ্ঞ ক্রেইগ সিলভারম্যানের পরামর্শগুলো।
কারণ ১৫০টিরও বেশি দেশে নির্বাচন হয়, আর প্রতিটি দেশের নির্বাচনী আইন, নাগরিক স্বাধীনতা ও প্রধান তথ্যের উৎস ভিন্ন। তাই এমন কোনো একক অনুসন্ধানী টুল বা কৌশল নেই যা দেশ-কাল ভেদে সবখানে সমানভাবে কাজে লাগবে। তবে কিছু বহুল ব্যবহৃত টুল ও পদ্ধতি আছে, যেগুলো অনেক দেশে এবং প্রায় সব ধরনের নির্বাচনী পরিমণ্ডলে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।
নিচে এমন চারটি নির্বাচনী অনুসন্ধান কৌশল সম্পর্কে বলা হয়েছে যেগুলো চালাতে উচ্চস্তরের কম্পিউটার দক্ষতার প্রয়োজন নেই:
- বুলিয়ান সার্চ. ডিজিটাল দক্ষতা কম বা বেশি হোক না কেন, বিশ্বজুড়ে শীর্ষ অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা গুগলের ডেটা খুঁজে বের করার প্রক্রিয়াকে নিখুঁতভাবে কাজে লাগাতে বুলিয়ান গুগল সার্চ পদ্ধতির উপর নির্ভর করেন। এক্ষেত্রে হয় তারা প্রতিষ্ঠিত সার্চ অপারেটর বা অ্যাডভান্সড গুগল “ডর্কস” ব্যবহার করেন। (ডর্কস বিশেষ অনুসন্ধান অপারেটর ব্যবহার করে, প্রায়শই লুকানো বা সংবেদনশীল তথ্য উন্মোচন করে।) যেমন: আপনি যদি খুঁজে দেখতে চান কোনো প্রার্থীর অতীতে কোনো অপরাধী বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এমন কোনো ব্যক্তির সঙ্গে উঠাবসা ছিলেন কিনা। আপনার হাতে সময় কম। এক্ষেত্রে গুগল সার্চ বারে এ ধরনের একটি কমান্ড লিখে দেখতে পারেন—“name of candidate” “AROUND(18)” “name of criminal” —এর ফলে গুগল এমন সব নথি-প্রমাণ খুঁজবে যেখানে ওই দুটি নাম একই বাক্যে এসেছে। আরেকটি কৌশল রয়েছে—যেটি বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক তথ্য ছড়ানো ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে বিস্ময়করভাবে কার্যকর, সেটি হলো “এক্সক্লুডিং ট্রিক”। এখানে কোনো পোস্টের ইউআরএল কপি করে সার্চে পেস্ট করতে হবে, তারপর পুরো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম বাদ দিতে হবে মাইনাস চিহ্ন ব্যবহার করে। যেমন: “-site:youtube.com” বা “-site:Instagram.com”— এতে বোঝা যাবে সমস্যাযুক্ত নির্বাচনী ভিডিওটি আর কোথায় বা প্রথম কবে কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল।
- “স্টোর ম্যানেজার ট্রিক” — রাজনৈতিক সহিংসতা অনুসন্ধানের উপায়। শহরের যেখানে ওই রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে ওই স্থানের গুগল ম্যাপে জায়গাটিকে বড় করে দেখুন; সেখানে কাছাকাছি যে সব দোকানের নম্বরগুলো দেখাবে সেগুলোতে কল করুন; প্রথমে দোকানের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাদের ইমেইল ঠিকানা জিজ্ঞাসা করুন, তারপর তাদের বাইরের সিসিটিভি বা নিরাপত্তা ক্যামেরার ভিডিও দেখার অনুমতি চান। প্রথমে অনেকেই ফুটেজ দিতে অস্বীকৃতি জানাবেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিটের অভিজ্ঞ রিপোর্টাররা বলেন, আসল “ট্রিক” হলো— প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশের পর সেটির একটি কপি ইমেইল করে ওই ম্যানেজারদের কাছে পাঠানো এবং পুনরায় সেই সিসিটিভি ফুটেজ চাওয়া। তাদের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সাংবাদিক হিসেবে আপনার নিরপেক্ষতা দেখে অনেক ম্যানেজারই পরবর্তীতে মত পরিবর্তন করেন এবং ফুটেজ দিতে রাজি হয়ে যান।
- কপি-পেস্ট-সার্চ: গোপনে প্রভাব বিস্তারকারী প্রচারণাগুলো চেনার সবচেয়ে সহজ উপায়। যদি আপনি কোনো নির্বাচনী ওয়েবসাইটে সমস্যাযুক্ত বা উসকানিমূলক কনটেন্ট পান, কিন্তু সেখানে সাইটের মালিকের কোনো তথ্য না থাকে, তাহলে হোমপেজ থেকে যেকোনো অংশ কপি করে গুগলের সার্চ বারে পেস্ট করুন। দেখুন একই বা মিল আছে এমন কনটেন্ট অন্য কোথাও আছে কিনা। যদি একাধিক সাইটে একই ধরনের লেখা পাওয়া যায়, তাহলে এটি একটি গোপন ও সমন্বিত প্রভাব বিস্তারের প্রচারণার ইঙ্গিত হতে পারে। এভাবে আপনি মূল সাইটের মালিক বা রাজনৈতিক প্রচারণার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারেন। (একই ধরনের লোগো বা ওয়েবসাইটের ডিজাইন লক্ষ্য করুন—এগুলো অনেক সময় একই ওয়েব ডিজাইনারের সম্পৃক্ততাকে তুলে ধরে।)

জিআইজেএনের জন্য এই অলংকরণটি করেছেন মার্সেল লু
- “জিওকোড ট্রিক”—প্রচারণার ঘটনাগুলো চিহ্নিত করার উপায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নির্দিষ্ট একটি এলাকা থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ করার জন্য টুইটডেক টুল ব্যবহার করাটা ছিল রাজনৈতিক ঘটনা অনুসন্ধানের একটি শক্তিশালী কৌশল। তবে দুঃখজনকভাবে, এক্স প্ল্যাটফর্মের সাম্প্রতিক পরিবর্তনের ফলে এখন টুইটডেক (যার নাম বদলে রাখা হয়েছে “এক্স প্রো”) ব্যবহার করতে চাইলে একটি বিস্তৃত ও পেইড সাবস্ক্রিপশন নিতে হয়। তবুও, এটি এখনো বিক্ষোভ বা সমাবেশ থেকে আসা ভিডিও ও পোস্ট তাৎক্ষণিক সংগ্রহে দারুণ কাজ করে। সাংবাদিকরা এটি ব্যবহার করে হামলাকারীদের শনাক্ত করতে পারেন, কিংবা দ্রুত প্রমাণ করতে পারেন যে সহিংসতার জন্য ভুক্তভোগীদের দোষারোপ করে প্রচারিত দাবিগুলো মিথ্যা। কোনো ঘটনার স্থান গুগল ম্যাপে “What’s here” ট্যাগ থেকে কপি করে তার কোঅর্ডিনেটস নিয়ে নিন। এরপর টুইটডেকে সেই কোঅর্ডিনেটস “geocode:” শব্দটির সঙ্গে পেস্ট করে দিন, এবং একটি দূরত্বের সীমারেখা (রেডিয়াস) উল্লেখ করুন। এতে ওই এলাকার সব সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ও ভিডিও এক জায়গায় আসবে। পদ্ধতিটি ধাপে ধাপে বেলিংক্যাটের এই বিবৃতিতে ব্যাখ্যা করা আছে। যারা এক্স-এর টুল এড়িয়ে যেতে চান, তারা Hootsuite এর মতো বিকল্প টুল ব্যবহার করতে পারেন। (দ্রষ্টব্য: যদি আপনি এর থেকে ভালো কোনো ওপেন সোর্স টুল জানেন, দয়া করে hello@gijn.org-এ শেয়ার করুন, আমরা এই অধ্যায়টি আপডেট করব।)
অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য আরও চারটি উদাহরণ দেওয়া হলো:
- আলেফ ডেটাবেস। নির্বাচন ঘিরে অর্থনৈতিক অনিয়ম ও গোপন সংযোগ খুঁজে বের করতে সাংবাদিকরা ওসিসিআরপির আলেফ ডকুমেন্ট লিকস ডেটাবেস ব্যবহার করে সফল হয়েছেন। এই রিসোর্সটিতে এখন একটি “ক্রস-রেফারেন্স” ফিচারও রয়েছে, যার মাধ্যমে আপনি আপনার আপলোড করা ফাইলটিতে পাওয়া নামগুলো আলেফে থাকা শত শত অন্য ডাটাবেসে খুঁজে দেখতে পারেন।
- জাঙ্কিপিডিয়া। সাংবাদিকদের মধ্যে ফেসবুকের শক্তিশালী সোশ্যাল মিডিয়া বিশ্লেষণ টুল ক্রাউডট্যাংল-এর প্রতি আস্থা কমে যাওয়ার পর, দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠা অন্য দারুণ অনুসন্ধানী টুলটি হলো জাঙ্কিপিডিয়া। এটি এখন নির্বাচনী বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা ও সমস্যাযুক্ত পোস্ট ও ওয়েবসাইট ট্র্যাক করার জন্য অন্যতম নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম। এখানে ব্যবহারকারীরা ১২টি ভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের তালিকা তৈরি করতে পারেন—এর মধ্যে রয়েছে কট্টর-ডানপন্থী গোষ্ঠীর ব্যবহৃত সাইট যেমন GETTR এবং Gab, আবার বড় প্ল্যাটফর্ম যেমন TikTok, Facebook, এবং Telegram।
- নিপীড়িত নাগরিকদের কাছে পৌঁছাতে—সাইফন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্বৈরশাসিত দেশের নাগরিকদের জন্য অন্যতম উদ্ভাবনী ও গুরুত্বপূর্ণ নতুন টুল হলো কানাডার সাইফন প্ল্যাটফর্ম। এটি একটি উন্নত সেন্সরশিপ-বাইপাস টুল, যা ভোটারদেরকে তাদের অধিকার ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে স্বাধীন তথ্য জানার সুযোগ দেয়—ধরা পড়া বা শাস্তির ঝুঁকি ছাড়াই। অ্যান্ড্রয়েড, উইন্ডোজ এবং আইওএস প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যায় সাইফন ৩। এটি ফ্রি ও ওপেন সোর্স সফটওয়্যার ব্যবহার করে এবং নিরাপদ সার্ভার, এনক্রিপশন ও “অবফাসকেশন টেকনোলজি”র সমন্বয়ে সংযোগ আড়াল করে নিষিদ্ধ দেশে ব্লক করা নিউজ সাইটগুলোতে পাঠকদের যুক্ত করে। নির্বাসিত বা ঝুঁকির মুখে থাকা সংবাদমাধ্যমগুলো তাদের দর্শকদের এই পদ্ধতি সম্পর্কে জানাতে পারে, কারণ এটি প্রচলিত ভিপিএনের চেয়ে বেশি নিরাপদ। সাইফনের ইউজার গাইড দেখতে পারেন এই লিংকে, অথবা বিকল্প হিসেবে প্রোটনভিপিএন ব্যবহার করে দেখতে পারেন।
- বেলিংক্যাট অটো আর্কাইভার। নির্বাচনী সহিংসতা দিনে দিনে ক্রমবর্ধমান সমস্যা হওয়ার কারণে এর ভিডিও প্রমাণ সংরক্ষণ করাটা জটিল আর ঝুঁকিপূর্ণ—২০২৪ ও ২০২৫ সালেও। এটি মোকাবিলায় বেলিংক্যাটের প্রযুক্তি দল একটি নতুন টুল তৈরি করেছে। এর মাধ্যমে সাংবাদিকরা সহজেই কোনো ভিডিওর ইউআরএল একটি নির্দিষ্ট স্প্রেডশীটে কপি-পেস্ট করতে পারেন। আর সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিটি ক্লিপের জন্য সেরা ডাউনলোড ও আর্কাইভ করার কৌশল খুঁজে বের করে। (অ্যাক্সেস ও সেটআপের জন্য জিআইজেএনের “২০২৩ সালে সেরা দশ অনুসন্ধানী টুল” এর লিঙ্কগুলো দেখুন।)
সাংবাদিকদের শুধুমাত্র অবৈধ বিষয়গুলো নয়, আরও গভীরে কেন অনুসন্ধান করা উচিত

প্রোপাবলিকা ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে প্রায় এক লাখ ভোটারের নিবন্ধন চ্যালেঞ্জ করার আইনসম্মত কিন্তু নৈতিকভাবে বিতর্কিত প্রচারণার তথ্য উন্মোচন করে। ছবি: স্ক্রিনশট, প্রোপাবলিকা
গণতন্ত্রপন্থীরা বলেন, অনুসন্ধানী সম্পাদকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো নির্বাচনী প্রচারণার শুরুর দিকেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর পরিচিত হামলার জায়গাগুলো চিহ্নিত করা এবং সেগুলো নিয়মিত নজরদারিতে রাখা। এর মধ্যে শুধু মানবাধিকার লঙ্ঘন বা নির্বাচনী আইন ভাঙা নয়, আইনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার বা অপব্যবহারও অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৩ সালে প্রোপাবলিকার একটি অনুসন্ধানে উঠে আসে যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে মাত্র ছয়জন ডানপন্থী কর্মী নতুন নির্বাচন আইনকে কাজে লাগিয়ে ৮৯ হাজার ভোটারের যোগ্যতা নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আপত্তি তুলেছিলেন। এ অনুসন্ধান দেখায় কীভাবে এসব ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ গণহারে ভয়ভীতি ছড়ানো, প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি এবং ভোটার দমন করার আশঙ্কা তৈরি করছে। অনেক সময় হাজারো বৈধ ভোটারকে কেবল একজন নাগরিকের তোলা অমূলক আপত্তি খণ্ডন করতে শুনানিতে হাজির হতে হয়, অর্থ ব্যয় করতে হয়, কিংবা অকারণ প্রশাসনিক ঝক্কি পোহাতে হয়—শুধু ভোটার তালিকায় নাম টিকিয়ে রাখার জন্য।
এদিকে, গণতন্ত্রপন্থী অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ব্রেনান সেন্টার ফর জাস্টিসের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঈগল এআই নামের একটি নতুন টুল গণতন্ত্রের জন্য বড় ধরনের হুমকি। এই সফটওয়্যারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণহারে ভোটারদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ এই টুল ব্যবহার করে কয়েক মিনিটেই হাজার হাজার মানুষের ভোটার নিবন্ধনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। টুলটি ত্রুটিপূর্ণ ও পক্ষপাতদুষ্ট ডেটাবেস ব্যবহার করে ভোটারদের ব্যক্তিগত তথ্য ও স্থানীয় নির্বাচনী নিয়ম মিলিয়ে এক ধরনের “তথ্য-প্রমাণ” হাজির করে । অসৎ উদ্দেশ্য আছে এমন লোকেরা তা ব্যবহার করে অন্য নাগরিকদের ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। বাস্তবে ওই তথ্য-প্রমাণগুলো সঠিক না হলেও অন্যকে হয়রানির জন্য কাজে লাগানো হতে পারে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, যদি কেউ নার্সিং হোমে থাকেন বা বাড়ির বাইরে থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দেন—কিছু ক্ষেত্রে এগুলো ভোটার নিবন্ধন নিয়ে আপত্তি জানানোর প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।
জিআইজেএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভোটফ্লেয়ার–এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক জশ ভিসনো বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এই ব্যক্তিগত ভোটার চ্যালেঞ্জ ব্যবস্থা আসলে আরও বড় একটি সমস্যা তুলে ধরে। বর্তমান জনতুষ্টিবাদী যুগে ইউরোপ থেকে আফ্রিকা—সব গণতান্ত্রিক দেশেই সাংবাদিকদের এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। ভোটফ্লেয়ার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্টেভিত্তিক একটি ভোটার ক্ষমতায়ন টুল। তিনি যোগ করেন, সাংবাদিকরা অবৈধ কাজ বা আইনের বিরুদ্ধে যাওয়া কর্মকাণ্ড খুঁজে বের করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তবে এর পাশাপাশি সাংবাদিকদের উচিত আইনসম্মত হলেও গণতন্ত্রবিরোধী যেসব প্রক্রিয়া চালু আছে, সেগুলোও অনুসন্ধান করা এবং বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা।
২০২৪ সালের মার্কিন নির্বাচনকে ঘিরে যেসব “নোংরা কৌশল” সম্পর্কে ভিসনো সবচেয়ে বেশি চিন্তিত, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে— ভোটার তালিকা থেকে গণহারে নাম মুছে ফেলা, এবং চরম ডানপন্থী গভর্নরদের পক্ষ থেকে ভোটারদের বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি। তবে প্রোপাবলিকার প্রতিবেদনে যে ভোটার চ্যালেঞ্জ ইস্যুটি উঠে এসেছে, সেটাকেই তিনি সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
তিনি বলেন, “এটা অনেকটা ডক্সিংয়ের মতো। (ডক্সিং—কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য—যেমন ঠিকানা, ফোন নম্বর, কর্মস্থলের ঠিকানা ইত্যাদি ইন্টারনেটে প্রকাশ করে তাকে ভয় দেখানো বা হয়রানি করা)। ভাবুন তো, যে কেউ স্বয়ংক্রিয় একটি টুল ব্যবহার করে ভুল ডেটার ভিত্তিতে আপনার ভোটার নিবন্ধনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করতে পারে। আমি সহজেই বলতে পারি: ‘জো স্মিথ, আমি মনে করি তুমি মিশিগানে সঠিকভাবে ভোটার নিবন্ধন করো নাই, কারণ শুনেছি তোমার ফ্লোরিডায় একটা বাড়ি আছে।’ এভাবে পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়াই জটিল হয়ে পড়ে।”
নির্বাচন সম্পর্কিত অনুসন্ধানে যে কৌশলগুলো বিবেচনা করা যায়
১. নাগরিক পর্যবেক্ষকদের মাধ্যমে স্থানীয় তথ্য ও ডেটাবেস খুঁজে বের করুন
নির্বাচন নিয়ে অনুসন্ধান করেন এমন বিশেষজ্ঞরা আর জিআইজেএনের সদস্য বার্তাকক্ষগুলোর মতে, কার্যকর ডেটাবেস ও টুল গুরুত্বপূর্ণ হলেও বেশিরভাগ প্রভাবশালী অনুসন্ধানের শুরু হয় মানবসূত্র থেকেই। এর মধ্যে থাকতে পারে হুইসেলব্লোয়ার, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও নাগরিক সমাজের পেশাজীবী, নির্বাচন কর্মকর্তা, প্রচারণায় জড়িত নিম্নপর্যায়ের কর্মী—আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেই সাধারণ নাগরিকরা যারা গণতন্ত্রকে গুরুত্ব দেন।
যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট–এর নির্বাচনী প্রোগ্রামের পরিচালক প্যাট মারলো বলেন, সারা বিশ্বের শত শত নিরপেক্ষ নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ গ্রুপ থেকে সাংবাদিকরা প্রচুর তথ্য পেতে পারেন। এনডিআই–এর দেশভিত্তিক ডেটাবেসে ৮৯টি দেশে ২৫১টি যাচাই করা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত আছে। তিনি বলেন, এই নির্ভরযোগ্য গ্রুপগুলো স্বাধীন মিডিয়ার জন্য এখনো কম ব্যবহৃত একটি সম্পদ। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—এরা সাংবাদিকদের সাম্প্রতিক স্থানীয় নির্বাচনী নিয়ম ও ডেটাসেটগুলোতে পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারে। যা প্রচারণা ও সমর্থকদের আইনি সমর্থ যাচাই করতে প্রয়োজন। উদাহরণ হিসেবে, মারলো জাম্বিয়ার ক্রিশ্চিয়ান চার্চেস মনিটরিং গ্রুপ (সিসিএমজে)–এর কথা উল্লেখ করেছেন, যারা ২০২১ সালের জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্টিয়াল বাই-ইলেকশনে ১ হাজার ১০৮ জন পর্যবেক্ষক মোতায়েন করেছিল। এছাড়া জর্জিয়ার দ্য ইয়ং লায়ার্স অ্যালায়েন্স এবং আইএসএফইডি (ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর ফেয়ার ইলেকশনস)–কেও উদাহরণ হিসেবে এনেছেন।
“কেউ কেউ নির্বাচনী সহিংসতার দিকে নজর রাখবেন; কেউ কেউ বিভ্রান্তিমূলক তথ্য বা ডেটার দিকে মনোযোগ দেবেন; আর সবাই ভোটার তালিকার সততা, ভোটকেন্দ্রের অবস্থান, নির্বাচনের দিনে যেসব বিষয় খেয়াল রাখতে হবে—এই ধরনের বিষয়গুলো দেখবেন। এদের সঙ্গেই আমি যোগাযোগ করব,” বলেছেন মারলো।
২. এমনভাবে রিপোর্ট করুন যেন আপনার দেশে সত্যিকারের গণতন্ত্র রয়েছে—হোক বা না হোক
যেসব দেশ বর্তমানে কর্তৃত্ববাদী শাসনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে নির্বাচন কভার করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো, এমনভাবে রিপোর্ট করা যেন দেশটিতে একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। অর্থাৎ নির্বাচনী প্রচারণা ও দুর্নীতি ঘিরে এমন সব ঘটনা অনুসন্ধান করা যার কারণে হয়তো কাউকে গ্রেপ্তার বা বরখাস্ত করা হবে না বা ভোটের ফলাফল বদলাবে না। যেমনটা মিসরের মাদা মাসর সাইটের প্রধান সম্পাদক লিনা আতালাহ বলেন, এটি সাংবাদিকদের স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপ (self-censorship) কমাতে সাহায্য করে এবং সরকারী নৈতিকতার ওপর ভোটারদের আস্থা বৃদ্ধি করে।
৩. নির্বাচনী “ডার্টি ট্রিকস”-এর প্রমাণ জনগণের কাছ থেকেই সংগ্রহ করুন
যদি আপনার দেশের নির্বাচনী আলোচনা প্রায়ই হোয়াটসঅ্যাপ–এর মতো ব্যক্তিগত বার্তা প্ল্যাটফর্মে চলে—যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকাতে দেখা যায়—তাহলে বিশেষজ্ঞদের মত নিউজরুমগুলো গুগল ভয়েস অ্যাপ ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপ টিপ লাইন নম্বর প্রকাশ করুন। এরপর তা ব্যবহার করে দর্শক বা পাঠকদের থেকে খবর নিন যে তারা কোনো ভুয়া নির্বাচনী দাবি, ভোটার নিবন্ধন সংক্রান্ত চক্রান্ত, বা উগ্রপন্থীদের হুমকির মুখোমুখি হয়েছেন কিনা। আরও বলা হয়েছে, একই টিপ লাইন ব্যবহার করে প্রতিদ্বন্দ্বী নিউজরুমগুলো একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা, একসঙ্গে গণতন্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ড উন্মোচন এবং সূত্র খুঁজে বের করতে পারে।
এই কৌশলটি প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর জন্যও গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার রোবোকল (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কল করা, বিশেষ করে অন্যের কণ্ঠস্বর নকল করে বা পূর্ব-রেকর্ড করা বার্তা পাঠিয়ে কল করা) খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে। এমন কলের পেছনে যারা দায়ী—যারা ভোটারদের করের তথ্য সম্পর্কিত অতিরিক্ত হুমকি দেয় বা সংখ্যালঘুদের ভোটের দিন ভুল তথ্য দেয়—তাদের খুঁজে বের করা সাংবাদিকদের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে অন্যতম কঠিন কাজ। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই কলগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ক্রাউডসোর্সিং (ইন্টারনেট বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো) শুরু করার সবচেয়ে ভালো উপায়।
৪. সহজ বুলিয়ান গুগল সার্চ করুন—এবং বারবার করতে থাকুন
যেমনটা আগেও বলা হয়েছে, উন্নত বুলিয়ান সার্চ কৌশল এবং “গুগল ডর্কস” অনলাইনে প্রয়োজনীয় ডেটা খুঁজে বের করার জন্য শক্তিশালী টুল। তবে জিআইজেএনের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার থেকে যা বোঝা গেছে, তা হলো—অনুসন্ধানীরা প্রায়ই খুবই সাধারণ, দ্রুত এবং ট্রায়াল-অ্যান্ড-এরর পদ্ধতিতে অনলাইনে তথ্য খোঁজেন। যেমন, ন্যান্সি ওয়াটসম্যান। তিনি অনুসন্ধানী সাংবাদিক এবং নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইবারসিকিউরিটি ফর ডেমোক্রেসি প্রকল্পের পরামর্শক। আমরা দেখেছি কীভাবে তিনি ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানোর পরিকল্পনা খুঁজতে গুগল সার্চ চালাচ্ছেন। অধিকাংশ সময়, একই গুগল সার্চ বারে তিনি শুধু প্রয়োজনমত Keywords আর AND ও OR এর মতো সাধারণ টার্ম ব্যবহার করেছেন— যা আমরা সবাই ব্যবহার করি।
- ন্যান্সি ওয়াটসম্যানের সাধারণ গুগল সার্চের একটি উদাহরণ। ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল দাঙ্গার পর, তিনি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ২০ জানুয়ারি শপথগ্রহণে সহিংসতার হুমকি আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে সিরিজ জোড়া কীওয়ার্ড ব্যবহার করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ: “patriot”AND “march” (OR “rally” OR “january 20” OR “jan 20” OR “fraudulent election” OR “Ashli babbit” OR “storm” OR “capital” OR “capitol”) এবং “inauguration” AND “march” (OR “rally” OR “storm” OR “fraud”). এই সার্চগুলো ব্যবহার করে তিনি বিভিন্ন অনলাইন উৎস থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য দ্রুত সংগ্রহ করেছিলেন।
ন্যান্সি ওয়াটসম্যান বলেন, নির্বাচন বিষয়ক অনুসন্ধানের জন্য গুগল নিজেই অত্যন্ত শক্তিশালী উৎস। তবে এটি কার্যকর করতে হলে আমাদের সেই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করতে হবে যেভাবে সার্চ ইঞ্জিনটি কাজ করে এবং যেভাবে আমরা লোকেদের ওপন অনুসন্ধান চালানোর সময় ভাবতে থাকি যে, তারা কিভাবে চিন্তা করে। এছাড়া, বারবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।
৫. ভোটারদের প্রত্যাশা বোঝার চেষ্টা করুন
অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের ভূমিকা শুধু নির্বাচন ঘিরে জবাবদিহি তৈরি করা বা অনিয়ম প্রকাশ করাই নয়, বরং কার্যকর জনসেবামূলক সাংবাদিকতাও হওয়া উচিত। এর মধ্যে রয়েছে রিপোর্টে তুলে ধরা তথ্যের সত্যতা ও নির্বাচনের বৈধতা বোঝানো। উদাহরণস্বরূপ, ওপেন সোর্স টুল ফ্লরিশ ব্যবহার করে ভিজ্যুয়ালাইজেশন তৈরি করা যেতে পারে, যা ভুয়া জালিয়াতির অভিযোগ খণ্ডন করবে, নিউজরুমগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বাড়াবে এবং ভোট গণনায় স্বাভাবিক দেরি বা ছোটখাটো ভুলগুলো সম্পর্কে ভোটারদের আশ্বস্ত করবে। বিশেষজ্ঞরা আরও বলেন, রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত দেশগুলোতে গণমাধ্যমের ওপর আস্থা বাড়াতে স্পষ্টভাবে “আমরা কেন এই প্রতিবেদনটি করেছি” এমন ব্যাখ্যা-ধর্মী লেখা প্রকাশ করা জরুরি। ট্রাস্টিং নিউজ–এর সহকারী পরিচালক লিন ওয়ালশ পরামর্শ দিয়েছেন, অনুসন্ধানী নির্বাচনী প্রতিবেদনের মূল অংশেই বড় করে “কীভাবে/কেন আমরা এটি করেছি” বক্স রাখা উচিত। প্রয়োজনে সাংবাদিক নিজেই ছোট দৈর্ঘ্যের সরাসরি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে ব্যাখ্যা দিতে পারেন।
কেস স্টাডি: ইউএ/পাব টুল (অ্যান্ড গ্রিড) যেভাবে গোপন রাখা বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ও প্রপাগান্ডা নেটওয়ার্কগুলোকে সামনে আনতে পারে
অনলাইন নিয়ে কাজ করেন অনুসন্ধানী সাংবাদিক ক্রেগ সিলভারম্যান। তার লেখা ভেরিফিকেশন হ্যান্ডবুক বইটি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আর এ কাজটি করার মাধ্যমে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত বিভিন্ন সাংবাদিক ও বার্তাকক্ষকে নতুন ডিজিটাল টুল ব্যবহারের দিক নির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে নির্বাচনী জবাবদিহিতার বিষয়গুলোকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে রহস্যময় নির্বাচনী ওয়েবসাইট রয়েছে, যেগুলো ঘৃণা ও ষড়যন্ত্রকে ছড়িয়ে দেয়, প্রচার করে। সিলভারম্যান একটি কৌশল শেয়ার করেছেন— যা “ইউএ/পাব মেথড” (UA/Pub method) নামে পরিচিত। যেটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা জরুরি।
এর কাজের মূল সুবিধা দুইটি। প্রথমত, কোডটি যদিও জটিল মনে হতে পারে, এটি আসলে কোনো উন্নত প্রযুক্তিগত দক্ষতা ছাড়াই ব্যবহার করা যায়। দ্বিতীয়ত, অনেকে নির্বাচন ঘিরে অসৎ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। তারা ব্যক্তিগত লাভ বা লোভের কারণে এমন কাজ করে। এই পদ্ধতিটি তাদের শনাক্ত করতে সাহায্য করে।
নির্বাচনে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিরা থাকেন—যেমন প্রচারণার কর্মী, বিশেষ স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত লবিস্ট বা দাতা। অনেক কারণে তারা চাইবেন না যে জনগণ জানুক কিছু ওয়েবসাইটের পেছনে তারাই মূলত আসল শক্তি। হয়তো এই ওয়েব সাইটগুলোরই বিদ্বেষ ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার করছে বা বিদেশি শক্তির সঙ্গে অবৈধ সংযোগ রয়েছে।
তারা কি নিজেদের নাম লুকানোর জন্য সেই ওয়েবসাইটের স্বত্ব ত্যাগ করতে রাজি? হ্যাঁ, অনেকেই ডোমেইন প্রাইভেসি সেটিং ব্যবহার করে নিজেদের নাম সরিয়ে রাখে। তবে তারা কি সেই সাইট থেকে আসা বিজ্ঞাপন আয়ও ত্যাগ করতে রাজি? সম্ভবত না, মনে করেন সিলভারম্যান। এ কারণেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা নির্বাচনী বিষাক্ত ওয়েবসাইটগুলোর পেছনের ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে পারেন।
ইউএ/পাব টুল কীভাবে কাজ করে
- লক্ষ লক্ষ ওয়েবসাইটের মালিকরা বিনামূল্যের গুগলের অ্যাডসেন্স সার্ভিসের জন্য সাইন আপ করেছেন, এতে গুগল তাদের সাইটে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিজ্ঞাপন দেখায়। এই বিজ্ঞাপন থেকে আয় করতে হলে ওয়েবসাইট মালিককে তাদের সাইটের সোর্স কোডে একটি বিশেষ অ্যাডসেন্স নম্বর যোগ করতে হয়। এই নম্বর সবসময় “Pub-” দিয়ে শুরু হয়।
- একইভাবে, লাখ লাখ ওয়েবসাইটের মালিক ফ্রি গুগল অ্যানালিটিক্স সার্ভিসেও সাইন আপ করেছেন। এটি তাদের জানায় কতজন দর্শক আসছে এবং তারা কোথা থেকে আসছে। এই তথ্য পেতে হলে তাদের সব সাইটে একটি বিশেষ কোড বসাতে হয়, যা সবসময় “UA-” দিয়ে শুরু হয়।
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ওয়েবসাইট মালিকরা সাধারণত একই আইডি ব্যবহার করেন। এতে গুগল সহজেই বুঝতে পারে বিজ্ঞাপন থেকে পাওয়া অর্থ আর ডেটা কাকে পাঠাতে হবে।
- Reporters can find either the identifying Pub or UA tags in any website source code (see
- সাংবাদিকরা যেকোনো ওয়েবসাইটের সোর্স কোডে থাকা শনাক্তকারী Pub অথবা UA ট্যাগগুলো খুঁজে নিয়ে (এই ধাপগুলো খেয়াল করুন), তারপর সেগুলো তিনটি ফ্রি টুলের যেকোনো একটিতে—BuiltWith, SpyOnWeb, অথবা DNSlytics — পেস্ট করে খুব দ্রুত জানতে পারেন একই আয় বা ডেটা ট্যাগ ব্যবহার করে আরও কোন কোন সাইটগুলো চলছে। এভাবে তারা রহস্যময় নির্বাচনী সাইটগুলোর পেছনে থাকা নেটওয়ার্ক ও ব্যক্তিদের খুঁজে পেতে পারেন।
- জেনে অবাক হবেন, নিষ্ক্রিয় বা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে এমন ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রেও UA/Pub পদ্ধতি কাজ করে। ফলে সাংবাদিকরা খুঁজে বের করতে পারেন কীভাবে একই রাজনৈতিক প্রচারণায় যুক্ত লোকেরা আগের নির্বাচনে ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে লাভবান হয়েছিল, কিংবা কীভাবে তারা ভিন্ন বা পরিবর্তিত ডোমেইন নেটওয়ার্কে জড়িত ছিল। সিলভারম্যান বলেন, সাংবাদিকরা যদি আগে থেকেই ওয়েব্যাক মেশিন ব্রাউজার এক্সটেনশন ইনস্টল করে রাখেন, তাহলে UA/Pub খোঁজার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে পপ-আপ মেসেজ আসবে — জানিয়ে দেবে যে খুঁজে পাওয়া সাইটগুলোর আর্কাইভ কপি সেখানে সংরক্ষিত আছে। এরপর সেই আর্কাইভ করা পেজ থেকেও একই UA/Pub সার্চ করে ট্যাগগুলো খুঁজে পাওয়া যায়। সিলভারম্যানের ভাষায়, “এটা কি দারুণ এবং একেবারে সহজ পদ্ধতি নয়? এক্সটেনশন থাকলে সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানিয়ে দেয়, আর আপনি সহজেই সেই সোর্স কোড ট্রিক ব্যবহার করতে পারেন।”
সিলভারম্যানের ভাষায়, “ওয়েবসাইটগুলোকে যুক্ত করার সবচেয়ে মৌলিক কৌশল এটি। বাইরে থেকে জটিল মনে হলেও আসলে খুবই সহজ। তাই আমি সাংবাদিকদের পরামর্শ দিই, নির্বাচনের সময় কোনো ওয়েবসাইটে ঢুকলে এই অনুশীলনটা করে দেখুন।”
তিনি বলেন, বিশেষ করে অ্যাডসেন্সের ‘Pub’ পাবলিশার আইডি খুবই পাকাপোক্ত প্রমাণ তুলে ধরতে সক্ষম যে, আলাদা মনে হওয়া একাধিক ওয়েবসাইটের পেছনে আসলে একই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জড়িত। “একই পাবলিশার ট্যাগ ব্যবহার করা বিজ্ঞাপন আয়ের সব অর্থ একই অ্যাকাউন্টে জমা হয়। তাই আমি যদি আমার সাইটে অন্য কারও গুগল পাবলিশার আইডি বসাই, তবে আমার বিজ্ঞাপন থেকে আসা সব অর্থ সে-ই পেয়ে যাবে—যা বাস্তবে প্রায় অসম্ভব।”
UA/Pub ট্যাগ খুঁজে বের করার উপায়
- যেকোনো ওয়েবপেজে যান, তারপর মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করুন। সেখান থেকে “View Source Code” বা “Show Page Source” অপশন সিলেক্ট করুন।

একটি ওয়েবপেজের সোর্স কোডের ছোট অংশ, যেখানে গুগল অ্যাডসেন্সের “UA-” ট্যাগ ব্যবহৃত হয়েছে। ছবি: স্ক্রিনশর্ট
- সোর্স কোড দেখে ভীত হবেন না! শুধু Control-F ব্যবহার করুন, অথবা Edit মেনু থেকে “Find” সিলেক্ট করে সোর্স কোডে “UA-” বা “Pub-” খুঁজুন।
- পাওয়া গেলে পুরো ট্যাগটি কপি করুন — এতে UA বা Pub এবং তার পরের সব নম্বর থাকবে।
- এরপর DNSlytics.com খুলে কপি করা ট্যাগটি সার্চ বারে পেস্ট করুন। সার্চটি ক্লিক করা যায় এমন একটি তালিকা দেখাবে, যেখানে একই রেভিনিউ (আয়) বা অ্যানালিটিক্স ট্যাগ ব্যবহার করা অন্য ওয়েবসাইটগুলোর ডোমেইন থাকবে। লক্ষ্য করুন, এতে এমন সাইটও থাকতে পারে যা এখন বন্ধ।
- একই প্রক্রিয়া SpyOnWeb এবং BuiltWith টুলেও ব্যবহার করুন। কারণ বেশিরভাগ সময় অতিরিক্ত ফলাফলও পাওয়া যায়—এমনকি নিষ্ক্রিয় সাইটগুলোর ক্ষেত্রেও। সিলভারম্যান বলেন, BuiltWith শুধু ওয়েবসাইটের URL দিয়েও কাজ করে, তবে তিনি সাংবাদিকদের UA এবং Pub নম্বরগুলো ম্যানুয়ালি সার্চ করে সাইটগুলোর মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ যাচাইয়ে উৎসাহ দেন।
- ওয়েব্যাক মেশিনে পাওয়া আর্কাইভ পেজগুলোর ক্ষেত্রেও পুনরায় UA/Pub সার্চ করুন।
- আপনার ফলাফল নিশ্চিত বা আরও বিস্তৃত করতে, Whoisology.com এবং DomainBigData.com-এ URLগুলো সার্চ করুন, এবং UA/Pub সার্চের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যের ইতিহাস যাচাই করুন।
নোট: যদি আপনি এমন কোনো নতুন টুল বা ডেটাবেস সম্পর্কে জানেন যা সাংবাদিকদের নির্বাচন কভার করতে ও অনুসন্ধানে সাহায্য করতে পারে, আমাদের সঙ্গে শেয়ার করুন: hello@gijn.org.
 রোয়ান ফিলিপ জিআইজেএনের গ্লোবাল রিপোর্টার এবং ইমপ্যাক্ট এডিটর। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সানডে টাইমসের প্রধান প্রতিবেদক ছিলেন। বিশ্বজুড়ে দুই ডজনেরও বেশি দেশে সংবাদ, রাজনীতি, দুর্নীতি এবং সংঘাত নিয়ে প্রতিবেদন করেছেন। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকার বিভিন্ন বার্তাকক্ষে অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর হিসেবেও কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার।
রোয়ান ফিলিপ জিআইজেএনের গ্লোবাল রিপোর্টার এবং ইমপ্যাক্ট এডিটর। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার সানডে টাইমসের প্রধান প্রতিবেদক ছিলেন। বিশ্বজুড়ে দুই ডজনেরও বেশি দেশে সংবাদ, রাজনীতি, দুর্নীতি এবং সংঘাত নিয়ে প্রতিবেদন করেছেন। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকার বিভিন্ন বার্তাকক্ষে অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর হিসেবেও কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার।