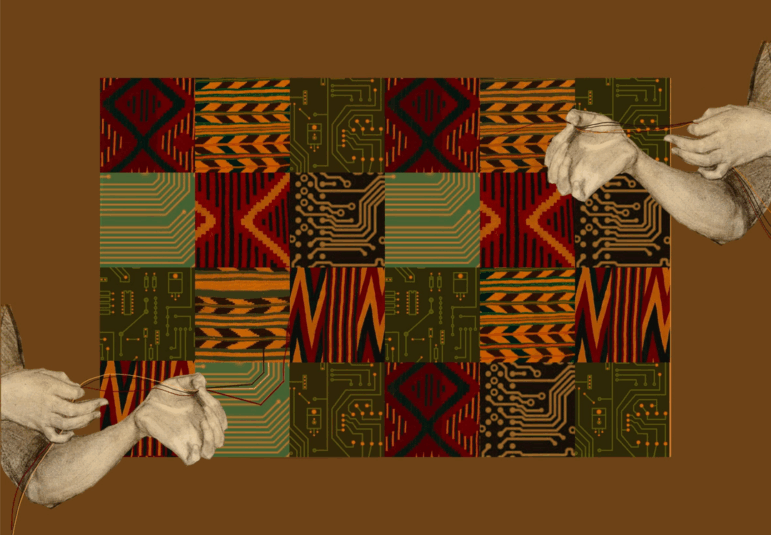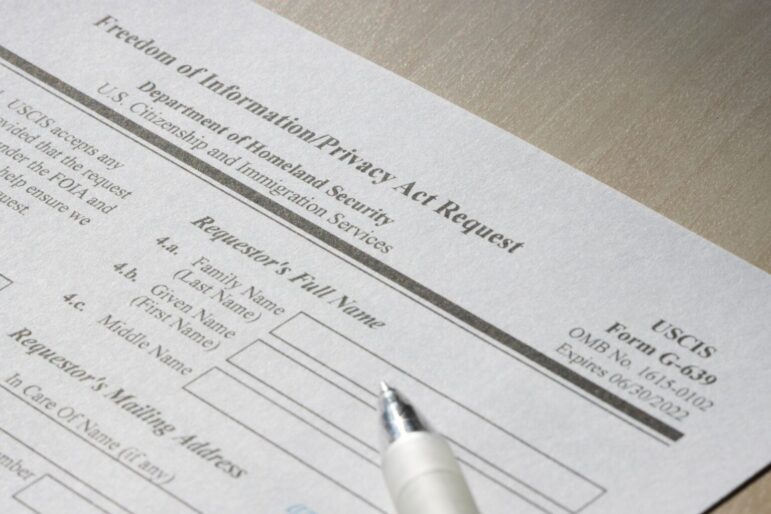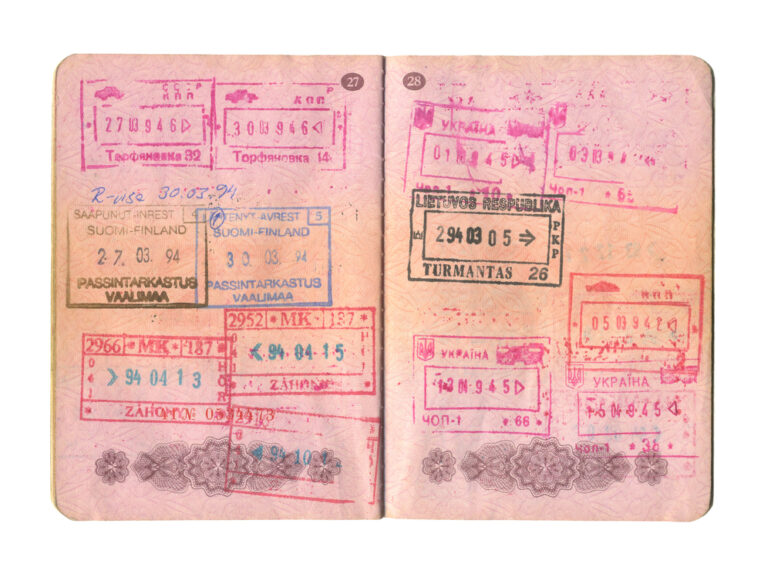মার্কিন নির্বাচন কাভার করবেন? সাংবাদিকদের জন্য দরকারি সব রিসোর্স এখানে পাবেন
আর্টিকেলটি পড়ুন এই ভাষায়:

আগামী ৩ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য ভোট দেবেন মার্কিন জনগণ। একই সঙ্গে বেছে নেবেন সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য, আর হাজারো স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। ভুল হবে না, যদি বলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবারের মতো পরিস্থিতি আগে কখনোই দেখেনি। এবার শঙ্কা আছে ভোটারদের ভয় দেখাতে কিংবা মেইল-ইন-ব্যালট পদ্ধতিতে বাধা দিতে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পাঠানো হতে পারে সশস্ত্র পর্যবেক্ষক; আছে ভোট জালিয়াতির আর বিদেশি হস্তক্ষেপের ঝুঁকি, প্রকাশ্য বা গোপন অনুদানের কল্যাণে রেকর্ড পরিমাণ টাকার ছড়াছড়ি, আর ভুয়া তথ্যের জোয়ার। আবার এত কিছু কিনা হচ্ছে এমন একটি মহামারির মধ্যে, যা শত বছরে একবার দেখা যায়।

এই নির্বাচনের সঙ্গে শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, গোটা বিশ্বেরই অনেক স্বার্থ জড়িয়ে আছে। এ কারণে নির্বাচনী মৌসুমের বাকি সময়টাতে জিআইজেএন মনোনিবেশ করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। যাবতীয় রিসোর্স ঘেঁটে গোটা বিশ্বের সাংবাদিকদের জন্য আমরা গড়ে তুলেছি সেরা টিপস ও টুলের এই সংগ্রহ, যাতে তাঁরা এই মার্কিন নির্বাচন নিয়ে অনুসন্ধান করতে পারেন।
যাঁরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন কাভার করছেন, তাঁরা টুইটারে ফলো করতে পারেন আমাদের এই হ্যাশট্যাগ: #gijnElectionWatchdog। এখানে প্রতিদিন নতুন নতুন কৌশল ও পরামর্শের আপডেট পাবেন। আর যদি কোনো মতামত বা হালনাগাদ তথ্য দিতে চান, তাহলে ইমেইল করুন এখানে: ElectionWatchdog@gijn.org
এই গাইডে থাকছে ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে বাছাই করা সেরা রিসোর্স:
বিশ্লেষণ, জরিপ ও রাউন্ডআপ
কুক পলিটিক্যাল রিপোর্ট হলো স্বাধীন ও দলনিরপেক্ষ নির্বাচনী বিশেষজ্ঞদের একটি গ্রুপ, যারা যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন ও রাজনৈতিক প্রবণতা নিয়ে কাজ করে। তাদের সাইটে ফ্রি ও সাবস্ক্রিপশন; দুই ধরনের কনটেন্ট পাবেন।
ফাইভথার্টিএইট, নামটি অদ্ভুত শোনালেও এটি এসেছে মূলত ইউএস ইলেকটোরাল কলেজের (যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন) সদস্য সংখ্যা থেকে। সংগঠনটির কাছ থেকে খুবই গভীর রাজনৈতিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। পোলিং অ্যাগ্রিগেশনের জন্যও এটি খুব কাজের সাইট।
ইলেকশনল্যান্ড২০২০ হলো অলাভজনক গণমাধ্যম প্রোপাবলিকার একটি সহযোগিতামূলক সাংবাদিকতা প্রকল্প। তারা ২০২০ সালের নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার, সাইবার নিরাপত্তা, ভুয়া তথ্য ও নির্বাচনী সততা ইত্যাদি নিয়ে কাজ করছে।
প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্রে একজন করে রিপোর্টার আছেন বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-র। তাঁরা প্রতিদিন মাঠপর্যায়ের নানা খবরাখবর দিয়ে যাচ্ছেন নির্বাচনী কাভারেজের মাধ্যমে।
প্রচার অর্থায়ন
সেন্টার ফর রেসপনসিভ পলিটিকস (সিআরপি) একটি দলনিরপেক্ষ গবেষণা গ্রুপ, যারা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে অর্থের লেনদেন ট্র্যাক করে এবং নির্বাচনে ও নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তার প্রভাব নির্ধারণ করে। ফেডারেল ক্যাম্পেইন কন্ট্রিবিউশন, লবিং ডেটা ও নানা রকম বিশ্লেষণের জন্য যেতে পারেন তাদের ওয়েবসাইট ওপেনসিক্রেটস-এ।
নির্বাচনী প্রচারণায় যে অর্থায়ন হয়েছে, তা নিয়ে কাজ করার পরামর্শ, টুল ও টাইমলাইন পাওয়া যাবে সিআরপির লার্নিং সেন্টারে; স্থানীয় নির্বাচনে জাতীয় পর্যায় থেকে আসা অনুদান ট্র্যাক করে এই সেন্টার; এবং তাদের নিউজরুম স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতির ওপর নানা ধরনের বিশ্লেষণ হাজির করে।
ফেডারেল ইলেকশন কমিশন (এফইসি)-র কাছ থেকে পাওয়া নির্বাচনী অর্থায়নের ইলেকট্রনিক ফাইলগুলো খুব সহজে ব্রাউজ করতে পারবেন প্রোপাবলিকার এফইসি আইটেমাইজার-এর মাধ্যমে। এখানে তারিখ, কমিটি, সুপার প্যাকস, রেস ইত্যাদি অনেক বিষয় ধরে সার্চ করতে পারবেন।
ফলো দ্য মানি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণায় অর্থায়নের দিকে নজর রাখে এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন মানি ইন পলিটিকস (এনআইএমপি)।
এই সব নির্বাচনী অর্থায়নের ডেটার সূত্র এফইসি। এটিই কেন্দ্রীয় নির্বাচনী প্রচারণায় অর্থায়ন-সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা পর্যবেক্ষেণ ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠান।
রাজ্য পর্যায়ে নির্বাচনী প্রচারণায় অর্থায়নের ডেটা ও বিধিমালা নিয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে, দেখুন ন্যাশনাল কনফারেন্স অব স্টেট লেজিসলেটরস (এসসিএসএল) ডিসক্লোজার অ্যান্ড রিপোর্টিং রিকয়ারমেন্টস এবং দ্য ক্যাম্পেইন ফিন্যান্স ইনস্টিটিউটের অফিশিয়াল স্টেট এজেন্সিস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিপোর্টস।
বিজ্ঞাপন ব্যয়
অনলাইন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচারণায় কেমন খরচ করা হয়েছে, জানতে চান? সিআরপি সেটিও ট্র্যাক করে। এর পলিটিক্যাল অ্যাডস ট্র্যাকারের মাধ্যমে জানতে পারবেন ফেসবুক ও গুগলে এবং রেডিও ও টেলিভিশনে কত টাকার বিজ্ঞাপন চালানো হয়েছে।
কান্তার মিডিয়া, অ্যাডভারটাইজিং অ্যানালিটিকস বা মিডিয়া মনিটরস-এর মতো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও আপনি রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনী ব্যয়ের ডেটা কিনে নিতে পারেন। অ্যাডভারটাইজিং অ্যানালিটিকস তাদের টুইটার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেও নিয়মিত তথ্য জানায়।
বিজ্ঞাপনী ব্যয়সংক্রান্ত এসব ডেটা বিনা মূল্যে পাবেন ফেডারেল কমিউনিকেশনস কমিশন (এফসিসি)-র পাবলিক ইন্সপেকশন ফাইলস এবং এফইসি ক্যাম্পেইন ফিন্যান্স ডেটায়। কিন্তু এগুলো এমন ফরম্যাটে থাকে যে, সেগুলো সেখান থেকে বিশ্লেষণ করাটা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এফইসি ডেটায় বিজ্ঞাপনী ব্যয় খুঁজে পাওয়ার জন্য স্পেন্ডিং ট্যাবে গিয়ে “ডিসবার্সমেন্টস” নির্বাচন করুন, এরপর ফিল্টার করুন “অ্যাডভারটাইজিং” দিয়ে।
অনলাইন বিজ্ঞাপনে কত টাকা খরচ করা হয়েছে, তা ট্র্যাক করার পাশাপাশি এটি বোঝাও জরুরি, কীভাবে সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া তথ্যগুলো যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। এবং এ ব্যাপারে ফেসবুক, গুগল, রেডিট, স্ন্যাপচ্যাট ও টুইটারের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোর নীতিমালা কী?
বড় বড় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন পাবেন দ্য সেন্টার ফর ইনফরমেশন, টেকনোলজি অ্যান্ড পাবলিক লাইফ (সিআইটিএপি)-র ডিজিটাল পলিটিকস-এ। আরও দেখুন: প্ল্যাটফর্ম অ্যাডভারটাইজিং এবং পলিটিক্যাল অ্যাড ডেটাবেস কম্প্যারিজনস।
১৪টি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের নির্বাচন-সংক্রান্ত ভুয়া তথ্য মোকাবিলার নীতিমালা পর্যালোচনা করেছে ইলেকশন ইন্টেগ্রিটি পার্টনারশিপ। প্রতিটি প্ল্যাটফর্মের নীতিমালা ও তার কার্যকারিতা তারা আলাদা করে দেখিয়েছে।
গুগলের পলিটিক্যাল অ্যাডভারটাইজিং লাইব্রেরি পরিচালিত হয় এর ট্রান্সপারেন্সি রিপোর্টের অংশ হিসেবে। এবং এটি সাধারণত প্রতিদিন হালনাগাদ করা হয়। এ বিষয়ে আরও জানতে দেখুন তাদের সবচেয়ে বেশি আসা প্রশ্ন।
ফেসবুকের অ্যাড লাইব্রেরি রিপোর্টে আপনি বেশ কিছু বিষয় ধরে সার্চ করতে পারবেন। প্রার্থী, বিজ্ঞাপনদাতা ও জায়গা ধরে দেখতে পারবেন বিজ্ঞাপনী ব্যয়।
এনওয়াইইউ অনলাইন ট্রান্সপারেন্সি প্রজেক্ট সম্প্রতি একটি অ্যাড অবজারভেটরি চালু করেছে। এখানে ফেসবুকের অ্যাড লাইব্রেরির চেয়েও আরও অনেক সার্চ ফাংশন থাকায় আপনি বিজ্ঞাপনী ব্যয় দেখতে পারবেন রাজ্য ধরে ধরে। এ ছাড়া বিভিন্ন ট্রেন্ড সার্চ এবং নোটিফিকেশন তৈরি করা যাবে।
ভুয়া খবর ও যাচাই
নির্বাচনী প্রার্থীদের দাবি করা নানা তথ্য ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া পোস্টের সত্যতা দ্রুততার সঙ্গে যাচাই করে পয়েন্টার ইনস্টিটিউটের পোলিটিফ্যাক্ট।
অ্যানেনবার্গ পাবলিক পলিসি সেন্টার অব দ্য ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার একটি প্রকল্প, ফ্যাক্টচেক ডট অর্গ। পয়েন্টারের মতো তারাও যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের সময় বৈশ্বিক মনোযোগ আকর্ষণ করা শিরোনাম, বক্তৃতা ও বিভিন্ন দাবির সত্যতা যাচাই করে।
আমেরিকান প্রেস ইনস্টিটিউটের ফ্যাক্টচেকিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি জার্নালিজম প্রজেক্ট-এর সাপ্তাহিক নিউজলেটার, ফ্যাকচুয়ালি। এখানে অনুসন্ধান করা হয় ভুয়া তথ্য ছড়ানোর মতো ইস্যুগুলো নিয়ে।
ফার্স্ট ড্রাফট-এর ইনফোদ্যকিউ২০২০-তে পাবেন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ভুয়া তথ্য নিয়ে প্রাথমিক ধারণা। এগুলো মোকাবিলায় সাংবাদিকদের জন্য একটি টুলকিট ও নিউজরুমের জন্য তথ্য যাচাইয়ের রিসোর্স তৈরি করেছে ফার্স্ট ড্রাফট। দেখতে পারেন তাদের বিভিন্ন সাইবার অপরাধ কাভারের (ফিশিং, হ্যাকিং ও ভুয়া তথ্য) গাইডটিও, অ্যাট্রিবিউশন.নিউজ।
সাধারণভাবে বিভিন্ন তথ্য যাচাইয়ের জন্য, অবশ্যই দেখুন ডেটাজার্নালিজম ডট কমের ভেরিফিকেশন হ্যান্ডবুক, বেলিংক্যাটের অনলাইন ইনভেস্টিগেশন টুলকিট, এবং ক্রেইগ সিলভারম্যানের ভেরিফিকেশন অ্যান্ড ডিজিটাল ইনভেস্টিগেশন রিসোর্স।
নির্বাচনী কাভারেজের “হাউ-টু
আমেরিকান প্রেস ইনস্টিটিউট (এপিআই) বিভিন্ন নির্বাচনী প্রকল্পে সহায়তা দেয়, যেগুলো নিউজরুম ম্যানেজারদের সংযুক্ত করে এবং সেখানে উদ্ভাবনী উপায়ে নির্বাচন কাভার, ভুয়া তথ্য মোকাবিলা ও বিভিন্ন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।
এপিআই-এর ট্রাস্টেড ইলেকশন নেটওয়ার্ক প্রকাশ করেছে “গাইড টু কাভারিং ইলেকশন অ্যান্ড মিসইনফরমেশন”। আরও দেখুন: এপিআই-এর চার পর্বের প্রতিবেদন: গেটিং ইট রাইট: স্ট্র্যাটেজিস ফর ট্রুথ-টেলিং ইন আ টাইম অব মিসইনফরমেশন অ্যান্ড পোলারাইজেশন।”
সাবেক এক নির্বাচনী কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন কাভারের জন্য দিয়েছেন এই আট পরামর্শ। সব কটির মধ্যেই মূল একটা বিষয় বারবার এসেছে: নির্বাচনী প্রক্রিয়া, নিয়মনীতি সম্পর্কে ভালোমতো জানুন এবং হালনাগাদ থাকুন।
মেইল-ইন ভোটিং নিয়ে একটি কার্যকরী রিপোর্টিং গাইড তৈরি করেছে প্রোপাবলিকা। এখানে আছে প্রয়োজনীয় প্রেক্ষাপট ও পরামর্শ।
নির্বাচনে নিরাপত্তা
নির্বাচনী নিরাপত্তা নিয়ে ব্রেনান সেন্টার ফর জাস্টিস-এর বিশেষ একটি প্রকল্পে উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের ভোটিং ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলো। সঙ্গে আছে সেগুলো মোকাবিলার পরামর্শ ও নির্বাচনী বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগের উপায়। নিরাপদে ভোট আয়োজন নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচনী কর্মকর্তাকে কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে, সেটিও ধাপে ধাপে দেখানো হয়েছে এখানে। স্থানীয় কর্মকর্তারা কতটা প্রস্তুত, তা যাচাই করতে এটি ব্যবহার করতে পারেন।
নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে ন্যাশনাল পাবলিক রেডিওর বিশেষ সিরিজটিও এ বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য পাওয়ার ভালো উপায়।
নির্বাচনের দিনে যে সাতটি বাজে পরিস্থিতি দেখা যেতে পারে, তা নিয়ে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেছে নিউ ইয়র্ক টাইমস। এবং বলেছে: এগুলো মোকাবিলায় কী করা যেতে পারে।
নির্বাচনী এক্সপ্লেইনার
নির্বাচন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণ পাওয়ার জন্য দারুণ জায়গা ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির ইলেকশন ডেটা + সায়েন্স ল্যাব (এমইডিএসএল)। এখানে পাবেন বিভিন্ন পর্যায়ের ভোটিং, ব্যালট প্রাপ্তি ও পুরো ভোটিং ব্যবস্থার ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এ ছাড়া পাবেন নির্বাচনী ডেটাসেট ও টুল এবং বিশেষজ্ঞের খোঁজ।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনী মানচিত্র কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তা নজরে রাখে ফাইভথার্টিএইট (যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী ব্যবস্থায়, একজন প্রার্থী জনগণের ভোটে জিতলেও নির্বাচনে হেরে যেতে পারেন)।
নিউ ইয়র্ক টাইমসের এই ইন্টারঅ্যাকটিভে, প্রতিটি রাজ্যকে উপস্থাপন করা হয়েছে বর্তমান কুক পলিটিক্যাল রিপোর্টের রেটিং দিয়ে; যা থেকে বোঝা যায় কোনো রাজ্যে কোন প্রার্থীর জেতার সম্ভাবনা বেশি। এটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।
ভোটার অংশগ্রহণ ও ভোটের ধরনে সম্ভাব্য কিছু পরিবর্তনের দিকে নজর দিয়েছে ওয়াশিংটন পোস্ট এবং বোঝার চেষ্টা করেছে, এতে ট্রাম্প না বাইডেন—কে লাভবান হবেন। প্রতিবেদনের নিচে সব ডেটার সূত্রেরও একটি তালিকা দিয়েছে তারা।
আইনি ইস্যু ও নোংরা কৌশল
ডিজিটাল ডিসইনফরমেশন ও ভোট সাপ্রেশন নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে দ্য ব্রেনান সেন্টার ফর জাস্টিস। এখানে বলা হয়েছে: ২০২০ সালের নির্বাচন কী ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো বা নিবৃত্ত করার জন্য কী ধরনের কৌশল ব্যবহার করা হতে পারে, তার সম্ভাব্য একটি তালিকাও করেছে সেন্টার। অন্য আরও কিছু নোংরা কৌশলের দিকে নজর রাখার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে এখানে।
২০২০ সালের নির্বাচনের সঙ্গে যেসব আইনি মামলার বিষয় জড়িয়ে আছে, তা পর্যালোচনা করা হয়েছে এনসিএসএল-এর নিউজলেটার, দ্য ক্যানভাস-এ। এখানে চারটি মূল বিষয় তুলে ধরা হয়েছে: মেইলে নির্বাচন, অ্যাবসেন্টি ব্যালটের যোগ্য হবেন যে শর্তে, সাক্ষী হবার পূর্বশর্ত এবং কীভাবে ব্যালট ফেরত দেওয়া যায়।
স্টানফোর্ড-এমআইটি-র হেলদি ইলেকশনস প্রজেক্ট, একটি নির্বাচনী মামলাসংক্রান্ত ট্র্যাকার তৈরি করেছে। কোভিড-সংক্রান্ত নির্বাচনী মামলাগুলো এই ডেটাবেসে যুক্ত হয়।
নির্বাচনসংক্রান্ত আইনকানুন সম্পর্কে জানানোর জন্য ইবেঞ্চবুক তৈরি করেছে উইলিয়াম অ্যান্ড ম্যারি ল স্কুল এবং দ্য ন্যাশনাল সেন্টার ফর স্টেট কোর্টস। এখানে আপনি রাজ্য ধরে ধরে আইনকানুন সম্পর্কে সার্চ করতে পারবেন। এবং প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন আইনি নথি পাবেন।
নির্বাচনী প্রচারণায় অর্থায়ন, ভোটের অধিকার ও সরকারের নৈতিকতা নিয়ে কাজ করে অলাভজনক, দলনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান ক্যাম্পেইন লিগাল সেন্টার।
নির্বাচন কাভারের সময়, কোনো ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিকদের কী ধরনের আইনি অধিকার থাকে, সে সম্পর্কে জানা-বোঝা তৈরির জন্য একটি গাইড তৈরি করেছে রিপোর্টার্স কমিটি ফর ফ্রিডম অব দ্য প্রেস।
২০২০ মার্কিন নির্বাচনের সময় সাংবাদিকদের শারীরিক ও ডিজিটাল—দুই ধরনের সুরক্ষার জন্য অনেক বাস্তবিক পরামর্শ ও রিসোর্স দিয়ে একটি সুরক্ষা গাইড বানিয়েছে কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস। কীভাবে বট শনাক্ত করবেন এবং আপনার মোবাইল বা কম্পিউটারকে সেগুলো থেকে রক্ষা করবেন, অনলাইন ট্রল বা ভুয়া তথ্যের জোয়ার কীভাবে মোকাবিলা করবেন; ইত্যাদি জরুরি প্রসঙ্গ এখানে আলোচনা করা হয়েছে।
ভাষণ, অনুলিখন, টুইট ও ভিডিও
প্রচারণা ও নির্বাচনের ভিডিও এবং ২০২০ সালের নির্বাচনী প্রচারণার আর্কাইভে আপনি বিভিন্ন কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করতে পারবেন। এগুলোর সবকিছুই পাওয়া যাবে পাবলিক-সার্ভিস কেবল নেটওয়ার্ক, সি-স্প্যানে।
আরও দেখতে পারেন ভোট স্মার্ট। এখানে প্রার্থীদের অবস্থান, বিগত নির্বাচনের রেকর্ড ও জনসমক্ষে দেওয়া বক্তৃতা ট্র্যাক করা হয়।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, তাঁর যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন টুইটারকে। ফলে ট্রাম্প টুইটার আর্কাইভ ও ট্রাম্পের ডিলিট করে দেওয়া টুইটগুলো নিয়ে ফ্যাক্টবেসের এই আর্কাইভ থেকেও আপনি অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। আর প্রেসিডেন্টের আনুষ্ঠানিক সরকারি নথিপত্রের জন্য দেখুন এই আর্কাইভ।
ভোটার ডেটা
ডেমোগ্রাফিক ডেটার ওপর ভিত্তি করে মানুষ খোঁজা ও চিহ্নিত করার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় ভোটার নিবন্ধন ডেটা। এগুলো ব্যবহৃত হয় নির্বাচনী প্রচারণায়, সংবাদমাধ্যমে এবং অন্য আরও নানা ক্ষেত্রে। এল২ পলিটিকাল-এর মতো জায়গা থেকে এ রকম ডেটাসেট পাওয়া যায়। লেক্সিসনেক্সিস-এর মতো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও এগুলো পাওয়া যায়। ডেটাসেটের দাম নির্ভর করে বেশ কিছু বিষয়ের ওপরে।
ভোটার নিবন্ধন তালিকা, সবার জন্য উন্মুক্ত নথি। যেকোনো নাগরিক এটি পেতে পারে। কোন রাজ্যে কী ধরনের তথ্য, কার জন্য উন্মুক্ত অবস্থায় আছে; তা দেখতে পারবেন এখানে।
ভোটার নিবন্ধন ডেটায় কী ধরনের তথ্য আছে, সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জানতে রাজ্য পর্যায়ের বা স্থানীয় নির্বাচনী কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ভোটকেন্দ্রের তালিকা, ব্যালট ব্যবস্থাপনা, নির্বাচনী আইনসহ নানা বিষয়ে তথ্যও আপনি পেতে পারেন এমন যোগাযোগের মাধ্যমে।
ভোটের অধিকার ও নীতিমালা
যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচন আসলে স্থানীয় পর্যায় থেকে গড়ে ওঠে। নির্বাচনগুলো আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকে নিজ নিজ রাজ্য ও অঞ্চলের। দুটি রাজ্যের কর্মপদ্ধতি কখনো একই রকম হয় না।
ভোটার আইডির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ভোটিং সেন্টারের ঠিকানা, অনুপস্থিতদের ব্যালট কবে মেইল করা হবে, কবে ভোট গণনা শুরু হতে পারে; ইত্যাদি নানা তথ্য ক্রমাগত হালনাগাদ করে দ্য ন্যাশনাল কনফারেন্স অব স্টেট লেজিসলেটরস (এসসিএসএল)। রাজ্যভিত্তিক নির্বাচনী আইনকানুনের একটি সার্চ-যোগ্য ডেটাবেসও আছে তাদের।
এটির সঙ্গে যোগ করুন ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব স্টেট ইলেকশন ডিরেক্টরস-এর এই রিসোর্স তালিকা এবং ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব সেক্রেটারিয়েট অব স্টেট (এনএএসএস)-এর ক্যান আই ভোট ওয়েবসাইটকে। এগুলো একসঙ্গে মিলিয়ে দেখলে আপনি যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনসংক্রান্ত নীতিমালা, পদ্ধতি ও প্রযুক্তি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেয়ে যাবেন।
নির্বাচনী প্রশাসনিক জরিপের মাধ্যমে অনুপস্থিতদের ভোট দেওয়ার তারিখ, রাজ্যের নির্বাচনী আইনসহ নানা বিষয়ে নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ করে এনএএসএস।
এসিএলইউ-এর লেট পিপল ভোট সাইটটির মাধ্যমে সহজেই প্রতিটি রাজ্যের ভোটিং নিবন্ধনের তারিখ এবং নানা তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়।
অনুপস্থিতদের ভোট দেওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে ও বাইরে থাকা নাগরিকদের নিবন্ধনের সেবা দেওয়া নিয়ে যারা কাজ করে, তাদের একটি তালিকা তৈরি করেছে ইউএস ভোট ফাউন্ডেশন।
এবং প্রতিটি রাজ্যে মেইলের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা চালুর জন্য নির্বাচনী কর্মকর্তা ও অ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলোর সঙ্গে মিলে কাজ করছে ন্যাশনাল ভোট অ্যাট হোম ইনস্টিটিউট।
আগে থেকেই বিতর্কিত অবস্থায় থাকা ভোটিং ইস্যুকে আরও সমস্যাদায়ক করে তুলেছে কোভিড-১৯ মহামারি। পুরো প্রক্রিয়ায় গতি আনার জন্য কোন রাজ্য কী ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে, তার একটি বিবরণ তুলে ধরেছে এনবিসি নিউজ।
ভোটের ফলাফল
২০২০ সালের এই নির্বাচনে অনেক বেশি মাত্রায় ভোটার অনুপস্থিতি দেখা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে ফলাফল নিয়ে রিপোর্টিংয়েও বিলম্ব হতে পারে। সংকটপূর্ণ সময়ে বৈধ নির্বাচন আয়োজন নিয়ে পড়ুন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির এরভিন স্কুল অব ল-এর এই লেখা। বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সুপারিশের কথাও বলা হয়েছে এখানে।
দ্য ইলেকটরাল কলেজ: এ ২০২০ প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন টাইমলাইন। কংগ্রেশনাল রিসার্চ সার্ভিসের এই প্রতিবেদনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: কীভাবে এই নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত এসেছে। এবং এখানে সব কটি ডেডলাইন, নিয়মনীতি ও দৃশ্যপটের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভোট দেওয়ার পর কী কী ঘটতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় প্রতিটি রাজ্য ও ন্যাশনাল প্রাইমারি, সাধারণ নির্বাচন ও গণভোটের ফলাফল সুবিন্যস্তভাবে হিসাব করে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস। কীভাবে তারা সেই কাজ করে, তা জানতে পারবেন এখানে। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে তাদের তাৎক্ষণিক খবরাখবর জানতে টুইটারে ফলো করুন: #APracecall।
নির্বাচনের পর ফলাফল নিয়ে আইনি বা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ শুরু হলে, তার পরিণতি কী হতে পারে?
এ বিষয়ে খুবই বিস্তারিত একটি বিশ্লেষণ দিয়েছেন ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের অধ্যাপক এডওয়ার্ড বি. ফলি। প্রিপেয়ারিং ফর আ ডিসপুটেড প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন: এন এক্সারসাইজ ইন ইলেকশন রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট।
ভোট গ্রহণ শেষ হয়ে যাওয়ার পর মানুষ যদি নির্বাচনী ফলাফল মেনে না নেন, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান, ইলেকটোরাল কলেজ, কংগ্রেস ও ভাইস প্রেসিডেন্টের ভূমিকা কী হবে, তা এই লেখায় ব্যাখ্যা করেছেন হার্ভার্ড ল স্কুলের অধ্যাপক কাস আর. সানস্টেইন: “পোস্ট-ইলেকশন ক্যাওস: আ প্রাইমার”।
আরেক আইনের অধ্যাপক রিচার্ড হাসেন ২০২০ সালের জানুয়ারিতে এনপিআর-এর টেরি গ্রোসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আলোচনা করেছিলেন তাঁর বই নিয়ে: ইলেকশন মেল্টডাউন: ডার্টি ট্রিকস, ডিসট্রাস্ট অ্যান্ড দ্য থ্রেট টু আমেরিকান ডেমোক্রেসি।
 টবি ম্যাকিনটোশ ও জিআইজেএন স্টাফদের সহায়তা নিয়ে এই গাইডটি তৈরি করেছেন জিআইজেএন রিসোর্স সেন্টারের পরিচালক লিন ডোমবেক। তিনি এর আগে এনবিসি নিউজ, এবিসি নিউজ, টাইম ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের গবেষণা দল পরিচালনা করেছেন। এপিতে তিনি ১০ বছর ধরে কাজ করেছেন গবেষণা পরিচালক হিসেবে।
টবি ম্যাকিনটোশ ও জিআইজেএন স্টাফদের সহায়তা নিয়ে এই গাইডটি তৈরি করেছেন জিআইজেএন রিসোর্স সেন্টারের পরিচালক লিন ডোমবেক। তিনি এর আগে এনবিসি নিউজ, এবিসি নিউজ, টাইম ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের গবেষণা দল পরিচালনা করেছেন। এপিতে তিনি ১০ বছর ধরে কাজ করেছেন গবেষণা পরিচালক হিসেবে।