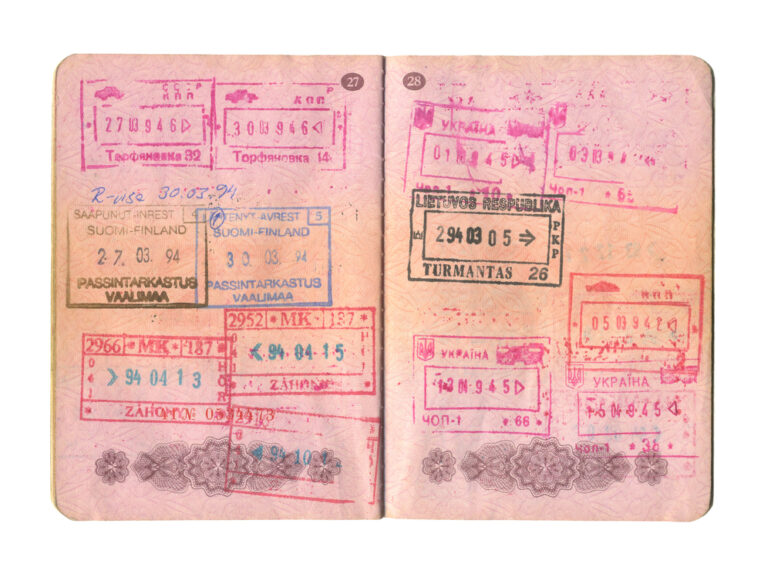Illustration: Marcelle Louw for GIJN
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
ভূমিকা: আরব উপসাগরীয় অঞ্চলে অভিবাসন নিয়ে রিপোর্টিংয়ের জিআইজেএন গাইড
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
অধ্যায় ১: উত্তম চর্চা ও কোভিড যুগের উপযোগী বিষয়বস্তু
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
অধ্যায় ২ : কোভিড-১৯ এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের অভিবাসী শ্রমিক
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
অধ্যায় ৩: পরিসংখ্যান ও গবেষণা
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
অধ্যায় ৪: দরকারি পাঠ
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
অধ্যায় ৫: বিশেষজ্ঞ গাইড
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
অধ্যায় ৬: মানব পাচারের কেস স্টাডি
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
অধ্যায় ৮: গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
অধ্যায় ৯: পাচার ও বলপূর্বক শ্রম সংক্রান্ত পরিভাষা
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
অধ্যায় ১০: বাহরাইনের জন্য রিপোর্টিং গাইড
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
অধ্যায় ১১: কুয়েতের জন্য রিপোর্টিং গাইড
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
অধ্যায় ১২: ওমানের জন্য রিপোর্টিং গাইড
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
অধ্যায় ১৩: কাতারের জন্য রিপোর্টিং গাইড
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
অধ্যায় ১৪: সৌদি আরবের জন্য রিপোর্টিং গাইড
অধ্যায় গাইড রিসোর্স
অধ্যায় ১৫: সংযুক্ত আরব আমিরাতের জন্য রিপোর্টিং গাইড
বলপূর্বক শ্রম, মানব পাচার এবং অবৈধ অভিবাসন বিশ্বের সবখানেই আছে। তবে গাল্ফ কোঅপারেশন কাউন্সিল (জিসিসি) এবং বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা (মেনা) অঞ্চলের শ্রম ও অভিবাসনসংক্রান্ত আইন ও চর্চায় এমন কিছু সুনির্দিষ্ট ও অভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো বলপূর্বক শ্রম ও মানব পাচারকে উৎসাহিত করে।
সংজ্ঞা
বলপূর্বক শ্রম নিয়োজন। এর মানে, এমন কাজ বা সেবা, যা কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে জোর করে বা শাস্তির হুমকি দিয়ে করানো হয়, এবং যেই কাজে তিনি নিজে যেচে যাননি অথবা স্বেচ্ছায় করতে রাজি হননি। শাস্তির হুমকি বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে, আটক অথবা জেল, মজুরি দিতে অস্বীকৃতি, শ্রমিকের অবাধ ঘোরাফেরায় বাধা, পরিচয়পত্র জব্দ করে নেওয়া এবং ঋণ শোধের নামে বেতনের একটি অংশ আটকে রাখা। শ্রমিকদের কাজের ধরন সম্পর্কে বিভ্রান্ত করাও অনিচ্ছা শ্রমের মধ্যে পড়ে।
বলপূর্বক যৌন শ্রম। এমন শ্রম বা সেবা, যেখানে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কোম্পানি জোর করে কাউকে বাণিজ্যিক যৌন পেশায় যেতে বাধ্য করে।
ঋণগ্রস্ততা। ঋণ শোধের বিনিময়ে যে শ্রম ও সেবা দেওয়া হয়। অভিবাসী শ্রমিকেরা কাজের খোঁজে প্রায়ই বড় অঙ্কের ঋণ নিয়ে থাকেন এবং নিয়োগকর্তার জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তাঁর বেতন থেকে ঋণের টাকা শোধ করতে হয় বলে তাঁরা চাপিয়ে দেওয়া কাজও প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। ঋণগ্রস্ততাকে আধুনিক দাসত্বের জন্য অন্যতম বড় ঝুঁকি হিসেবে ধরা হয়।
আধুনিক দাসত্ব। মনে রাখা প্রয়োজন, আধুনিক দাসত্ব কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন দিয়ে নির্ধারিত কোনো পরিভাষা নয়। কখনো কখনো বলপূর্বক শ্রম বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহার করা হয় এবং এটি মূলত শ্রম সাপ্লাই চেইনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। গ্লোবাল এস্টিমেট অন মডার্ন স্লেভারির সাম্প্রতিক সংস্করণে জোর করে বিয়ে করানোকেও এই শব্দের আওতায় আনা হয়েছে।
“অবৈধ” অভিবাসন/অভিবাসী। উৎস, ট্রানজিট এবং গন্তব্য দেশের আইনি কাঠামোর বাইরে যে অভিবাসন হয়, তাঁরাও “অবৈধ” অভিবাসী হতে পারেন, যাঁরা বৈধ উপায়ে কোনো দেশে গেলেও পরবর্তী সময়ে কোনো কারণে সেখানে বসবাসের বৈধতা হারিয়েছেন।
দ্রষ্টব্য: “অবৈধ অভিবাসন” শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয় সরকারি ও রাষ্ট্রীয় প্রকাশনাগুলোতে। তবে একাডেমিক ও নাগরিক সমাজের কর্মীরা সতর্ক করে বলে থাকেন যে, এই শব্দের ব্যবহার অভিবাসীদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করে। বিশেষ করে আলোচ্য অঞ্চলে, অভিবাসীদের আনডকুমেন্টেড (বৈধ কাগজহীন) বানাতে রাষ্ট্র এবং নিয়োগদাতারা শব্দটিকে প্রশ্রয় দেয়। বিকল্প পরিভাষার মধ্যে রয়েছে “অনিয়মিত অভিবাসন” এবং “অনিয়মিত অভিবাসী”। এই শব্দগুলোর কোনো নির্দিষ্ট অথবা আইনি সংজ্ঞা নেই।
মানব পাচার। এর মানে, আন্তর্জাতিক সীমানার বাইরে অথবা একক দেশের সীমানার ভেতরে, শোষণের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ, পরিবহন, স্থানান্তর, আশ্রয় প্রদান বা গ্রহণ করা। এর মধ্যে রয়েছে বলপ্রয়োগ, প্রতারণা, অপহরণ, ক্ষমতার অপব্যবহার বা যেকোনো ধরনের জোর-জবরদস্তির হুমকি অথবা প্রয়োগ। মানব পাচারের উদ্দেশ্যই হলো শোষণ, যার মধ্যে আছে পতিতাবৃত্তি, বলপূর্বক শ্রম, দাসত্ব বা দাসবৃত্তি।
মানব পাচারের ঝুঁকি যা তৈরি করে
- নিরাপদ অভিবাসনের সুযোগ এবং পাচারের ঝুঁকি সম্পর্কে সম্ভাব্য অভিবাসীদের জন্য পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব।
- আইনসম্মত অভিবাসনের পথে বাধা সৃষ্টি করা। যেমন: উৎস বা গন্তব্য দেশে কর্মসংস্থান নিষিদ্ধ করা।
- যৌন সেবা বা সস্তা শ্রমের দাবি।
- বৈষম্য ও অনিয়মিত স্ট্যাটাসের কারণে অভিবাসী শ্রমিকদের দুর্দশা
এই অঞ্চলের কয়েকটি অভিন্ন সমস্যা
চুক্তি প্রতিস্থাপন
প্রায় ক্ষেত্রেই শ্রমিকেরা তাঁদের উৎস দেশে নিয়োগকারী এজেন্টের সঙ্গে যে চুক্তি সই করেন, শেষ পর্যন্ত গন্তব্য দেশে গিয়ে স্বাক্ষরিত চুক্তি তার চেয়ে আলাদা হয়। এজেন্টরা নিয়মকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করলেও বিভিন্ন দেশ এই “মুলা ঝোলানোর” চর্চা মোকাবিলায় পদক্ষেপ নিয়েছে। এই ধরনের চর্চার কারণে শ্রমিকেরা প্রত্যাশার চেয়ে কম মজুরির চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারেন, আরও দীর্ঘ সময় বা পুরোপুরি ভিন্ন জায়গায় কাজ করতে বাধ্য হতে পারেন। চুক্তি প্রতিস্থাপনের ঘটনা বেশি ঘটে অননুমোদিত অভিবাসন রুটের ক্ষেত্রে।
চুক্তি প্রতিস্থাপন হলো প্রতারণামূলক নিয়োগের একটি মাধ্যম মাত্র। এই প্রক্রিয়ায় দালাল বা রিক্রুটিং এজেন্টরা সাধারণত অভিবাসী শ্রমিকদের কাছে স্বপ্ন বিক্রি করে এই বলে যে, তাঁরা উপসাগরীয় দেশগুলোতে গেলে ধনী হয়ে যাবেন। এই শ্রমিকদের যে মজুরি এবং কাজের পরিবেশের আশ্বাস দেওয়া হয়, সেগুলো বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে।
চড়া রিক্রুটমেন্ট ফি
জিসিসি দেশগুলোর আইন অনুযায়ী, নিয়োগের জন্য (ফ্লাইটসহ) সব ধরনের ফি দেওয়ার কথা নিয়োগকর্তাদের। কিন্তু অনেক সময় অভিবাসী কর্মীরা উৎস দেশেই নিজে নিজের নিয়োগ ফি প্রদান করেন। অত্যন্ত চড়া এই ফির টাকা জোগাতে গিয়ে শ্রমিকেরা প্রায়ই ঋণ নিয়ে থাকেন, অথবা নিয়োগকর্তার কাছে ঋণী হয়ে পড়েন (ওপরে দেখুন, “ঋণগ্রস্ততা”)। এর ফলে তাঁদেরকে বেতনের কিছু অংশ রিক্রুটিং প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দিতে হয়। অনেক সময় নিয়োগকর্তারা শ্রমিকদের বেতন থেকে রিক্রুটিং প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া ফির টাকা কেটে রাখেন। অবশ্য অনেকেই বলে থাকেন, এমন ঘটনা এখন কম ঘটছে (বা অন্তত কম হারে রিপোর্টিং করা হচ্ছে)। কারণ, উপসাগরীয় তিনটি রাষ্ট্র শ্রমিকদের ঠিকমতো বেতন দেওয়া হচ্ছে কি না, তার ওপর নজরদারি করতে তথাকথিত মজুরি সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে। এই ব্যবস্থার সাফল্যও একেকখানে একেক রকম (নিচে দেখুন, “মজুরি না দেওয়া”)।
মজুরি না দেওয়া
জিসিসি দেশগুলোতে শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ না করা একটি সাধারণ অভ্যাস। মজুরি সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োগ করেও এই প্রবণতা পুরোপুরি দূর করা যায়নি। এই চর্চা কোনো নির্দিষ্ট খাতে সীমাবদ্ধ নয়। তবে দীর্ঘদিন ধরে বেতন না দেওয়ার কারণে সবচেয়ে বেশি ভোগেন গার্হস্থ্য ও কৃষি কর্মীদের মতো বিচ্ছিন্ন শ্রমিকেরা। কাজের জায়গা ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে না বলে বেশির ভাগ সময়ই তাঁরা অন্যায় সম্পর্কে অভিযোগ জানাতে পারেন না। তবে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া কিংবা নগদ সংকটে থাকা বড় বড় কোম্পানিতেও মজুরি পরিশোধ না করার ঘটনা ঘটে। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো, সৌদি ওগার।
ফ্রি ভিসা
“ফ্রি ভিসা” মানে হলো, স্পন্সরকে টাকা দিয়ে কোনো অভিবাসীর একটি দেশে গিয়ে বৈধভাবে বসবাস করা। তবে পরে সেই দেশে গিয়ে বিভিন্ন নিয়োগদাতার সঙ্গে স্বাধীনভাবে কাজ করা। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, উপসাগরীয় অঞ্চলের অভিবাসীদের কেবল সেই নিয়োগকর্তাদের জন্য কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়, যারা তাঁদের স্পনসর করে (যখন নিয়োগকর্তা নিবন্ধিত সাবকন্ট্রাক্টর হয় এবং তাঁরা একাধিক সাইটে কাজের জন্য নিযুক্ত হন)। ফ্রি ভিসায় যাওয়া অভিবাসীরা অন্যদের চেয়ে বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারেন। সাধারণত গৃহকর্মী এবং শ্রমিকেরা ফ্রি ভিসা বেশি ব্যবহার করেন।
ফ্রি ভিসায় যাওয়া অভিবাসীরা যে সব সময় ভিকটিম হন, এমন নয়। কেউ কেউ এই পথ বেছে নেন; কারণ, এখানে কাজের সময়ের ক্ষেত্রে নমনীয়তা পাওয়া যায় এবং তাঁরা কী কাজ করবেন, তা নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারেন। এভাবে তাঁদের আয়ের সুযোগও বাড়ে। কিন্তু ফ্রি ভিসা তখনই শোষণের অস্ত্র হয়ে ওঠে, যখন স্পন্সর বা কোনো অনিয়মিত নিয়োগকর্তা তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়, চড়া ফি দাবি করে অথবা প্রতিশ্রুত মজুরি দিতে অস্বীকৃতি জানায়।
গৃহকর্মী কেনাবেচা

ইলাস্ট্রেশন: জিআইজেএন-এর জন্য মার্সেল লো
বিশেষত গার্হস্থ্য শ্রমিকেরা “দাস ব্যবসার” ঝুঁকিতে থাকেন বেশি। এর বিভিন্ন রূপ আছে। দালালেরা গৃহকর্মীদের জিসিসি অঞ্চলের এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাচার করেন। কখনো তাঁদের জন্য কর্মসংস্থানের দেশের কাগজপত্র জোগাড় করা হয়, আবার কখনো কাগজপত্র ছাড়াই কাজে যোগ দিতে হয়। এটি তখনই বেশি ঘটে, যখন কোনো উৎস দেশ নির্দিষ্ট গন্তব্য দেশে গৃহকর্মীদের ট্রানজিট স্থগিত বা নিষিদ্ধ করে। এতে আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে গৃহকর্মীর চাহিদা মেটানো আরও কঠিন হয়ে পড়ে এবং কালোবাজারি সমৃদ্ধ হয়।
“গৃহকর্মী বাণিজ্য” একটি দেশের ভেতরেও ঘটতে পারে, এমনকি বৈধ ভিসা এবং রেসিডেন্স পারমিট থাকার পরও। এমন ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা তাঁদের গৃহকর্মীদের “বিক্রি” করে দেন। এর অর্থ: তাঁরা শ্রমিকের স্পনসরশিপ হস্তান্তর করার জন্য অন্যের কাছ থেকে টাকা নেন। যেসব নিয়োগকর্তা বিদেশ থেকে নতুন কাউকে আনতে বা নিয়োগ দিতে চান না, তাঁদের জন্য এই পথটাই সহজ। যেসব দেশ একটি নির্দিষ্ট দেশ থেকে গৃহকর্মী আনা নিষিদ্ধ করেছে, সেখানে এ ধরনের বাণিজ্য আরও সাধারণ হয়ে ওঠে। কারণ, কোনো নির্দিষ্ট জাতীয়তার গৃহকর্মীর ব্যাপারে নিয়োগকর্তাদের আগ্রহ থাকতে পারে।
পাচার ও বলপূর্বক শ্রম
ওপরের চর্চাগুলো ব্যাপকভাবে ঘটে থাকে এবং অনেক জায়গায় “সাধারণ” বলে বিবেচিত। এর অর্থ হলো, যেকোনো “সাধারণ” নিয়োগদাতা মানব পাচারে জড়িত হতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনই তাঁদের এমন আচরণ ও কাজকে উৎসাহিত করে অথবা তাতে সম্মতি দেয়। ফলে অনেকে জানেনই না, তাঁদের এসব কর্মকাণ্ড পাচারের আওতায় পড়ে। শ্রম অভিবাসনে একাধিক পক্ষ জড়িত থাকে। কখনো কখনো একটি পক্ষ (নিয়োগকারী এজেন্ট বা নিয়োগকর্তা) অন্য পক্ষের অজান্তে একজন অভিবাসীকে পাচার করে দেয়। এই চর্চা কমিয়ে আনার জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো, রিক্রুটারদের সম্পর্কে নিয়োগদাতাদের (এমপ্লয়ার) ভালো ধারণা থাকা; এবং শ্রমিক নিয়োগদাতাদের সম্পর্কে রিক্রুটারদের আরও সচেতন করা।
এটি বলা জরুরি যে, কয়েকটি দেশের আপাত-পাচারবিরোধী উদ্যোগ সত্ত্বেও, শ্রমিক নির্যাতনের বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা বরাবরই অপ্রতুল ও অসম্পূর্ণ ছিল। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যৌন-পাচার রোধে যতটা গুরুত্ব দেয়, শ্রমসংশ্লিষ্ট পাচারের দিকে ততটা মনোযোগ দেয় না। আবার, পাচারের শিকার ব্যক্তিরা কারাগারে কিংবা ফেরত পাঠানোর আশঙ্কায় কথা বলতে এগিয়ে আসতেও রাজি হন না। বিভিন্ন দেশও তাঁদের ভূখণ্ড থেকে পাচারের সংখ্যা কমিয়ে দেখায়। তবে কোন দেশ কতটা আন্তরিকতার সঙ্গে বিষয়টি মোকাবিলার চেষ্টা করছে, তার একটি নির্ভরযোগ্য মূল্যায়ন পাওয়া যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাফিকিং ইন পারসনস রিপোর্ট থেকে।
অনিবন্ধিত (বৈধ কাগজহীন) অভিবাসী
ওপরে যত রকমের চর্চার কথা বলা হয়েছে, এমন একাধিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় অভিবাসী শ্রমিকদের। ফলে চাইলেও তাঁদের জন্য চাকরি ছেড়ে দেওয়া আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এরপরও যাঁরা নির্যাতনমূলক বা অসুখী কাজের পরিবেশ ছেড়ে যেতে চান, তাঁদের হাতেও নিয়োগকর্তাকে পরিবর্তনের খুব একটা উপায় থাকে না মূলত নিয়ন্ত্রণমূলক স্পনসরশিপ আইন এবং নিয়োগকর্তাদের আদালতে মোকাবিলা করার মতো বাধার কারণে। যে অভিবাসীরা তাঁদের নিয়োগকর্তার সম্মতি না নিয়ে চাকরির ছেড়ে দেন, তাঁদের “পলাতক” শ্রমিক হিসেবে রিপোর্টিং করা হয় এবং তাঁদের স্ট্যাটাস সঙ্গে সঙ্গে “অনিয়মিত” হয়ে যায়।
কাজ ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক শ্রমিকেরা দেশে ফিরতেও অসুবিধায় পড়েন। কাতার ও সৌদি আরবে যেসব অভিবাসী দেশ ত্যাগ করতে চান, তাঁদের অবশ্যই নিয়োগকর্তার কাছ থেকে এক্সিট ভিসা আকারে অনুমতি নিতে হয়। অন্যান্য দেশে, আগেই পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে নেওয়ার কারণে সাধারণত শ্রমিকেরা সহজেই অভিবাসনের দেশ ছেড়ে যেতে পারেন না; এমনকি স্বল্প আয়ের সেই শ্রমিকদের ফিরতি ফ্লাইটের টিকিটের টাকা জোগানো কিংবা নিয়োগের জন্য চড়া ফি দেওয়ার সামর্থ্য থাকলেও।
কাফালা ব্যবস্থা
কাফালা বা স্পনসরশিপ ব্যবস্থা এই অঞ্চলের প্রতিটি দেশে আলাদা। তবে এই ব্যবস্থার একটি সাধারণ অভিঘাত হলো বড় আকারের অনিবন্ধিত (বৈধ কাগজহীন) অভিবাসী জনসংখ্যা। অভিবাসীদের বৈধ রেসিডেন্সি দলিল না থাকলে সাধারণত তাঁদেরকে “অবৈধ” হিসেবে উল্লেখ করে জিসিসি রাষ্ট্রগুলো এবং সেখানকার গণমাধ্যম। তবে বেশ কয়েকটি কারণে সাংবাদিকদের এই শব্দ বাদ দিতে হবে। প্রথমত, “অবৈধ” শব্দটি অমানবিক; এবং অভিবাসীমাত্রই যে অপরাধী, এমন ছাঁচেঢালা ধ্যানধারণাকে এটি আরও পোক্ত করে। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের অনিচ্ছুক স্থিতি ও বৈধতাহীনতার ক্ষেত্রে অন্যায্য আইন ও নিয়োগকর্তাদের যে দায়, তাকে এই শব্দটি আরও অস্পষ্ট করে তোলে।
নোট: কোথাও “অবৈধ নিয়োগদাতা” বলে কোনো শব্দ নেই। অথচ তাঁদের কারণেই অভিবাসী শ্রমিকেরা “অনিবন্ধিত” বা “বৈধতাহীন” হয়ে পড়েন। নিয়োগকর্তা পরিবর্তন করে একটি দেশে আইনসম্মতভাবে থাকার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় এই কাফালা বা স্পন্সরশিপ ব্যবস্থা। এই অনিবন্ধিত শ্রমিকেরা স্থানীয় অর্থনীতির একটি জরুরি উপাদান এবং তাঁরা স্থানীয় দোকানে সাধারণ শ্রমিক অথবা ফ্রিল্যান্স গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করে থাকেন।
জিসিসি দেশগুলো নিয়মিতভাবে অননুমোদিত কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় এবং তাঁদের ফেরত পাঠানোর জন্য এক জায়গায় জড়ো করে। এই দেশগুলো মাঝেমধ্যে অনিবন্ধিত কর্মীদের সাধারণ ক্ষমা করে দেয়, তাদের দূতাবাসের সহযোগিতায় বিনা শাস্তিতে বা কালো তালিকাভুক্ত করে দেশে ফিরতে অনুমতি দেয়। তবে এই ধরনের সুবিধাগুলো নিয়োগকারীদেরও জবাবদিহি থেকে মুক্ত করে দেয়। কারণ, এরপর কর্তৃপক্ষ আর অভিবাসীদের অনিয়মিত স্ট্যাটাসের মূল কারণগুলো সমাধানের কোনো উদ্যোগ নেয় না। অ্যামনেস্টি বা সাধারণ ক্ষমার সময় অননুমোদিত কর্মীদের ব্যাপকভাবে ধরপাকড়ও করা হয়। আর নীতিতে বড় কাঠামোগত পরিবর্তন না আসায় অনিয়মিত অভিবাসন এবং বিশেষ করে জোর খাটানোর মতো অনিয়ম—চলতেই থাকে।
এই অঞ্চলে অনিবন্ধিত শ্রমিকের সংখ্যা সম্পর্কে কয়েকটি জায়গা থেকে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পেতে পারেন। পুলিশ বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রিপোর্টে নির্দিষ্ট সময়ে, বিশেষ করে সাধারণ ক্ষমার সময়ে কতজন বহিষ্কৃত হলেন, সেই সংখ্যা থাকতে পারে। তবে উৎস দেশের দূতাবাস এবং কর্তৃপক্ষ অনেক সময় তাদের দেশের ফেরত পাঠানো নাগরিকদের তথ্য রাখে।