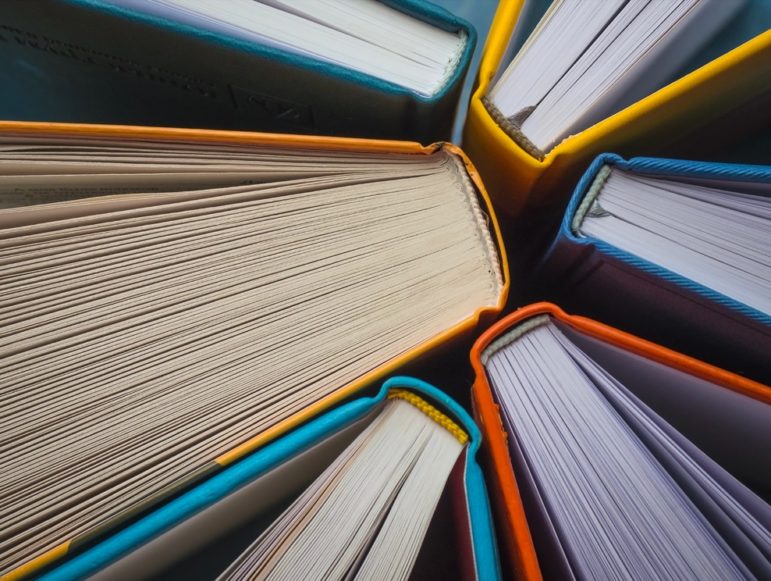বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল নিয়ে প্রতিবেদন করবেন যেভাবে

ছবি: শাটারস্টক
কোনো নতুন গবেষণা কিছু একটা প্রমাণ করেছে – সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনে এমনটি বলা হলে সেটিকে নিঃসন্দেহে ভুল বলে ধরে নিতে পারেন।
গণিত ছাড়া অন্য বিষয়ের গবেষণা কোনো কিছু “প্রমাণ” করে না। সেগুলোতে প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় – সেই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ অনেক সময় বেশ শক্তিশালীও হয়।
বিজ্ঞান যে প্রামাণিক তথ্য সংগ্রহ ও সেটিকে খতিয়ে দেখার একটি চলমান প্রক্রিয়া, সেটি সাংবাদিকদের জানতে হবে। এখানে প্রতিটি নতুন আবিষ্কার আগের আবিষ্কারের ভিত্তিতে হয় বা আগের আবিষ্কার নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে। সাধারণত কোনো বিষয় বা সমস্যাকে পুরোপুরি বোঝার ক্ষেত্রে গবেষণা হলো ছোট একটি পদক্ষেপ মাত্র।
এমনকি বিজ্ঞানীদের কাছে যথেষ্ট শক্তিশালী প্রামাণিক তথ্য থাকলেও তাঁরা খুব কমই প্রমাণ পাওয়ার দাবি করেন, কারণ প্রমাণ বিষয়টি চূড়ান্ত। কোনো কিছু প্রমাণ করার মানে অন্য কোনো ব্যাখ্যার সুযোগ নেই।
হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানের ইতিহাসের অধ্যাপক নাওমি ওরেসকেস ২০২১ সালের জুলাইয়ে সায়েন্টিফিক আমেরিকান ম্যাগাজিনের একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, “বিজ্ঞানের ইতিহাসের সঙ্গে যদি মোটামুটি পরিচিতিও থাকে, তাহলে এমন অনেক উদাহরণ পাবেন যেখানে বিজ্ঞানীরা ভেবেছেন তাঁরা বিষয়গুলো সমাধান করে ফেলেছেন, কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে সেটি পুনর্বিবেচনা করতে হয়েছে। এমন কিছু পরিচিত উদাহরণ হলো: পৃথিবীর অবস্থান মহাবিশ্বের কেন্দ্রে, সময় ও স্থানের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য, মহাদেশের স্থিতিশীলতা এবং সংক্রামক রোগের কারণ।”
ওরেসকেস তাঁর “সায়েন্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি: হোয়াটস প্রুফ গট টু ডু উইথ ইট?” শীর্ষক ২০০৪ সালের গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেছেন যে “প্রমাণ – অন্তত চূড়ান্ত অর্থে – জ্যামিতি ক্লাসে তত্ত্বগতভাবে আদর্শ হলেও বাস্তব জীবনে নয়।”
গণিতজ্ঞেরা সন্দেহাতীতভাবে কোনো কিছু প্রমাণের জন্য নিয়মিতভাবে যুক্তিতে আস্থা রাখেন। সেন্ট লুইসের ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির পরিসংখ্যান ও গণিতের অধ্যাপক স্টিভেন জি ক্রান্টজ খোলাসা করে বলেন, গণিতবিদদের অন্যান্য বিজ্ঞানীদের থেকে যা আলাদা করে তা হলো তাদের গাণিতিক প্রমাণের ব্যবহার, ধাপে ধাপে যুক্তি যা শব্দ, চিহ্ন এবং ডায়াগ্রাম ব্যবহার করে লেখা, যাতে অন্য গণিতবিদকে বোঝানো যায় যে প্রদত্ত বিবৃতিটি সত্য।
দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড কনসেপ্ট অব ম্যাথমেটিক্যাল প্রুফ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখেন, “বিষয়ভিত্তিক কোনো বিবৃতির চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় সত্যতা প্রতিষ্ঠার উপায় হলো প্রমাণ। এ কারণেই আমরা গণিতে আস্থা রাখতে পারি; ২৩০০ বছর আগে ইউক্লিড যা করেছিলেন এখনো সেই গণিতকে আমরা একইভাবে বিশ্বাস করি। জ্ঞানের আর কোনো শাখা এত নিশ্চয়তা দিতে পারে না।”
গবেষণার ফলাফলের উপসংহার বর্ণনার উপায় নিয়ে যদি আপনি এখনও অনিশ্চয়তায় ভুগেন, তবে পড়তে থাকুন। এই চারটি পরামর্শ আপনাকে সঠিক পথ পেতে সাহায্য করবে।
১. কোনো গবেষণা বা গবেষণা গুচ্ছ কিছু “প্রমাণ” করে – প্রতিবেদনে এমন কিছু লেখা থেকে বিরত থাকুন — এমনকি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হলেও তা লিখবেন না।
একাডেমিক গবেষণায় দেখা যায়, সংবাদ বিজ্ঞপ্তিগুলোতে প্রায়ই নতুন গবেষণার ফলাফল নিয়ে বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলা হয়। কেউ কেউ ভুল করে বলে ফেলেন যে গবেষকরা কিছু একটা প্রমাণ করেছেন, যা তাঁরা আসলে করেননি।
কেএসজে সায়েন্স এডিটিং হ্যান্ডবুক সাংবাদিকদেরকে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি সাবধানে পড়ার তাগিদ দিয়েছে। এমআইটির নাইট সায়েন্স জার্নালিজম ফেলোশিপের প্রকল্প এই হ্যান্ডবুকটি বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিভাবান বিজ্ঞান লেখক ও সম্পাদকদের কিছু দিক নির্দেশনা ও অন্তর্দৃষ্টি তুলে ধরে।
এই হ্যান্ডবুকে বলা হয়েছে, “জার্নাল প্রকাশনাগুলোর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিগুলোতে খুব কমই ডেটা থাকে এবং সংজ্ঞা অনুসারে, ফলাফলের গুরুত্ব সম্পর্কে পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে।” তাই সাংবাদিকদের সতর্ক করে বলা হয়, “সেগুলোর সবকিছুই সঠিক বা সম্পূর্ণ – এমন অনুমান কখনও করবেন না।”
টেক্সাস এঅ্যান্ডএম ইউনিভার্সিটির ইন্টিগ্রেটিভ বায়োসায়েন্স, হিউম্যানিটিজ ইন মেডিসিন ও বায়োটেকনোলজির অধ্যাপক বারবারা গ্যাস্টেল বলেন, গণিত ছাড়া অন্য যে কোনো বিষয়ের গবেষকেরা কিছু প্রমাণ করেছেন, এমন দাবি সম্পর্কে সাংবাদিকদের সতর্ক থাকা উচিত।
তিনি বলেন, সাংবাদিকদের নিজেদেরকেই গবেষণার মূল্যায়ন করতে হবে।
টেক্সাস এঅ্যান্ডএম-এর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সাংবাদিকতায় মাস্টার্স ডিগ্রি প্রোগ্রামের পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত গ্যাস্টেল বলেন, “গবেষণাটি আগাগোড়া পড়ুন। কেবল সংবাদ বিজ্ঞপ্তির পেছনে ছুটবেন না। প্রামাণিক তথ্যের শক্তিমত্তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে কেবল সারাংশ পড়বেন না। পুরো প্রবন্ধটি পড়ুন এবং গবেষকদের কিছু প্রশ্ন, মাঝে মাঝে কঠিন প্রশ্ন করার প্রস্তুতি নিন।”
২. এমন ভাষা ব্যবহার করুন যা কোনো গবেষণা বা গবেষণা গুচ্ছের তথ্যপ্রমাণের শক্তিমত্তা যথাযথভাবে তুলে ধরে।
গবেষকেরা আগের গবেষণার ভিত্তিতে কোনো বিষয় বা সমস্যা আরও ভালভাবে বুঝতে অনুসন্ধান চালান। গবেষণাগুলো সাধারণত নতুন তথ্য উন্মোচন করলেও চূড়ান্ত উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য তা যথেষ্ট নয়।
পাবলিক স্কুল, জাদুঘর, ও অন্যান্য সংস্থাগুলোর বিজ্ঞান সংশ্লিষ্টতা নিয়ে গবেষণা কাজে নিয়োজিত অলাভজনক সংস্থা ন্যাশনাল সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশনের ডেপুটি ডিরেক্টর গ্লেন ব্রাঞ্চ বলেন, কোনো গবেষণা বা গবেষণাগুচ্ছ নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির সময় সাংবাদিকদের এমন শব্দ চয়ন করা উচিত যেন তা ফলাফল নিয়ে গবেষকদের আস্থার যথাযথ মাত্রা তুলে ধরে।
যেমন, একটি গবেষণা অমুক তথ্যকে “প্রতিষ্ঠিত করেছে” বা দীর্ঘ এত দিন ধরে ঝুলে থাকা প্রশ্নের “মীমাংসা করেছে,” এমনটি বলবেন না; কারণ গবেষণা কেবল পরীক্ষাধীন কোনো বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে “ধারণা দেয়” বা কিছু দিক সম্পর্কে “সূত্র দেয়।”
সাংবাদিকদেরকে একাডেমিক নিবন্ধে গবেষকদের ব্যবহৃত ভাষায় গভীর মনোযোগ দেয়ার আহ্বান জানান ব্রাঞ্চ। তিনি উল্লেখ করেন, বিজ্ঞানীরা সাধারণত সম্ভাব্যতার মাত্রার ভিত্তিতে একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করেন। তিনি সাংবাদিকদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অনুধাবন, অভিযোজন ও প্রশমনের ক্ষেত্রে সরকারকে সহায়তার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ ও বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার প্রতিষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকারি প্যানেলের দেওয়া বিষয় নির্বিশেষে নিশ্চয়তার ধাপগুলোর মধ্যে যোগসূত্র মেলানোর নির্দেশিকা খুঁটিয়ে দেখতে বলেন৷
ব্রাঞ্চ ইমেইলে জানান, “বৈজ্ঞানিক ফলাফলের আস্থার মাত্রা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবেদন তৈরির সবচেয়ে উন্নত ব্যবস্থা সম্ভবত আইপিসিসি নির্দেশিকা, তাই এটি বা এর মতো কিছু, উত্তম মানদণ্ড হতে পারে।”
গ্যাস্টেল বলেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সাংবাদিকেরা জানেন যে গণিত ছাড়া অন্য বিষয়ের গবেষণায় কিছুই প্রমাণিত হয় না; একত্রে, বেশ কিছু গবেষণা মিলে প্রমাণের কাছাকাছি শক্তিশালী প্রামাণিক তথ্য দিতে পারে।
তিনি বলেন, এটি “বেশ শক্তিশালী প্রামাণিক তথ্য হাজির করতে পারে, যদি বিশেষ করে নির্দিষ্ট বিষয়ে ভালো কয়েকটি গবেষণা হয়ে থাকে।”
যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস বোঝাতে সাংবাদিকেরা “গবেষকরা সবাই নিশ্চিত” এবং “এই অনুসন্ধানে গবেষকদের যথা সম্ভব আস্থা আছে” এমন বাক্য ব্যবহার করতে পারেন।
নিশ্চয়তার মাত্রা বোঝানোর আরেকটি উপায়: বিশেষজ্ঞরা কোনো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে এক মত হয়েছেন কিনা বা বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ব্যাখ্যায় সমন্বিতভাবে এক জায়গায় পৌঁছেছেন কিনা তা খুঁজে বের করুন।
ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস, আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স, আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের মতো স্বাধীন বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলো বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণত বৈজ্ঞানিক ঐকমত্য বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের সমবেত প্যানেলের সমন্বিত মতামত জানাতে যৌথ বিবৃতি দিয়ে থাকে।
৩. একটি একক গবেষণা নিয়ে প্রতিবেদন করার সময়, প্রদত্ত বিষয়ে বিদ্যমান জ্ঞানে এটি কী অবদান রাখছে এবং প্রমাণগুলো, সামগ্রিকভাবে, একটি নির্দিষ্ট দিকে ঝুঁকেছে কিনা তা ব্যাখ্যা করুন।
অনেকেই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে অপরিচিত, তাই একটি গবেষণা কীভাবে একটি ইস্যু বা সমস্যা নিয়ে বিদ্যমান জ্ঞানসম্ভারের বৃহত্তর পরিসরে জায়গা করে নেয়, তা বুঝতে সাংবাদিকদের সহায়তা প্রয়োজন। গবেষকেরা যদি সমস্ত প্রামাণিক তথ্য একসঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে জোর দিয়ে নিশ্চয়তার সঙ্গে ঐ ইস্যু বা সমস্যা সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন, তবেই পাঠকশ্রোতাদের জানান।
গ্যাস্টেল উল্লেখ করেন, বাস্তবতার সঙ্গে গবেষণার যোগসূত্র মেলানোর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সাংবাদিকদের জন্য একটি দুর্দান্ত রিসোর্স হলো: একাডেমিক জার্নালে প্রকাশিত সম্পাদকীয়। নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন ও আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জার্নাল জেএএমএ সহ কয়েকটি জার্নাল অনেক সময় কোনো নতুন গবেষণাপত্রসহ অন্যান্য প্রবন্ধ নিয়ে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।
নির্দিষ্ট বিষয়ে এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ – যারা গবেষণার সঙ্গে সরাসরি জড়িত নন – সাধারণত সম্পাদকীয় লিখে থাকেন। তাই কোনো গবেষণাপত্রের গুরুত্ব ও ভূমিকা বুঝতে এই সম্পাদকীয় সাংবাদিকদের সহায়ক হতে পারে।
“আমি দেখেছি, এটি সত্যিই কাজের,” গ্যাস্টেল যোগ করেন।
৪. প্রকাশিত হওয়ার আগে শিরোনামগুলো নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করুন। আর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণার শিরোনামে ভুল এড়াতে আমাদের টিপ শিট পড়ুন।
সম্পাদকেরা, বিশেষ করে যাঁরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁরা গবেষণা সম্পর্কে শিরোনাম লেখা বা পরিবর্তনে সহজেই ভুল করতে পারেন। আর একটি বাজে শিরোনামের কারণে নিখুঁতভাবে গবেষণা নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া একজন প্রতিবেদকের সর্বোচ্চ চেষ্টাও ভেস্তে যেতে পারে।
ত্রুটি এড়াতে গ্যাস্টেল সাংবাদিকদেরকে তাঁদের স্টোরি সহ প্রস্তাবিত শিরোনাম জমা দেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি তাঁদের স্টোরির শিরোনামটি প্রকাশিত হওয়ার আগেই আরেকবার দেখার তাগিদ দেন।
আরেকটি ভলো আইডিয়া: কপি এডিটর সহ সম্পাদকেরা গবেষণা, বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিষয়ে সংবাদ শিরোনামের ব্যাপারে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন। একসঙ্গে তাঁরা সবচেয়ে যথাযথ ভাষা বেছে নিতে পারেন এবং “প্রমাণ” শব্দটি ব্যবহার করা হবে কিনা, সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
গ্যাস্টেল ও ব্রাঞ্চ একমত যে বিশেষ করে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে সম্পাদকেরা বিজ্ঞান বিষয়ক সাংবাদিকতার প্রশিক্ষণ থেকে উপকৃত হতে পারেন। নির্দিষ্ট ওষুধ ও চিকিৎসার কার্যকরিতা নিয়ে বিভ্রান্তিকর দাবি করা শিরোনাম বা ক্যান্সার, ডিমেনশিয়া ও সিজোফ্রেনিয়ার মত স্বাস্থ্যগত অবস্থার কারণ বা প্রতিরোধ নিয়ে গবেষকদের “প্রমাণ” দাবি করে শিরোনামগুলো জনসাধারণের ক্ষতির কারণ হতে পারে।
শিরোনাম লেখা নিয়ে আমাদের টিপ শিটে এই সমস্যাসহ অন্যান্য বিষয়ের সমাধান পাওয়া যাবে।
“‘প্রমাণ’ একটি ছোট, চটকদার শব্দ, তাই এটি শিরোনামে মানিয়ে যায় – তবে এটি সাধারণত ভুল,” ব্রাঞ্চ বলেন৷ “সাংবাদিকদের মত শিরোনাম লেখকদেরও এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।”
এই নিবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয় দ্য জার্নালিস্টস্ রিসোর্সের ওয়েবসাইটে। ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সের আওতায় এখানে পুনঃপ্রকাশ করা হলো।
আরও পড়ুন
বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উত্থান
রিপোর্টিংয়ে গাণিতিক ভুল এড়াতে ৪ পরামর্শ
মিট দ্য ওয়াচডগ সায়েন্টিস্টস ব্যাটলিং ডুবিয়াস সায়েন্টিফিক রিসার্চ
 ডেনিস-মেরি অর্ডওয়ে ২০১৫ সালে দ্য জার্নালিস্টস রিসোর্সে যোগদান করেন। এর আগে তিনি অরল্যান্ডো সেন্টিনেল ও ফিলাডেলফিয়া ইনকোয়ারার সহ যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্য আমেরিকার একাধিক সংবাদপত্র ও রেডিও স্টেশনে রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেছেন। ইউএসএ টুডে, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং ওয়াশিংটন পোস্টের মত পত্রিকাতেও তাঁর কাজ প্রকাশিত হয়েছে।
ডেনিস-মেরি অর্ডওয়ে ২০১৫ সালে দ্য জার্নালিস্টস রিসোর্সে যোগদান করেন। এর আগে তিনি অরল্যান্ডো সেন্টিনেল ও ফিলাডেলফিয়া ইনকোয়ারার সহ যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্য আমেরিকার একাধিক সংবাদপত্র ও রেডিও স্টেশনে রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেছেন। ইউএসএ টুডে, দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং ওয়াশিংটন পোস্টের মত পত্রিকাতেও তাঁর কাজ প্রকাশিত হয়েছে।