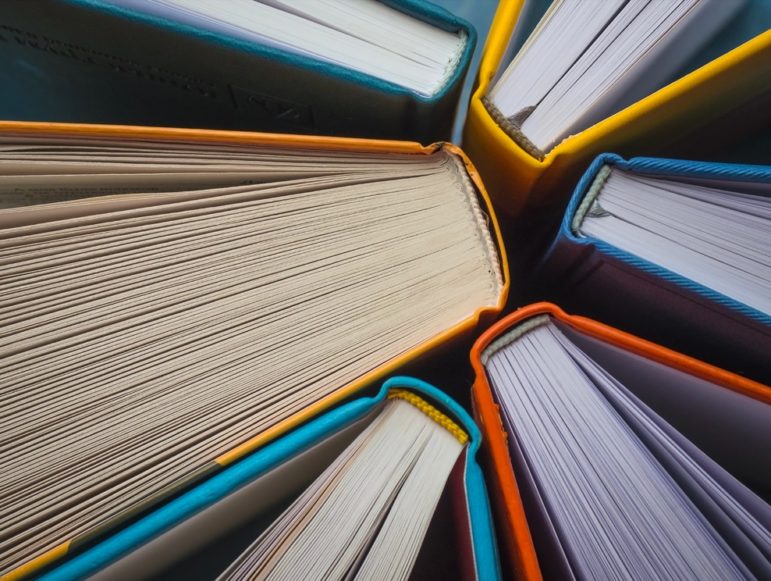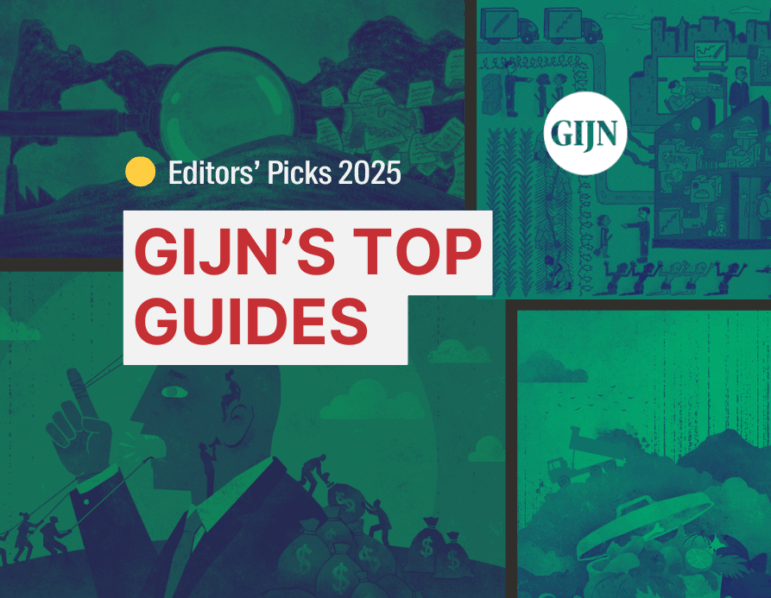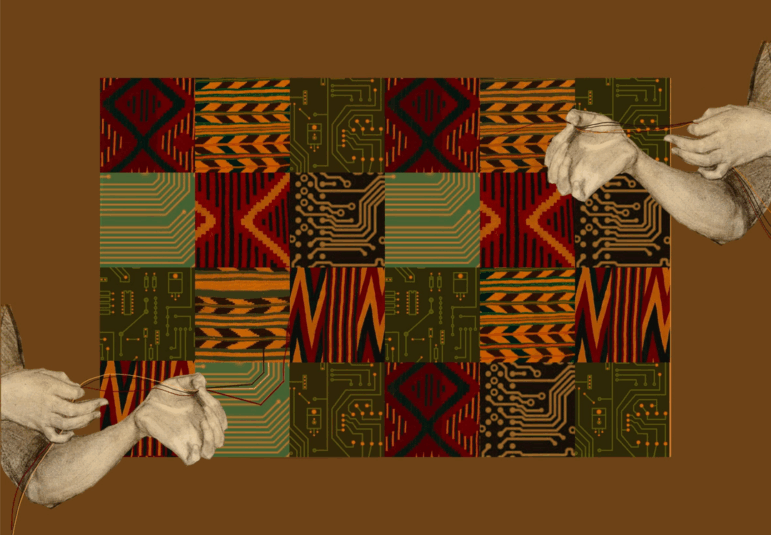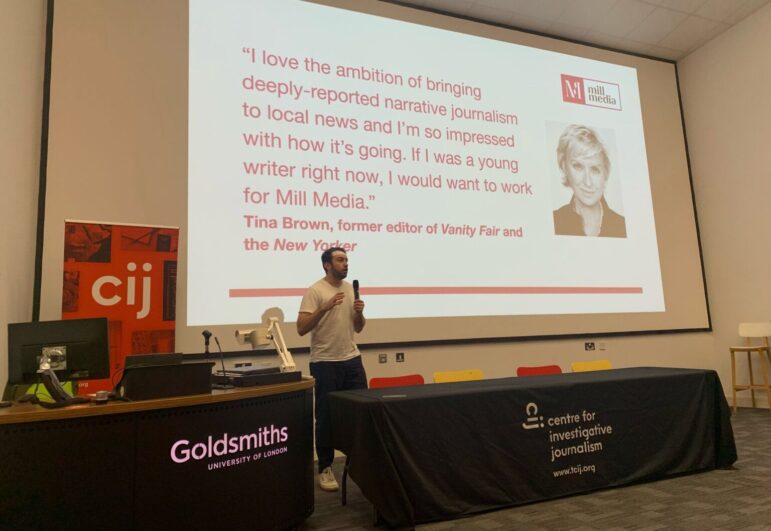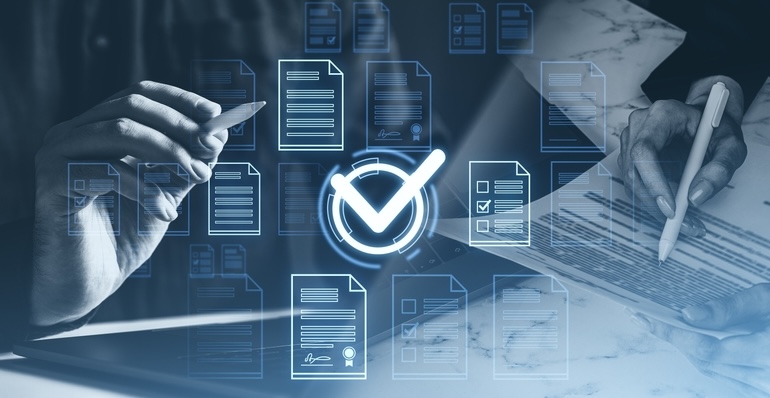
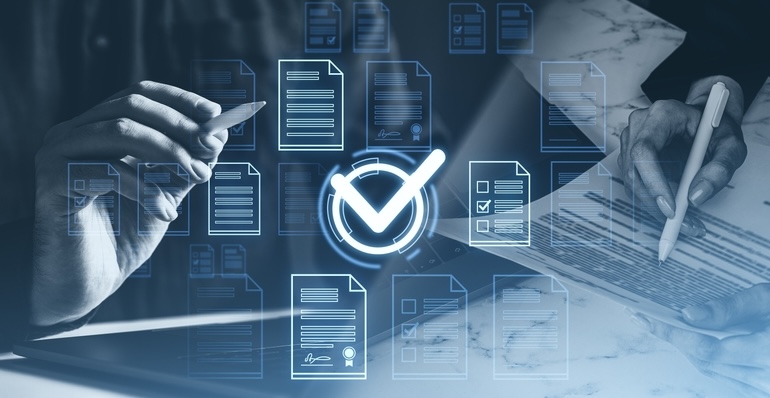
Hands with stylus reviewing documents, digital checkmarks overlay. Blue-toned style, business evaluation concept, approval process
ব্রাজিলের ফ্যাক্ট-চেক প্রকল্পের নতুন উদ্যোগ: ভুল তথ্য শনাক্তে লেবেল নয়, গুরুত্ব পাবে উৎস ও কৌশল
ব্রাজিলে যৌথভাবে পরিচালিত ফ্যাক্ট-চেক উদ্যোগ কমপ্রোভা। এটি এখন আর “মিথ্যা,” “বিভ্রান্তিকর,” “ব্যঙ্গাত্মক” বা “প্রমাণিত”—এই ধরনের শব্দ বা লেবেলগুলো ব্যবহার করছে না। বরং ভুয়া তথ্য মোকাবিলায় তারা আরও কার্যকর ও বড় পরিসরে কাজ করছে।
হোসে আন্তোনিও লিমা কাজ করেন প্রকল্পটির সহকারী সম্পাদক হিসেবে। তার মতে, আগের পদ্ধতিতে শুধু কনটেন্ট বা বিষয়বস্তুর ওপর জোর দেওয়া হতো, উপেক্ষিত থাকত ভুয়া তথ্যের অন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো—যেমন এটি কোথা থেকে এসেছে এবং কেন এত মানুষের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।
লাটাম জার্নালিজম রিভিউ (এলজেআর)-কে এই সাংবাদিক বলেন, “আমরা বুঝতে পেরেছি, শুধু অভিযোগ খণ্ডনই যথেষ্ট নয়। ফ্যাক্ট-চেকের মাধ্যমে এখন আর কেবল ভাইরাল পোস্টের প্রমাণ ও দাবিগুলো যাচাই করা হয় না। বরং ওই কনটেন্টের নির্মাতা ও তাদের স্বার্থ, সেই সঙ্গে মানুষকে বিশ্বাস করানো এবং প্ররোচিত করার কৌশলগুলোও পরীক্ষা করা হয়। মূল বিষয়টি হলো কনটেন্টকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যেন তা জনসাধারণের আলোচনার জন্য সহায়ক হয় এবং রাজনৈতিক বা আদর্শগত মতানৈক্য নির্বিশেষে মানুষ সত্য তথ্যের ওপর নির্ভর করে নিজের মত তৈরি করতে পারে।”
পাশাপাশি লিমা বলেন যে, তারা আশা করেন “লেবেল করা শব্দ” ব্যবহার বন্ধ করার মাধ্যমে তারা ওই সব লোকেদের সঠিক ও সত্য তথ্যের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবেন যারা ভুয়া তথ্য দিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়।
লিমা এলজেআরকে আরো বলেন,“এই ধরনের লেবেলগুলো শেষ পর্যন্ত যাচাইপ্রক্রিয়া এবং জনগণের মধ্যে সংযোগের জন্য প্রতিবন্ধকতা বা বাধার মতো কাজ করত। যখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে মানুষ এমন কনটেন্টের প্রতি বিরক্ত, যা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত। ঠিক তখনই আমরা তার ব্যবহার বন্ধ করেছি।”
চার মাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শেষমেশ এই পরিবর্তনগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। উদ্যোগটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতিগত সংস্কারেরই প্রতিফলন। প্রজেক্ট কমপ্রোভার শুরুটা ২০১৮ সালে। বর্তমানে ব্রাজিলের বিভিন্ন অঞ্চলের ৪২টি মিডিয়া আউটলেটকে একত্রিত করে যৌথভাবে কাজ করছে।
কমপ্রোভার রয়েছে নিজস্ব একটি সম্পাদকীয় দল। যারা সন্দেহজনক কনটেন্ট সংগ্রহ করে তাদের ফ্যাক্ট-চেকারদের কাছে পাঠায়। মিডিয়া পার্টনার হিসেবে যে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে তাদের সাংবাদিকরা স্বেচ্ছায় সেই কনটেন্ট যাচাই করেন। সাধারণত কমপ্রোভার ভিন্ন ভিন্ন তিনটি সদস্য আউটলেটের সাংবাদিকদের দিয়ে তা যাচাই করা হয়। যাচাই বাছাই শেষ হওয়ার পর সাংবাদিকরা একটি রিপোর্ট লিখেন। রিপোর্টটি অন্যান্য সহকর্মীদের মূল্যায়নের (পিয়ার রিভিউ) জন্য পাঠানো হয় এবং কেবল তখনই প্রকাশ করা হয়, যখন অন্তত আরও তিনটি বার্তাকক্ষ তথ্য যাচাইয়ের ওই প্রক্রিয়া আর প্রাপ্ত ফলাফলকে অনুমোদন করে। চূড়ান্ত প্রবন্ধটি কমপ্রোভার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়, যেখানে গোটা প্রক্রিয়াতে (তথ্য অনুসন্ধান এবং পরবর্তী যাচাই) অংশ নেওয়া বার্তাকক্ষগুলো নাম লেখা থাকে। অংশগ্রহণকারী বার্তাকক্ষগুলো চাইলে তাদের প্রতিবেদনে তা উল্লেখ করতে পারে।
শিরোনাম নতুনভাবে ভাবা
কোনো ধরনের লেবেল ব্যবহার না করার পাশাপাশি ফ্যাক্ট-চেক করা শিরোনামগুলোর ক্ষেত্রে নতুন করে ভাবতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রস্তাব করা হয়েছে, সব শিরোনাম “সত্যের পক্ষে” হওয়া উচিত এবং পুনরায় মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর বিষয়টি এড়িয়ে চলা উচিত, এমনকি ব্যাখা করার ক্ষেত্রেও।
লিমা বলেন, “বর্তমান পরিস্থিতিতে, উন্মুক্ত কোনো বিতর্কে কোনো ধরনের ভুল তথ্য ব্যবহার করা হচ্ছে না—এমনটা কল্পনা করাটাই বেশ কঠিন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এখনকার উন্মুক্ত আলোচনা বা বির্তকে ভুয়া তথ্যের বিষয়টি মারাত্নক দোষের হিসেবে দেখা হয় না। কেননা এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যা দূর করাটা কঠিন।” তিনি আরও বলেন, “তাইতো বাস্তবে আমরা ভুল তথ্যের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি কমাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—শিরোনামের বিষয়টি এর সঙ্গে সম্পর্কিত।”
কমপ্রোভার দলে কাজ করেন সাংবাদিক গ্যাব্রিয়েলা ব্রাজ। যুক্ত রয়েছেন কোহেও ব্রাজিলিয়েন্সে পত্রিকার সঙ্গে। তিনি বলেছেন, নতুন নিয়মের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো শিরোনাম এবং লেখা তৈরির ভাবনা ও পদ্ধতিকে এমনভাবে তুলে ধরা, যাতে পাঠকই যেন ধরতে পারে যে এটি ভুল তথ্য, কিন্তু তথ্যটি মিথ্যা— সরাসরি এমনটা উল্লেখ করা হয় না।
এলজেআরকে ব্রাজ বলেন। “আগে যেমন লেখাতে উল্লেখ করা হতো যে: ‘এটা এটা ঘটেছে—যা সম্পূর্ণ মিথ্যা।’ এখন আর সেভাবে লেখা হয় না। আমাদের অনেক বেশি পরোক্ষ শিরোনামের কথা ভাবতে হয়, কারণ আমরা বুঝি যে এই [মিথ্যা] লেবেলই সেই পাঠককে দূরে ঠেলে দিতে পারে, যারা এই মিথ্যা তথ্যের শিকার হয়েছেন। ‘মিথ্যা,’ ‘বিভ্রান্তিকর,’ বা ‘না’ এই শব্দগুলো ব্যবহার না করেও সত্য তুলে ধরার মনোভাব লেখার সময় আমাদের চিন্তাকেও পরিবর্তিত করে।”
লেখা ছাড়াও নতুন পদ্ধতিটি গোটা ফ্যাক্ট-চেক প্রক্রিয়া নিয়ে গভীর চিন্তার সুযোগ করে দেয়। যেমন, একটা ভুল তথ্যের মধ্যে যে সব উপাদান থাকে তা খুঁজে বের করা—কারা কনটেন্ট তৈরি করছে এবং এটি বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য কী কৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে—যেসব পেজ ফ্যাক্ট-চেক করা কনটেন্ট তৈরি করে, সেই পেজগুলো বিশ্লেষণ করা হয়। এছাড়া এই প্রোফাইলগুলো যে ভাষা ব্যবহার করে, শিরোনাম এবং ক্যাপশন তৈরির ধরন, এবং অন্যান্য শেয়ার করা পোস্টের বিষয়বস্তুও পরীক্ষা করা হয়। এই সবকিছু বিশ্লেষণ করে তা ফ্যাক্ট-চেকে ব্যবহার করা যায়।
ব্রাজ বলেন, “কারণ ভুল তথ্য ছড়ানোর ধারা এখন আরও জটিল হয়ে উঠেছে, তাই আমাদেরকেও বিষয়টি নিয়ে আরও গভীরভাবে ভাবতে হচ্ছে।” তিনি আরও বলেন, “এই প্রক্রিয়ায় আমরা কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখেছি, যেমন সতর্কবার্তা দেওয়া, ‘জরুরি’ শব্দ ব্যবহার করা, কিংবা আতঙ্ক সৃষ্টি করে এমন কনটেন্ট তৈরি করা। এসব প্রোফাইলে আমরা যে ধরনের বৈশিষ্ট্য আর নতুন কৌশলের সঙ্গে কনটেন্ট প্রকাশ করতে দেখি, তা মানুষের জন্য সতর্ক সংকেত হিসেবে কাজ করতে পারে—যাতে তারা ভুল তথ্য চিনতে শেখে।”
ভুয়া তথ্যের বিরুদ্ধে আরও সংলাপ
ব্রাজ বলেন, তিনি এখন এমন মানুষদের প্রতি আরও সহানুভূতিশীল, যারা এই কনটেন্টগুলো দেখে তা বিশ্বাস করে, এবং তাদের যুক্তিগুলো বোঝার চেষ্টা করে। তিনি বলেন, এখন তিনি যে কনটেন্ট তৈরি করেন তা অনেক বেশি শিক্ষামূলক।
তিনি আরও বলেন, “আমরা ফ্যাক্ট-চেকার বলে কিন্তু মাঝে মাঝে এমনটা ভাবি না যে, ‘ওহ, যদি আমি নিয়মিত তথ্যের সত্যতা যাচাই না করতাম, তাহলে এগুলো চোখে পড়তো না।’ এ সম্পর্কে সের্জিও [লুডটকে, সম্পাদক] এবং জে [লিমা, সহকারী সম্পাদক] বলেন, কখনও কখনও ভুলগুলো চোখে না পরার কারণে মানুষ নিজেই লজ্জিত বোধ করেন। তাই আমরা সরাসরি বলব না যে এটা মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর। বরং ব্যাখ্যা দিয়ে বলা উচিত কেন তারা ভুলটা বুঝতে পারিনি, আর এখন কীভাবে সতর্ক হতে পারে।”
গবেষক তাইস সেইব্ট ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয় অব রিও গ্র্যান্ডে দো সুল থেকে তথ্য ও যোগাযোগের ওপর পিএইচডি করেছেন। তিনি আরো বলেন যে, এই ধরনের লেবেল সরিয়ে দেওয়াটাও সমাধানের পথ হতে পারে এবং জনগণকে ভুল তথ্যের ওপর নির্ভরতা কমাতে সাহায্য করতে পারে। এই সাংবাদিক দশ বছর ধরে ব্রাজিলে ফ্যাক্ট-চেকিং নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি বলেন, ফ্যাক্ট-চেকিং শুধু তথ্যভিত্তিক সাংবাদিকতার একটি ধরন নয়, গণমাধ্যম সাক্ষরতারও অংশ, যা ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার হতে পারে।
এলজেআরকে সেইব্ট বলেন, “লেবেল বাদ দেওয়া এক ধরনের উপায় হতে পারে। এটা ফ্যাক্ট-চেকিংয়ের ভবিষ্যৎ কিনা আমি জানি না, তবে মানুষের বিরোধিতা কমাতে সাহায্য করতে পারে। কারণ, যখন আপনাকে বলা হয় যে, আপনার শেয়ার করা তথ্যটি ভুল, তখন আপনি নিজেকে ছোট মনে করতে পারেন এবং প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন। এক্ষেত্রে অনেক সময় রেগে গিয়ে সংশোধিত ওই তথ্য বা সংশোধনকারীকে আক্রমণও করা হয়। এখানে আবেগ কাজ করে— যেমন কিছু বিশ্বাস আঁকড়ে থাকার পেছনেও আবেগ থাকে।”
সেইব্ট আরো বলেন, এখনকার ভুল তথ্যের পরিবেশে বোঝা যাচ্ছে যে একা একা করা ফ্যাক্ট-চেক তেমন কাজ করে না। কারণ, ভুয়া তথ্য অনেক মানুষের মনে এরমধ্যেই গল্প বা বিশ্বাস হিসেবে গেঁথে গেছে। তাই দশ বছর আগে যে ধরণের ফ্যাক্ট-চেকিং শুরু হয়েছিল, তা দিয়ে এই মানসিকতা ভাঙা এখন অনেক কঠিন।
ব্রাজিলের এই তথ্য গবেষক উল্লেখ করেন, কোনো একটি তথ্যকে ‘ভুল’ বলে চিহ্নিত করেও খুব বেশি লাভ হয় না। কারণ আরও অনেক তথ্য একই ক্ষতি করবে, যেগুলো আলাদা করে কেউ যাচাই করে না। তাই এখন প্রিবাঙ্কিং বা আগেভাগেই মানুষকে প্রস্তুত করার পদ্ধতি গুরুত্ব পাচ্ছে, যেটা এক ধরনের ‘টিকা’র মতো কাজ করে। এতে কোনো নির্দিষ্ট কনটেন্টকে টার্গেট না করেই ভুয়া তথ্য আসার আগে থেকেই শ্রোতাদের সতর্ক করা যায়। এটি মিডিয়া জ্ঞান ((মিডিয়া লিটারেসি) এবং ফ্যাক্ট-চেকিংয়ের শিক্ষামূলক ভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কিত—আমি বলতে চাই, সাংবাদিকতার সবক্ষেত্রেই।”
এই প্রসঙ্গে প্রকল্পটির সহকারী সম্পাদক লিমা বলেন, কমপ্রোভা এখন শুধু ভুয়া তথ্য যাচাই করছে না, বরং ভুয়া তথ্য ছড়ানোর আগেই তা ধরতে পারার সক্ষমতাও বাড়াতে চাইছে। এর অংশ হিসেবে তারা মানুষকে শেখাচ্ছে কীভাবে এআই-তৈরি কনটেন্ট চিনতে হয়। পাশাপাশি, এই ফ্যাক্ট-চেকিং প্রকল্পটি এপ্রিল থেকে অনলাইন প্রতারণাও যাচাই করা শুরু করেছে।
লিমা আরও বলেন, “আমরা চাই মানুষ যেন বুঝতে পারে ভুয়া তথ্য ছড়াতে কী ধরনের কৌশল ব্যবহার করা হয় এবং অ্যালগরিদম কীভাবে কাজ করে। আমাদের লক্ষ্য হলো আরও উপযুক্ত তথ্য পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখা । যা শুধুমাত্র কমপ্রোভার মতো উদ্যোগের ওপর নির্ভর করে না, বরং এতে সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত, সমাজ ও প্রতিটি নাগরিক ভূমিকা রাখবে। ”
সম্পাদকের নোট: মূল প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল লাটাম জার্নালিজম রিভিউ-তে। অনুমতি নিয়ে এখানে পুনঃপ্রকাশ করা হলো। লেখাটির স্প্যানিশ ও পর্তুগিজ ভাষান্তর করেছেন তেরেসা মিওলি।
 মার্তা শপাসেনকফ একজন সাংবাদিক। তিনি ব্রাজিলের রিও দে জেনেরিওতে থাকেন। জর্নাল এক্সট্রা, ও গ্লোবো, দি ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস অ্যাট অস্টিন, ইয়াহু ব্রাজিল এবং লাটাম জার্নালিজম রিভিউ-তে তার লেখা প্রকাশ হয়েছে।
মার্তা শপাসেনকফ একজন সাংবাদিক। তিনি ব্রাজিলের রিও দে জেনেরিওতে থাকেন। জর্নাল এক্সট্রা, ও গ্লোবো, দি ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস অ্যাট অস্টিন, ইয়াহু ব্রাজিল এবং লাটাম জার্নালিজম রিভিউ-তে তার লেখা প্রকাশ হয়েছে।