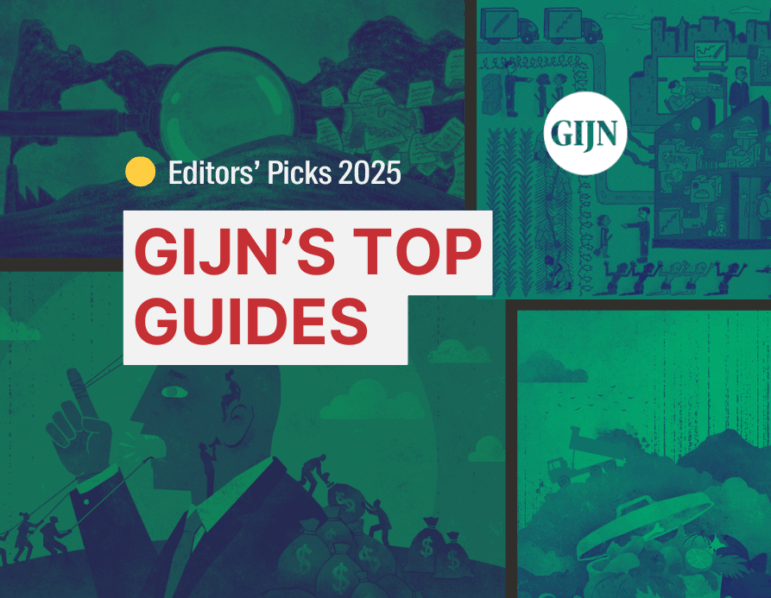সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম অনুসন্ধান গাইড
আর্টিকেলটি পড়ুন এই ভাষায়:
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অ্যালগরিদমের প্রভাব বহুমুখী ও গভীর। (সোশ্যাল মিডিয়া অ্যালগরিদম হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় নিয়ম বা গাণিতিক সূত্র, যা ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার (এক্স), ইনস্টাগ্রামসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারকারীর সামনে কোন কনটেন্ট আগে, কোনটা পরে পাঠক-দর্শকের সামনে আনা হবে বা একেবারেই দেখানো হবে না—তা ঠিক করে।) অ্যালগরিদম-নিয়ন্ত্রিত নিউজফিডের কারণে একদিকে বিশ্বজুড়ে রাষ্ট্র ও সরকারগুলোর স্থিতিশীলতা ঘিরে হুমকি তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। আমাদের সম্পর্কগুলো ভেঙে দিচ্ছে। নিচে এ সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দেওয়া হলো:
- শ্যাডো-ব্যানড কনটেন্ট ফ্রম প্রো-প্যালেস্টিনিয়ান অ্যাকাউন্টস।
- মিস-অ্যান্ড ডিসইনফরমেশন ক্যাম্পেইনস মেন্ট টু স্টার পলিটিক্যাল আনরেস্ট ইন ঘানা।
- আ মাদার আনফলোইং হার ডটার অন সোশ্যাল মিডিয়া বিকজ দেয়ার পলিটিক্যাল ডিফারেন্সেস আর অ্যাম্প্লিফায়েড অনলাইন।
সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম নিয়ে কাজের ধরন হতে পারে বিভিন্ন রকম। কিছু অনুসন্ধানী কাজ শেষ করতে কয়েক সপ্তাহ লাগতে পারে। যেখানে ডিজিটাল ফরেনসিকস ও কোডিং দক্ষতার প্রয়োজন হতে পারে। তবে খুব সামান্য বা কোনো প্রযুক্তিগত জ্ঞান ছাড়াই অনেক অনুসন্ধান করা সম্ভব। যেমন, বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে কনটেন্টের গতিপথ অনুসরণ করে দেখা। অথবা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ছোট ছোট পরীক্ষার মাধ্যমে সবার সামনে তুলে ধরা যে, কীভাবে ক্ষতি করে এসব অ্যালগরিদম।
তাই আপনি যে পদ্ধতিই ব্যবহার করেন না কেন, সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম নিয়ে জবাবদিহিমূলক প্রতিবেদন তৈরিতে কিছু না কিছু সৃজনশীলতা যোগ করতেই হবে। এর মূল কারণ মেটা বা টিকটকের মতো ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানিগুলোর অ্যালগরিদম কীভাবে তৈরি করা হয়েছে বা এগুলো কীভাবে কাজ করে—তারা তা প্রকাশ করতে বাধ্য নয়। কখনও কখনও তথ্য ফাঁস হওয়ার পর যা প্রকাশ্যে আসে। কিন্তু অ্যালগরিদম কীভাবে কাজ করতে পারে—অধিকাংশ সময় সাংবাদিকদের তা উল্টোদিক থেকে বিশ্লেষণ করতে হয়। অথবা প্রমাণ করে দেখাতে হয় যে, এই সাইটগুলো বিদ্বেষ বা বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট ছড়িয়ে ক্ষতি করছে।
অ্যালগরিদম কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে?
অ্যালগরিদম হলো কাজ সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত নিয়ম বা গণনার একটি সেট। সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে, অ্যালগরিদম ব্যবহারকারীর তথ্য মূল্যায়ন করে। যেমন, আপনি কোন কনটেন্ট পছন্দ করেছেন, ওই প্ল্যাটফর্মে আপনার সঙ্গে কার সংযোগ রয়েছে বা কোন ধরনের পোস্টে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন—এগুলো বিশ্লেষণ করে আপনার নিউজফিড, টাইমলাইন বা স্ট্রিমে আপনি কী দেখতে পারেন এবং কোন কনটেন্টে বেশি আগ্রহী হতে পারেন অ্যালগরিদম তা বিশ্লেষণ করে ঠিক ওই ধরনের কনটেন্ট আপনার সামনে হাজির করে।
এই অ্যালগরিদমগুলো তাদের কর্পোরেট মালিক কর্তৃক নিয়মিত পরিবর্তিত হয় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি আধুনিক হয়ে উঠছে। যেমন ২০২১ সালে ওয়াশিংটন পোস্টের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ফেসবুকের অ্যালগরিদম প্রায় ১০ হাজার সংকেত বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুমান করে একজন ব্যবহারকারী কোন ধরনের পোস্টে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন।
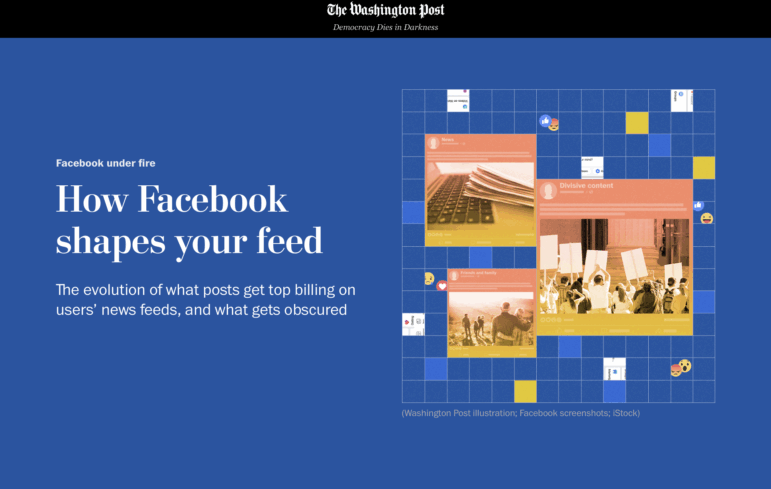
২০২১ সালে ওয়াশিংটন পোস্ট ফেসবুকের পরিবর্তনশীল অ্যালগরিদম এবং এটি ব্যবহারকারীদের ফিডে কীভাবে প্রভাব ফেলে তা নিয়ে গভীর অনুসন্ধান চালায়। ছবি: স্ক্রিনশট, দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট
সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম কেবল জটিলই নয়, বরং যে কোম্পানিগুলো তা তৈরি করেছে তারা এর বিশ্লেষণ পদ্ধতিও প্রকাশ করে না। তাই প্ল্যাটফর্মগুলোর দায়বদ্ধতা নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির সময় সাংবাদিকদের প্রধানত অ্যালগরিদমের ক্ষতিকর প্রভাবের ওপর মনোযোগ দিতে হবে। যেখানে থাকতে পারে কোন ধরনের কনটেন্ট ভাইরাল হয় তা খুঁজে দেখা, নির্দিষ্ট দুর্বল জনগোষ্ঠীর কাছে কী ধরনের ভিডিও পৌঁছায় তা বোঝার চেষ্টা, অ্যালগরিদম কীভাবে কাজ করে তা পরীক্ষা করার জন্য নকল বা ডামি অ্যাকাউন্ট তৈরি করা, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে আক্রমণাত্মক পোস্ট দিয়ে উসকে দেওয়া বা মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর মাত্রা কতটা ব্যাপক তা খতিয়ে দেখা।
সোশ্যাল ওয়েব নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির সময় তথ্য কিভাবে ছড়ায় তা বোঝাও জরুরি। এটা নিয়ে অনুসন্ধানী কাজে যখন নামবেন, তখন কিছু সাধারণ শব্দ ও ধারণা সম্পর্কে বোঝাপড়া তৈরি করা ভালো। কারণ আমরা অনলাইনে যে বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করি তা সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ।
অপতথ্য, ভুল তথ্য আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক ভাষা: কী ও কীভাবে ছড়ায়?
অনলাইন তথ্যের প্রবাহ নিয়ে কাজ করেন—এমন সাংবাদিকদের জন্য বিভিন্ন রিসোর্স রয়েছে, যেমন ইউ ডিসইনফোল্যাব নামের একটি অলাভজনক গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে মিসইনফরমেশন গ্লসারি। তবে সাধারণ আলোচনায় তিনটি শব্দ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়: অপতথ্য, ভুয়া তথ্য এবং অনলাইনে ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক ভাষা।
ঠিক যেমন, সাংবাদিকদের বুঝতে পারা জরুরি যে মিডিয়া ইকোসিস্টেমে এই ধরনের তথ্য ছড়ানোর মূল কারিগর কারা।
ভুল তথ্য (মিসইনফরমেশন): এই শব্দটি অনেক সময় অনলাইনের নানা ধরনের সমস্যাকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আসলে এর অর্থ অনেক সীমিত—মিসইনফরমেশন হলো ভুল তথ্য। লোকেদের অজ্ঞতা বা অসতর্কতার কারণে এমন ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ যে বা যারা শেয়ার করছে বা ছড়াচ্ছে তারা তথ্যটিকে সত্যি মনে করেই ছড়াচ্ছে। যেমন, বড় কোনো ঘটনা ঘটলে অনেকেই ভুলবশত অন্য সময় বা অন্য ঘটনার ছবি শেয়ার করেন। ভেবে নেন, এটি বুঝি বর্তমান ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত।
অপতথ্য ( ডিসইনফরমেশন) হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি বা ছড়ানো মিথ্যা তথ্য, যা বিভ্রান্তি সৃষ্টি বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ছড়ানো হয়। যেমন, ২০১৬ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়, মার্কিন সিনেট ও হাউস ইন্টেলিজেন্স কমিটির যৌথ অনুসন্ধানে এবং ফেসবুকের সহযোগিতায় জানা যায়, রুশ এজেন্টরা মার্কিন ভোটার হিসেবে ছদ্মবেশ ধারণ করে মিথ্যা প্রতিবাদের খবর ছড়িয়ে রাজনৈতিক বিভাজন সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। যদিও রাশিয়া এ ধরনের কোনো নির্বাচনী হস্তক্ষেপ অস্বীকার করেছে।
হেট স্পিচ বা বিদ্বেষমূলক বক্তব্য হলো আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিকর তথ্যের ধরন যা অনলাইনের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়ায়। এতে কোনো জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ বা যৌন পরিচয়সহ নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণা বা সহিংসতা উসকে দেওয়া হয়। যেমন মিয়ানমারের কিছু রাজনৈতিক নেতা ফেসবুকে রোহিঙ্গা মুসলিম সংখ্যালঘুদের অপমান ও অমানবিকভাবে উপস্থাপন করেছিলেন, যার ফলে তাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনের পর ফেসবুক মিয়ানমারে ২০টি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিকে নিষিদ্ধ করে “ঘৃণা ও মিথ্যা তথ্যের প্রসার রোধ” করার উদ্দেশ্যে। তবে দেশটির সামরিক কর্মকর্তারা ওই প্রতিবেদনের বিষয়গুলো অস্বীকার করেছে।
ঠিক যেমন, সাংবাদিকদের বুঝতে পারাটা জরুরি যে মিডিয়া ইকোসিস্টেমে এই ধরনের তথ্য ছড়ানোর মূল কারিগর কারা। অ্যালগরিদম প্রত্যেকের জন্য ব্যক্তিগত অনলাইন আবহ তৈরি করে। যার মানে আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজস্ব তথ্যজগতে বসবাস করি, যাকে সাধারণত “ইকো চেম্বার” বা “ফিল্টার বাবল” বলা হয়।
এই ইকোসিস্টেমে প্রথমত আছেন সাধারণ দর্শক বা ব্যবহারকারীরা, যারা বেশিরভাগ সময় নিষ্ক্রিয় থাকেন। তারা মাঝে মাঝে কনটেন্ট শেয়ার করতে পারেন, কিন্তু বেশি পরিমাণ কনটেন্ট তৈরি করেন না। এরপর আছেন সক্রিয় কনটেন্ট নির্মাতা—যারা অনেক তথ্য দেন। এরা সাধারণত দর্শকদের প্রভাবিত করে যে তারা কোন ধরনের তথ্যের ওপর নির্ভর করবেন। এর মধ্যে থাকতে পারে সরকারী সংস্থা, সংবাদসংস্থা, ইনফ্লুয়েন্সার। পাশাপাশি খারাপ উদ্দেশ্যে কিছু ব্যক্তি, যারা তাদের অসৎ উদ্দেশ্যে হাসিল করতে চায়। আর সবশেষে আছে অ্যালগরিদম। যা ডেটা-ভিত্তিক নিয়মের সেট। এটি নির্ধারণ করে কোন কনটেন্ট-ব্যবহারকারীর টাইমলাইনে দেখা যাবে। অ্যালগরিদম এই মিডিয়া ইকোসিস্টেমকে আকার দিতে সাহায্য করে।
সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম অনুসন্ধানের তিনটি পদ্ধতি
কয়েক বছর আগে সাংবাদিক জেন লিটভিনেঙ্কো এবং আমি এই বিষয়গুলো অনুসন্ধানের জন্য একটি রূপরেখা তৈরি করেছিলাম। মূল কথা হলো, মিডিয়া পরিবেশ গঠনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের মধ্যে একটির উপর নির্ভর করে গল্পগুলো অনুসন্ধান করা—সেটি হতে পারে দর্শক, কনটেন্ট নির্মাতা অথবা অ্যালগরিদম।
১. দর্শকদের অ্যালগরিদম চালিত ফিডের অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান
অনুসন্ধান শুরুর জন্য সবচেয়ে ভালো জায়গা হচ্ছে দর্শক বা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের ওপর মনোযোগ দেওয়া। অনেক সময় এসব ব্যবহারকারী অনিচ্ছাকৃতভাবেই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করেন বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করা বা তথ্য সংগ্রহের জন্য।
যেমনটা আগেই আলোচনা করেছি যে ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্যের অভিজ্ঞতা প্রত্যেকের জন্য আলাদা। অ্যালগরিদম ও নিউজফিড যে ভুল ধারণা তৈরি করে, তা বোঝার জন্য সাংবাদিকরা চাইলে একজন ব্যবহারকারীর অনলাইনে দেখা কনটেন্টের তথ্য নিয়ে কাজ করতে পারেন—অথবা একজন ব্যক্তিগত অনলাইন অভিজ্ঞতাকে তথ্য ও পরিসংখ্যান (কোয়ালিফাইড সেলফি) আকারে তুলে ধরতে পারেন।
এই পদ্ধতিতে কারও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের অভিজ্ঞতা বোঝার জন্য তার ব্যক্তিগত ডেটায় প্রবেশের অনুমতি চাইতে হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডেটা ও সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন (জিডিপিআর) এর কারণে ইউরোপে কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী অনেক কোম্পানি—যেমন টিকটক, মেটা ও এক্স —ব্যবহারকারীদের নিজ ডেটার ওপর অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ দিতে বাধ্য হয়। এর মানে হলো, ব্যবহারকারীরা অনলাইনে কী করছেন, কোন সাইটে গেছেন, কী ডাউনলোড করছেন তা মুছে ফেলার সুযোগ পান।
ডকুমেন্টেড-এর জন্য করা একটি প্রতিবেদনে, সাংবাদিক মালিক গাই সেনেগালের পাঁচজন অভিবাসীর কাছ থেকে তাদের টিকটক ভিউইং আর্কাইভ সংগ্রহ করেন। এসব অভিবাসীরা টিকটকে পাওয়া কিছু তথ্য থেকে প্রলুব্ধ হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। নিজ মাতৃভাষার তথ্যে পাওয়া যায় বলে তারা মূলত এই প্ল্যাটফর্মের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। আর্কাইভে গিয়ে সাংবাদিক দেখতে পান যে, ব্যবহারকারীদের দেখা অনেক ভিডিওতে অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়া হয়েছে। যেমন, কিছু ভিডিওতে বিদেশে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য আবেদনপত্র কীভাবে পূরণ করতে হবে সে বিষয়ে ভুল নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যা অনুসরণ করলে তাদের অভিবাসন প্রক্রিয়ায় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারত। আরেকটি ভিডিওতে মিথ্যা দাবি করা হয়েছে যে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র অভিবাসীদের মধ্যে ৫ কোটি মার্কিন ডলার বিতরণ করছেন। যদিও টিকটকের মালিকানা প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্স এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।
একইভাবে, সাংবাদিকরা তরুণীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সোশ্যাল মিডিয়ার বিধ্বংসী প্রভাব নিয়েও অনুসন্ধান করেছেন। এনবিসি নিউজের সাংবাদিক ক্যাট টেনবার্জ এক্স (টুইটার) প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারকারীদের এমন কয়েকটি গ্রুপ খুঁজে পান, যারা ইটিং ডিসঅর্ডারকে (মানুষের খাদ্যাভাসের আচরণজনিত মানসিক সমস্যা) উসকে দিচ্ছিল। যাদের সদস্যসংখ্যা ছিল ২ হাজার থেকে ১ লাখ ৭৩ হাজারের মধ্যে। এরমধ্যে কেউ কেউ নিজেদের মাত্র ১৩ বছর বয়েসী হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। এনবিসি নিউজকে দেয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “ব্যক্তির নিজের ক্ষতির প্রবণতাকে উৎসাহিত করে বা প্রচার করে— এক্স এমন কনটেন্টকে নিষিদ্ধ করে। আমরা শিশু যৌন শোষণের প্রতি শূণ্য সহনশীল নীতি গ্রহণ করি। এই ঘটনার বিস্তারিত পর্যালোচনার পর আমাদের প্লাটফর্মের নিয়ম ভঙ্গের কারণে ওই অ্যাকাউন্টগুলো মুছে ফেলা হয়েছে।”
২০২৫ সালের তথ্যচিত্র “ক্যান্ট লুক অ্যাওয়ে”তে ফেসবুক, টিকটক এবং ইনস্টাগ্রামে কাজ করা প্রাক্তন হুইসেলব্লোয়ারদের সামনে আনা হয়। অ্যালগরিদম কিভাবে কনটেন্ট দেখানোর মাধ্যমে ক্ষতি করতে পারে—তথ্যচিত্রটি তা তুলে ধরে। বিশেষ করে তরুণদের ক্ষেত্রে। হুইসেলব্লোয়ারদের একজন চার্লস বাহার। তিনি টিকটকের কাজ নিয়ে আলোচনা করার সময় বলেন, অ্যালগরিদমের কোনো অনুভূতি বা নৈতিক বিচারবোধ নেই। সে শুধু দেখে কোন কনটেন্টে বেশি মনোযোগ পাওয়া যাচ্ছে। ফলে, এমন কনটেন্ট যদি হয় উস্কানিমূলক, ক্ষতিকর, বা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক, তবুও অ্যালগরিদম তা উৎসাহিত করতে পারে—কারণ তার লক্ষ্য শুধুই এনগেজমেন্ট বাড়ানো। অর্থাৎ, কেউ যদি বিষণ্ণতা বিষয়ক কোনো কনটেন্ট দেখে, তখন তাদের ফিড খুব দ্রুত একই ধরনের কনটেন্টের একটি ইকো চেম্বারে পরিণত হয়। টিকটক দাবি করে তারা “তরুণ দর্শকদের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা, স্ক্রিন-টাইম ম্যানেজমেন্ট টুলস, অভিভাবক ও পরিবারের জন্য নিরাপত্তা টুল এবং অন্যান্য অনুরূপ সংস্থান প্রদান করে।
ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে কাজ করেছেন এমন হুইসেলব্লোয়ারদের একজন আর্তুরো বেজার। তিনি জানান, এই ধরনের কোম্পানিগুলো ব্যবহারকারীদের বোঝাতে চায় যে “নট ইন্টারেস্টেড” এ ক্লিক করার মাধ্যমে আপনি আপনার ফিডে যা দেখতে চান না তা নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পান। তবে এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকর নয়। কারণ অ্যালগরিদম এখনও মূলত সেই কনটেন্টই দেখায় যা ব্যবহারকারীরা বেশি সময় দেখেন। মেটা দাবি করে তারা তাদের প্ল্যাটফর্মে কম বয়সী কিশোরদের কনটেন্ট দেখার অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য ৩০টির বেশি ফিচার চালু করেছে।
এদিকে চার্লস বাহার আরও বলেন, কোনো প্ল্যাটফর্মে অস্বস্তিকর বা উদ্বেগজনক কনটেন্টগুলো কেন বারবার ব্যবহারকারীর সামনে আসছে—এক্ষেত্রে বুঝতে হবে সমস্যাটি আসলে কাঠামোগত।” তাই সাংবাদিকরা চাইলে উল্টোভাবে পরীক্ষা করতে পারেন—যেমন, তারা যদি কোনো নির্দিষ্ট ধরনের কনটেন্টে বেশি ইন্টার্যাক্ট করেন, তাহলে তাদের ফিড কেমন হয় তা দেখে অনুমান করতে পারেন সাধারন ব্যবহারকারীদের ওপর এর প্রভাব কী হতে পারে।
২. অ্যালগরিদমের সুযোগ নিয়ে কনটেন্ট নির্মাতারা কীভাবে ক্ষতিকর বা ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে দেয়—তা অনুসন্ধান”
কিভাবে কনটেন্ট নির্মাতারা অ্যালগরিদমের সুযোগ নিয়ে ক্ষতিকর বা মিথ্যা তথ্য ছড়ান তা অনুসন্ধানে আপনি যদি সমস্যাজনক কনটেন্ট নির্মাতাদের দিকে মনোযোগ দিতে চান, তাহলে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর ভাইরাল কনটেন্ট খুঁজে সেটির উৎস অনুসরণ করতে পারেন।
অসৎ উদ্দেশ্যের ব্যক্তি যারা ভুয়া তথ্য ছড়ানোর কাজ করে, তারা মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বারবার পোস্ট করে থাকে।
কোড ফর আফ্রিকার একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, ঘানাভিত্তিক নয়—এমন ১৬টি ফেসবুক অ্যাকাউন্টের একটি নেটওয়ার্ক ধারাবাহিকভাবে রাশিয়াপন্থী বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তারের ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে দিচ্ছিল। তারা একই পোস্ট বারবার কপি-পেস্ট করে এই তথ্য প্রচার করছিল। রিপোর্টারের মতে, এসব অ্যাকাউন্ট ছিল আইভরি কোস্ট, বুর্কিনা ফাসো, মালি, ফ্রান্স ও স্পেনভিত্তিক।
আরেকটি প্রতিবেদনের জন্য, সুইস সরকারি সংবাদ সংস্থা শ্ভেইৎসার রাডিও উন্ড ফের্নেজেন (এসআরএফ) মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে ভুয়া অ্যাকাউন্ট শনাক্ত করেছিল। তারা ৫ হাজার ভুয়া অ্যাকাউন্ট কিনে সেই অ্যাকাউন্টগুলোর বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে মেশিন লার্নিং মডেল প্রশিক্ষণ দেন এবং পরে সেই প্রশিক্ষিত মডেল ব্যবহার করে আরও ভুয়া অ্যাকাউন্ট শনাক্ত করেন।

ঘানায় প্রো-রাশিয়া প্রচারণার প্রভাব নিয়ে কোড ফর আফ্রিকার এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ওই অ্যাকাউন্টগুলো আসলে বাইরের দেশের ছিল। ছবি: কোড ফর আফ্রিকা
৩. অ্যালগরিদম কীভাবে কাজ করে তা অনুসন্ধান
আরেকটি পদ্ধতি হলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অ্যালগরিদমের প্রভাব নিয়ে লেখা।
এসব প্রতিবেদনে ব্যবহারকারীদের অনলাইন অভিজ্ঞতার বড় অংশকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে—তা বিশ্লেষণের পাশাপাশি তথ্যের বিস্তার এবং কীভাবে তা ব্যবহারকারীর ফিডে আসছে, এক্ষেত্রে অ্যালগরিদম কী ধরনের প্রভাব রাখছে তা তুলে ধরতে হবে।
কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা অত্যন্ত জটিল—কারণ এগুলো অস্বচ্ছ, জটিল এবং সাধারণ মানুষের জন্য বোঝা কঠিন। উদাহরণস্বরূপ, দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের মতে, ফেসবুকের অ্যালগরিদম প্রায় ১০ হাজারটির বেশি সংকেত বিশ্লেষণ করে অনুমান করে যে ব্যবহারকারী ওই পোস্টে প্রতিক্রিয়া দেখাবে কিনা।
এর অর্থ, সাংবাদিকদের অনেক সময় তথ্য সংগ্রহ এবং টেস্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে কিছু অ্যালগরিদম কীভাবে কাজ করে তা বিপরীতভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ১০০টি টিকটক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে পরীক্ষা করে যে, বেশি সময় নিয়ে কোনো পোস্ট পড়া বা কোনো ভিডিও পুনরায় দেখার ফলে ওই অ্যাকাউন্টগুলোর ফিডে কী ধরনের প্রভাব পড়ে।
তবে প্রযুক্তি নিয়ে অনুসন্ধানে সবারই উচ্চতর প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। একজন প্রতিবেদক হিসেবে সব সময় ব্যাখ্যা করার দরকার নেই যে সামগ্রিক পদ্ধতিটি কীভাবে কাজ করে। কখনো কখনো শুধু সিস্টেমকে “টোকা দেওয়াই” যথেষ্ট, এবং দেখানো যে এটি ক্ষতি করছে।
প্রোপাবলিকার এই প্রতিবেদনে, সাংবাদিকরা ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন এবং দেখেন, প্ল্যাটফর্মটি তাদেরকে জাতি, লিঙ্গ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানুষকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞাপন দিতে বাধা দেয়নি। তারা কীভাবে আইন ভাঙার পথ খুঁজে পেয়েছেন তা দেখিয়ে প্রমাণিত হয় যে ফেসবুক ক্ষতি ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে ফেসবুক প্রোপাবলিকাকে জানিয়েছে যে, লিঙ্গ, জাতি বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বৈষম্য তৈরি করে—তারা এমন বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপন দেওয়া থেকে আটকায়।”
সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলো কীভাবে অ্যালগরিদমের ক্ষতি কমাতে ব্যর্থ হচ্ছে—তা অনুসন্ধান
সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর অন্তর্নিহিত কার্যপ্রণালী গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করাও জরুরি। কোম্পানির বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে, তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার তথ্য খতিয়ে দেখে অথবা হুইসেলব্লোয়ারদের সঙ্গে কথা বলার মাধ্যমে সাংবাদিকরা এই কাজ করতে পারেন।
উদাহরণস্বরূপ, ইথিওপিয়ার অধ্যাপক মেয়ারেগ আমারের হত্যাকাণ্ড নিয়ে অনুসন্ধানে নামেন ইনসাইডারের সাংবাদিক টেকেন্দ্র পরমার। ফেসবুকে বিদ্বেষ ও মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে অধ্যাপক মেয়ারেগকে হত্যা করা হয়। ফেসবুকের ট্রাস্টেড পার্টনার প্রোগ্রামের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেন পরমার। এই প্রোগ্রামটি হলো বিভিন্ন নাগরিক সমাজ সংগঠনের একটি নেটওয়ার্ক, যারা ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান দিয়ে কোম্পানিকে বিদ্বেষমূলক তথ্য চিহ্নিত করতে ও জানাতে সাহায্য করে। প্রোগ্রামের ছয়জন অংশগ্রহণকারী পরমারকে জানান যে, ফেসবুক নিয়মিতভাবে তাদের বিদ্বেষমূলক কনটেন্টের সতর্কতা উপেক্ষা করেছে, যার মধ্যে আমারের বিরুদ্ধে ছড়ানো মিথ্যা তথ্যের বিষয়টিও ছিল। তারা পরমারকে ফেসবুকের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ পর্যালোচনার অনুমতিও দিয়েছে। মেটা, যা ফেসবুকের প্যারেন্ট কোম্পানি, ইনসাইডারকে জানিয়েছে তারা ট্রাস্টেড পার্টনারদের দ্বারা রিপোর্টকৃত কনটেন্ট যত দ্রুত সম্ভব পর্যালোচনা করার চেষ্টা করে, যদিও সময়কালের তারতম্য থাকতে পারে।
এই উদাহরণগুলো যেমনটা দেখায় যে, সোশ্যাল ওয়েব নিয়ে অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন ধরনের রিপোর্টিং পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। এর মধ্যে থাকতে পারে প্ল্যাটফর্ম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করার মতো উচ্চতর প্রযুক্তি ব্যবহার, কিংবা ডিজিটাল ফরেনসিক পদ্ধতি দিয়ে অসৎ উদ্দেশ্যের মানুষদের খুঁজে বের করা। তবে সাংবাদিকরা কম প্রযুক্তির পদ্ধতিতেও সফল হতে পারেন। যেমন প্ল্যাটফর্মে ক্ষতির মুখোমুখি হওয়া ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেয়া বা ক্ষতিকর প্রভাব প্রমাণের জন্য ছোট ছোট পরীক্ষা চালানো। এক্ষেত্রে, সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম নিয়ে সফল অনুসন্ধানের মূল চাবিকাঠি হলো সৃজনশীল পদ্ধতি।
এ সম্পর্কিত আরো কিছু বিষয় নিয়ে পড়তে পারেন
সাংবাদিকদের জন্য কিছু টুল
- অ্যালগরিদমিক লিটারেসি ফর জার্নালিস্টস: সাংবাদিক ও সংবাদকক্ষকে অ্যালগরিদম বুঝতে সাহায্য করার জন্য একটি ব্যবহারিক টুলকিট। এই গবেষকরা অ্যালগরিদমের ওপর নিরীক্ষা চালানোর জন্য একটি সংক্ষিপ্ত গাইডও তৈরি করেছেন।
- ইন্ডিকেটর: ভুল ও মিথ্যা তথ্য নিয়ে বিশেষজ্ঞ ক্রেগ সিলভারম্যান এবং আলেক্সিওস মানটজার্লিসের নিউজলেটার।
- বেলিংক্যাট: সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপক যাচাই-বাছাই কাজ করে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যারা অনেক সহায়ক গাইডও প্রকাশ করে।
- নিউ ইনভেস্টিগেটিভ টুলস ফর মনিটরিং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মস: জিআইজিএন-এর একটি প্রবন্ধ।
- মাইনিং সোশ্যাল মিডিয়া: সোশ্যাল ওয়েব থেকে ডেটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য পাইথন ভিত্তিক একটি বই।
- দ্য অ্যালগরিদমস বিট: এঙ্গেলস অ্যান্ড মেথডস ফর ইনভেস্টিগেশন: ডেটা সাংবাদিকতা হ্যান্ডবুকের একটি অধ্যায় যা অ্যালগরিদম অনুসন্ধানের পদ্ধতি নিয়ে লেখা হয়েছে।
গবেষণা প্রতিষ্ঠান
- অ্যালগরিদমিক জাস্টিস লিগ: একটি প্রতিষ্ঠান যা অ্যালগরিদমজনিত ক্ষতি নথিভুক্ত ও পরীক্ষা করে।
- এআই নাউ ইনস্টিটিউট: একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অ্যালগরিদম দায়বদ্ধতা নিয়ে গবেষণা প্রকাশ করে।
- সেন্টার ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড টেকনোলজি: একটি অলাভজনক সংস্থা, যা ডিজিটাল যুগের নাগরিক স্বাধীনতা নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করে।
- ডেটা অ্যান্ড সোসাইটি: প্রযুক্তি, ডেটা এবং নীতিমালা নিয়ে গবেষণা করে এমন একটি অলাভজনক সংস্থা।
- অ্যালগরিদম ওয়াচ: জুরিখ এবং বার্লিনভিত্তিক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান।
 লাম থুই ভো একজন সাংবাদিক। বিভিন্ন নীতি ও পদ্ধতি ব্যক্তিকে কীভাবে প্রভাবিত করে—তথ্য বিশ্লেষণের সাথে মাঠ পর্যায়ের রিপোর্টিংয়ের মিশেলে তিনি তা তুলে ধরেন। বর্তমানে অনুসন্ধানী প্রতিবেদক হিসেবে অভিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিবেদিত স্বাধীন ও অলাভজনক বার্তাকক্ষ ডকুমেন্টেডের জন্য কাজ করছেন। পাশাপাশি তিনি ক্রেগ নিউমার্ক গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব জার্নালিজমে ডেটা সাংবাদিকতার সহযোগী অধ্যাপক। দ্য মার্কআপ, বাজফিড নিউজ, দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, আল জাজিরা আমেরিকা, এবং এনপিআর-এর প্ল্যানেট মানিতে সাংবাদিক হিসেবে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে।
লাম থুই ভো একজন সাংবাদিক। বিভিন্ন নীতি ও পদ্ধতি ব্যক্তিকে কীভাবে প্রভাবিত করে—তথ্য বিশ্লেষণের সাথে মাঠ পর্যায়ের রিপোর্টিংয়ের মিশেলে তিনি তা তুলে ধরেন। বর্তমানে অনুসন্ধানী প্রতিবেদক হিসেবে অভিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিবেদিত স্বাধীন ও অলাভজনক বার্তাকক্ষ ডকুমেন্টেডের জন্য কাজ করছেন। পাশাপাশি তিনি ক্রেগ নিউমার্ক গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব জার্নালিজমে ডেটা সাংবাদিকতার সহযোগী অধ্যাপক। দ্য মার্কআপ, বাজফিড নিউজ, দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, আল জাজিরা আমেরিকা, এবং এনপিআর-এর প্ল্যানেট মানিতে সাংবাদিক হিসেবে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে।