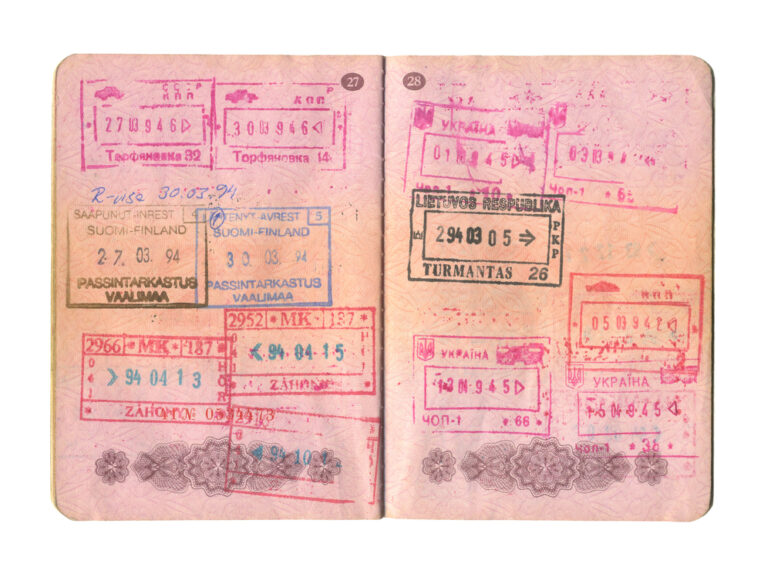কোভিড-১৯: লড়াই যখন গুজবের সাথে
“কোভিডের এই সময়ে একটা সঠিক তথ্য আর একটা ভুল তথ্যের মাঝখানে থাকে মানুষের জীবন। একটা ভুয়া খবরও তাই যে কোনো সময় হতে পারে কারো না কারো মৃত্যুর কারণ,” এক ওয়েবিনারে একথা বলছিলেন ঢাকায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মুখপাত্র ক্যাটালিন বেরকারু। “কোভিড-১৯: লড়াই যখন গুজবের সাথে” শীর্ষক ওয়েবিনারটি আয়োজন করে গণমাধ্যম উন্নয়ন সংস্থা ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই) এবং সুইডেনভিত্তিক ফোয়ো মিডিয়া ইনস্টিটিউট।
জিআইজেএন রিসোর্স সেন্টারে দেখুন কোভিড-১৯ কাভারের গাইড ও রিসোর্স।
কোভিড সংকটের এই সময়ে ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর তথ্য কিভাবে ছড়াচ্ছে, কত রকমের ভুয়া খবর দেখা যাচ্ছে, গুজব ঠেকাতে গণমাধ্যম কী করতে পারে – এমন সব বিষয় নিয়ে ওয়েবিনারে আলোচনা করেন কাটালিন বেরকারু, ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক ডা. মোর্শেদা চৌধুরী এবং বাংলাদেশ ও ভারতের দুই তথ্য যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান বিডি ফ্যাক্টচেক থেকে কদরুদ্দিন শিশির ও বুম বাংলার স্বস্তি চ্যাটার্জি। ওয়েবিনারটি সঞ্চালনা করেছেন এমআরডিআইয়ের হেড অব প্রোগ্রাম ও জিআইজেএন বাংলা সম্পাদক মিরাজ আহমেদ চৌধুরী।
.
তথ্যের মহামারি কী?
“আমাদের যুদ্ধ শুধু স্বাস্থ্য-মহামারির (এপিডেমিক) বিরুদ্ধে নয়, আমরা তথ্যের মহামারির (ইনফোডেমিক) সাথেও লড়ছি,” বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউওইচও) প্রধান তেদরোস আদানোম গেব্রেইয়েসুস একথা বলেছিলেন গত ১৫ ফেব্রুয়ারিতে। তারপরে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসসহ আরো অনেকের মুখে শোনা গেছে এই তথ্য মহামারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা। কোভিড-১৯ সংকটে গুজবের বিস্তার যে বাড়তে যাচ্ছে, তা অনুমান করে গত জানুয়ারিতেই ভুয়া তথ্য যাচাইয়ের একটি আন্তর্জাতিক জোট গঠন করে ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাক্টচেকিং নেটওয়ার্ক (আইএফসিএন)।
একটি নির্দিষ্ট বিষয় এভাবে পুরো বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করে নেওয়ার ঘটনা বিরল। সংবাদমাধ্যমসহ সব জায়গায় আলোচনার কেন্দ্রে এই করোনাভাইরাস। রোগটি নতুন হওয়ায় মানুষের মধ্যে এ সংক্রান্ত তথ্যের চাহিদাও আছে প্রবলভাবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর তথ্য সামনে আসছে। সেখানে সত্য যেমন আছে, তেমনি আছে অনেক মিথ্যা এবং বিভ্রান্তি। মানুষের জন্য বুঝে ওঠা কঠিন হচ্ছে কোনটা বিশ্বাসযোগ্য আর কোনটা নয়। ফলে অনেক সময়ই তারা ভুল তথ্য বিশ্বাস করছেন এবং সেটি ছড়িয়ে দিচ্ছেন। হাজার রকম তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত এমন একটি পরিস্থিতিকেই ইনফোডেমিক বা তথ্য মহামারি বলে আখ্যা দিয়েছেন ডব্লিউওইচওর প্রতিনিধি কাটালিন।
তাঁর মতে, ভুয়া যেসব তথ্য আসছে, তার মধ্যে কিছু কিছু ততটা ক্ষতিকর নয়। যেমন বেশি করে পানি বা আদা-রসুন খাওয়ার মতো পরামর্শ। কিন্তু কিছু ভুয়া-তথ্য বেশ ক্ষতিকর হতে পারে। যেমন, অ্যালকোহল খেলে কোভিড-১৯ সেরে যায়। আবার আপাতদৃষ্টিতে কম ক্ষতিকর ভুয়া তথ্যেরও অন্য ক্ষতিকর দিক আছে। সেটি হলো: ভুয়া তথ্যে পাওয়া পরামর্শের দিকে নজর দিতে গিয়ে আসল পরামর্শগুলো (ঘরে থাকা, হাত ধোয়া) থেকে মনোযোগ সরে যাচ্ছে।
মানুষ কী বিশ্বাস করে?
কিভাবে এই ইনফোডেমিক জনগণকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বাধা দিচ্ছে, তা তুলে ধরেন ব্রাকের ডা. মোর্শেদা। কোভিড-১৯ নিয়ে সাম্প্রতিক এক জরিপে আরো অনেক বিষয়ের সাথে ব্র্যাক প্রশ্ন রেখেছিল – মানুষ এই ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য কিভাবে জেনেছে এবং কী জেনেছে। তার ফলাফল থেকে দেখা গেছে, ৯৯.৬ শতাংশ মানুষ জানে যে, রোগটি কী। দুই তৃতীয়াংশ মানুষই জেনেছে টেলিভিশনের মাধ্যমে। কিন্তু ৫৬ শতাংশ মানুষ এটি জানে না যে, রোগটি কিভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। আবার দুই তৃতীয়াংশ মানুষ চিকিৎসা সম্পর্কিত নানা ভুয়া তথ্য বিশ্বাস করেন বলে জানিয়েছেন।
রোগটি নতুন হওয়ায় মানুষের মধ্যে এ সংক্রান্ত তথ্যের চাহিদাও আছে প্রবলভাবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর তথ্য সামনে আসছে। সেখানে সত্য যেমন আছে, তেমনি আছে অনেক মিথ্যা এবং বিভ্রান্তি। মানুষের জন্য বুঝে ওঠা কঠিন হচ্ছে কোনটা বিশ্বাসযোগ্য আর কোনটা নয়।
করোনাভাইরাস মোকাবিলার জন্য ঘরে থাকা, হাত ধোয়া, কাশি শিষ্টাচার মেনে চলা – এমন অনেক প্রতিরোধমূলক বার্তা ক্রমাগত প্রচারিত হওয়ার পরও ৫৬ শতাংশ মানুষ নিশ্চিত নন, এটি কিভাবে প্রতিরোধ করতে হবে। ডা. মোর্শেদার মতে, অনেক সূত্র থেকে অনেক ধরনের তথ্য পাওয়ায় মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে, এবং আসল জায়গা থেকে মনোযোগ সরে গেছে। তিনি বলেন, “মহামারির শুরু থেকেই মানুষ এ বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য অনেকাংশে নির্ভর করেছে গণমাধ্যমের ওপর। একেক গণমাধ্যম, একেকভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেছে। একেক গণমাধ্যম একেক বিশেষজ্ঞকে হাজির করেছে এবং তারা নিজেদের মতো করে মতামত দিয়েছেন। ফলে হাজারো তথ্যের ভীড়ে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে গেছে।” এর বাইরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকেও তারা অনেক ভুয়া তথ্য পেয়েছেন।
মানুষ কেন ভুয়া চিকিৎসা পরামর্শে বিশ্বাস করে, তা আরেকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কাটালিন। তাঁর মতে, নিজেদের সুরক্ষিত রাখার জন্য শুধু ঘরে বসে থাকা ও হাত ধোয়ার বাইরেও মানুষ আরো কিছু করতে চায়। আরো ব্যবস্থা নিতে চায়। আর এসব জায়গাতেই হাজির হয় চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা গুজব বা ভুয়া তথ্য।
তবে নিজেদের সুরক্ষিত রাখার জন্য নির্ভরশীল সূত্রগুলো থেকে পাওয়া তথ্যের দিকেই সবাইকে মনোযোগ দিতে হবে বলে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কাটালিন। যে কোনো প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য শুরুতেই ডব্লিউএইচও-র ওয়েবসাইটে ঢুঁ মারার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এখানে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য এক জায়গায় আছে। একইসঙ্গে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশ সরকারের তৈরি ওয়েবসাইট করোনা ডট গভ -এর কথা। এখানেও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য আছে বলে জানিয়েছেন কাটালিন, “শুধু ডব্লিউএইচও থেকে নেওয়া তথ্যই না, অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান যারা ইনফোগ্রাফিক্স, ভিডিও, পোস্টার বানাচ্ছে, তাদের এসব কনটেন্টও আছে এই সাইটে।”
ছবি: পিক্সাবে
গুজব যখন যেমন
করোনাভাইরাস যত দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে, গুজবও যেন ছড়াচ্ছে একইভাবে। আর পরিস্থিতি যত সংকটময় হয়েছে, ভুয়া তথ্যের ধরনও ততই সংবেদনশীল হয়ে উঠছে। সময়ের সাথে সাথে কিভাবে ভুয়া তথ্যের বিস্তার ঘটছে, সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন বাংলাদেশ ও ভারতের দুই তথ্য যাচাইকারী কদরুদ্দিন শিশির ও স্বস্তি চ্যাটার্জি। প্রতিবেশী দুই দেশের ক্ষেত্রে ভুয়া তথ্য বা গুজবের ধরনে অনেক মিল দেখা গেছে। চিকিৎসা সংক্রান্ত টোটকা ও ধর্মীয় সংযোগ সংক্রান্ত ভুয়া তথ্যের বিস্তার ছিল দুই দেশেই।
দুই দেশের ক্ষেত্রেই কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ভুয়া তথ্যের প্রথম ধাপে ছিল নানাবিধ ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ও জাতিগত বিদ্বেষ বা শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়। এই পর্বে আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়নি বা খুব অল্প পরিমাণে ছিল। শিশির জানান, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই সময়ে এমন ভুয়া তথ্য প্রচার পেয়েছে যে, এটি খাদ্যাভাসের কারণে বিশেষভাবে চীনের মানুষের হয়েছে। কিন্তু এ দেশে তেমনটি হবে না। এই সময়ে এমন ভুয়া তথ্যের আধিক্য দেখা গেছে যে, এটি মুসলমানদের হবে না, বা মুসলিম দেশগুলোতে হবে না। এসময় খাদ্যাভ্যাস নিয়ে বেশ কিছু ভুয়া ভিডিও সামনে এসেছিল বলে জানান স্বস্তি।
দ্বিতীয় ধাপে, কোভিড-১৯ রোগী সনাক্ত হওয়ার পর বদলে যায় ভুয়া তথ্যের ধরন। দুই দেশেই বেশি করে দেখা যেতে থাকে চিকিৎসা পরামর্শগত নানা ভুয়া তথ্য। ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জারি করা জনতা কারফিউকে ঘিরে নতুন করে কিছু ভুয়া তথ্য ছড়িয়েছে বলে জানান স্বস্তি। যেমন, থালা-বাটিতে শব্দ করলে করোনাভাইরাস মরে যাবে। এই সময়ে ভারতে অনেক ভুয়া নির্দেশনা, প্রজ্ঞাপন ঘুরতে থাকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। বিশেষ করে হোয়াটসঅ্যাপে। যেন সত্যি মনে হয়, সেজন্য এগুলোর সঙ্গে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লোগোও বসিয়ে দেওয়া হয়।
বুম বাংলা ও বিডি ফ্যাক্টচেকের প্রতিবেদনের স্ক্রিনশট
ভুয়া তথ্যের বিস্তারে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক চেহারা দেখা গেছে দুই দেশের ক্ষেত্রেই। তবে দুই জায়গায় ভুয়া তথ্যের ধরন ছিল ভিন্ন রকমের। যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিল ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বকেন্দ্রিক। যেমন, বিভিন্ন স্থানে অনেকে মুসলমান হয়ে যাচ্ছেন বা ট্রাম্প কোরআন তেলাওয়াত শুনছেন বা চীনের প্রেসিডেন্ট মসজিদে গিয়ে দোয়া চাইছেন, ইত্যাদি। অন্যদিকে ভারতে দেখা গেছে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। স্বস্তি জানান, গত ২২ মার্চ দিল্লির নিজামুদ্দিনে আয়োজিত একটি তাবলিগ জামাতে উপস্থিত কয়েকজনকে কোভিড-১৯ পজেটিভ হিসেবে সনাক্ত করা হয়। এরপর থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষদের দোষী করে প্রচারণা শুরু হয় এবং এ সংক্রান্ত অনেক ভুয়া তথ্য ছড়াতে থাকে।
সংকট ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভুয়া তথ্যের ধরনও আরো সংবেদনশীল হয়েছে বলে মনে করেন স্বস্তি। তিনি বলেন, “এসময় ছড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে অনেক ভুয়া অডিও বার্তা। অনিশ্চয়তা, সংশয়ের একটি সময়ে যেগুলো মানুষ বেশি করে বিশ্বাস করেছে।” আবার কিছু সত্য তথ্যকেও ভুয়া বা গুজব বলে প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিশির। তিনি বলেন, “সরকার বা কর্তৃপক্ষ যেসব তথ্য প্রকাশ হতে দিতে চাইছে না, সেসব তথ্য সত্য হলেও তা গুজব, মিথ্য বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে।”
মূলধারার গণমাধ্যমের ভূমিকা
দুই দেশের অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা যাচ্ছে, চিকিৎসা বিষয়ে নানা টোটকা হয়ে উঠছে ভুয়া তথ্যের বিষয়বস্তু। ব্রাকের জরিপ থেকে দেখা গেছে, ৬৫ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনো ভুয়া তথ্য পেয়েছে চিকিৎসা টোটকা নিয়ে। কেন এগুলো ছড়াচ্ছে, কিভাবে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং এক্ষেত্রে মূলধারার গণমাধ্যমের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিৎ, তা আলোচনা করেছেন ডা. মোর্শেদা চৌধুরি। তাঁর মতে, এ ব্যাপারে সংবেদনশীল কোনো তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে আরো সতর্ক হওয়া উচিৎ সংবাদমাধ্যমগুলোর। তিনি বলেন, “আমরা যদি [চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো গবেষণার খবর] এটা মিডিয়াতে দেই, তাহলে মানুষের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া আসবে? বিষয়টি হয়তো একটা গবেষণায় বলা হয়েছে। কিন্তু এটা ক্লিনিকাল ট্রায়ালে যেতে হবে। ডব্লিউএইচও এটির স্বীকৃতি দেবে। তারপর বলা যাবে যে হ্যাঁ, এটি কাজ করে। এখনই কিন্তু সেটির [কার্যকারিতা] ঘোষণা করা হয়নি। কিন্তু এ জাতীয় তথ্য মিডিয়াতে প্রচার করা হয়েছে।”
“মহামারির শুরু থেকেই মানুষ এ বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য অনেকাংশে নির্ভর করেছে গণমাধ্যমের ওপর। একেক গণমাধ্যম, একেকভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেছে। একেক গণমাধ্যম একেক বিশেষজ্ঞকে হাজির করেছে এবং তারা নিজেদের মতো করে মতামত দিয়েছেন। ফলে হাজারো তথ্যের ভীড়ে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে গেছে।” — ডা. মোর্শেদা চৌধুরী, ব্রাক
সংবাদমাধ্যমগুলোতে, বিশেষ করে ডিজিটাল মাধ্যমগুলোতে “ক্লিকবেইট সাংবাদিকতা”র প্রসার নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্বস্তি। কোনো খবর সবার আগে পাঠক-দর্শককে জানানোর যে প্রতিযোগিতা এবং বেশি ক্লিকের আশায় চাঞ্চল্যকর শিরোনাম ব্যবহারের যে চর্চা বিশেষভাবে ডিজিটাল মাধ্যমগুলোতে চলে, তা থেকে সবাইকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ভারতের এই তথ্য যাচাইকারী। বিশেষ করে এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে, যখন ভালোভাবে যাচাই না করা একটি তথ্য মানুষের জীবন-মরনের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। স্বস্তি বলেন, “ব্রেকিং নিউজের প্রতিযোগিতায় না গিয়ে আমাদের এখন নিজেদের একটু সময় দিতে হবে। কোনো কিছু প্রকাশ করার আগে তথ্যগুলো বারবার যাচাই করতে হবে।” একই কথার প্রতিধ্বনি করেছেন এমআরডিআইয়ের নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান। তিনি বলেন “কোনো তথ্য যাচাই করা সম্ভব না হলে সেই নিউজ দেওয়াটাও উচিৎ না। এটিই দায়িত্বশীলতা।”
শিশিরের মতে, তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে মূলধারার গণমাধ্যম তথ্য যাচাইকারীদের সঙ্গে জোট বেঁধে কাজ করতে পারে। তারা চাইলে নিজেদের বার্তাকক্ষে আলাদা তথ্য যাচাই বিভাগ গড়ে তুলতে পারে বা কোনো যাচাই-প্রতিষ্ঠানেরও সাহায্য নিতে পারে পারে। “শুধু নিজেদের রিপোর্টের জন্য ভুয়া খবর যাচাই করা নয়, ভাইরাল হয়ে যাওয়া গুজবকে মিথ্যা প্রমাণ করে, তা মানুষকে জানানোও মূলধারার গণমাধ্যমের দায়িত্বে মধ্যে পড়ে,” বলেন তিনি।
ছবি: আনস্প্ল্যাশ
গুজব যাচাই কিভাবে
কোভিড-১৯ পরিস্থিতির আগে থেকেই ভুয়া তথ্যের বিস্তার নিয়ে উদ্বেগ ছিল সাংবাদিকতার জগতে। আর এই বৈশ্বিক মহামারি যেন তৈরি করেছে একটা ঝড়ের মতো পরিস্থিতি। স্বস্তি আশঙ্কা জানিয়ে বলেন, “আমরা যেন একটা ভুয়া তথ্য ও গুজবের ঝড়ের মধ্যে আছি। এখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসা কঠিন হবে। এই পরিস্থিতিতে তথ্য যাচাইকারীদের তো বটেই, সাংবাদিকদেরও খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন ভুয়া তথ্য নিয়ে। এবং সব কিছু যাচাই করে নেওয়াটাকে অভ্যাস বানিয়ে ফেলা উচিৎ। ব্যবহার করা উচিৎ তথ্য যাচাইয়ের বিভিন্ন টুল।”
“ব্রেকিং নিউজের প্রতিযোগিতায় না গিয়ে আমাদের এখন নিজেদের একটু সময় দিতে হবে। কোনো কিছু প্রকাশ করার আগে তথ্যগুলো বারবার যাচাই করতে হবে।” — স্বস্তি চ্যাটার্জি, বুম বাংলা
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভুয়া ছবি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে রিভার্স ইমেজ সার্চ খুবই কার্যকর বলে জানান স্বস্তি। ভিডিওর ক্ষেত্রে থাম্বনেইল বা ভিডিওর মূল কিছু ফ্রেমও যাচাই করা হয় রিভার্স ইমেজ সার্চের মাধ্যমে। সেখান থেকেও অনেক সময় বেরিয়ে আসে, ভিডিওটি কোন সময়ের এবং এটি সত্য না ভুয়া। সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ভিডিও সম্পর্কিত কিওয়ার্ড দিয়ে ইউটিউবে সার্চ করেও পাওয়া যেতে পারে অনেক প্রাসঙ্গিক তথ্য।
এর বাইরেও সোশ্যাল মিডিয়ার ভিডিওতে করা কমেন্ট থেকেও সঠিক তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে বলে জানান স্বস্তি। তিনি বলেছেন, “ফেক ভিডিওগুলো যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করা হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় কেউ হয়তো সেখানে জানিয়েছে যে, এই ভিডিওটি সত্যি নয়। এটি বাংলাদেশ বা ভারতের ভিডিও নয়।”
তবে অডিও-র মাধ্যমে ছড়ানো ভুয়া তথ্য যাচাই করা বেশ চ্যালেঞ্জিং বলে মত দিয়েছেন স্বস্তি। কারণ এখানে জানা যায় না যে, কে কথাগুলো বলছে। ফলে এটি যাচাই করাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এসব ক্ষেত্রে তাঁরা স্থানীয় পুলিশের সহায়তাও নিয়ে থাকেন।
সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই ভুয়া তথ্যের বিস্তার বেশি করে ঘটলেও এই সোশ্যাল মিডিয়া থেকেই সাংবাদিকরা পেতে পারেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। একারণে পশ্চিমা অনেক গণমাধ্যমই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের জন্য নিউজরুমে বিশেষ বিভাগ তৈরি করেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিষয়টি নতুন হলেও অনলাইনে অনুসন্ধান এবং ওপেন সোর্স ইনটেলিজেন্স ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের বিষয়টিতে এখন মনোযোগ দেওয়া উচিৎ বলে মত দিয়েছেন শিশির।
প্রয়োজনীয় রিসোর্স
ভুয়া তথ্য ও গুজব মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় অনেক পরামর্শ ও রিসোর্স আছে জিআইজেএন-এর ওয়েবসাইটে। সেই রিসোর্সের মধ্য থেকে কয়েকটি ওয়েবিনারে তুলে ধরেন জিআইজেএন বাংলা সম্পাদক মিরাজ চৌধুরী। আগ্রহীরা দেখে নিতে পারেন একনজরে:
ভুয়া তথ্য ছড়ানোর কৌশল ও সেগুলো যাচাইয়ের পদ্ধতি নিয়ে পড়ুন এই রিসোর্স গাইড: গুজব ছড়ানোর ৬টি কৌশল এবং সেগুলো যাচাইয়ের সহজ পদ্ধতি সামাজিক মাধ্যমে যে ছবিটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন তা কী আসল না নকল – তা যাচাই করা যায় রিভার্স ইমেজ সার্চের মাধ্যমে। সেই পদ্ধতি ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই লেখায়: স্মার্টফোনে ভুয়া ছবি যাচাইয়ের ৩টি সহজ পদ্ধতি ভুয়া তথ্য যাচাই করতে গেলে অনেক সময় পুরোনো সার্চ ফলাফল খুঁজে বের করার প্রয়োজন হয়। সেটি কিভাবে করতে হয়, তার হদিশ থাকছে এই লেখায়। একই সঙ্গে পাবেন ভিডিও যাচাইয়ের কৌশল: নাম ও ওয়েবসাইট ট্র্যাকিং, ভিডিও যাচাই এবং ক্লাস্টারিং সার্চ ইঞ্জিন ভুয়া তথ্যের বিচারে সামনে আসতে যাচ্ছে ডিপ ফেইক ভিডিওর জোয়াড়। যেখানে একজনের মুখ অন্যের শরীরের উপর বসিয়ে দেয়া হয়। এগুলো কিভাবে মোকাবিলা করবেন? নির্বাচনের আগে ভুয়া তথ্যের বিস্তার মোকাবিলা করার জন্য একজোট হয়েছিল মেক্সিকোর ৯০টি সংবাদ প্রতিষ্ঠান। কিভাবে তারা একত্রে লড়েছে ভুয়া তথ্যের বিরুদ্ধে? ভুয়া তথ্য যাচাই ও অনুসন্ধানের প্রাথমিক জায়গা হচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট বা ওয়েবসাইটের নেপথ্যে থাকা নেটওয়ার্ক খুঁজে বের করা। সেটি কিভাবে করবেন? দেখুন ভুয়া তথ্য ছড়ানোর নেপথ্যে কারা?
পার্থ প্রতীম দাস কাজ করছেন গণমাধ্যম উন্নয়ন সংস্থা ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)-এ। এর আগে আট বছর কাজ করেছেন বাংলাদেশের দুটি গণমাধ্যমের অনলাইন বিভাগে।