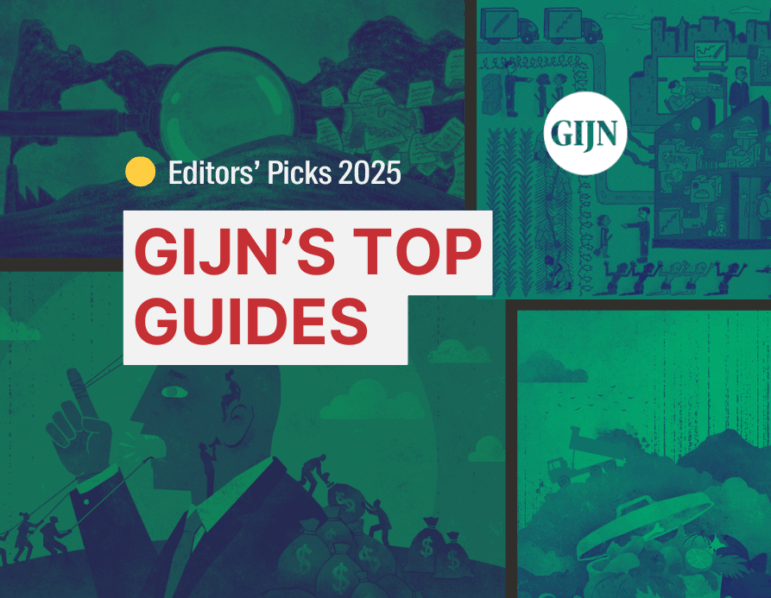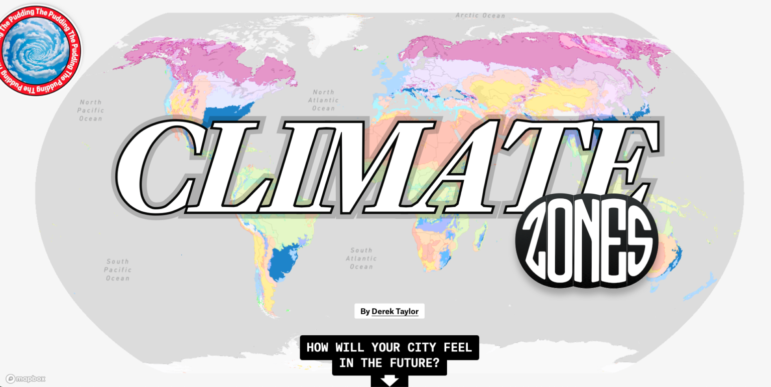
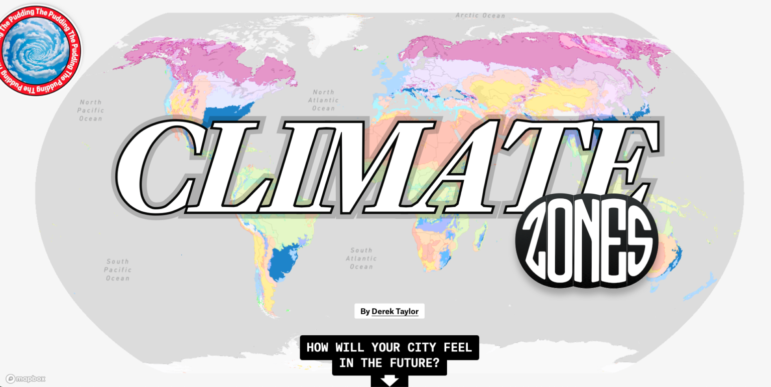
ছবি: স্ক্রিন শট। দ্য পুডিংয়ের সৌজন্যে
দ্য পুডিংয়ে ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন, জলবায়ু পরিবর্তনের গল্প পেয়েছে নতুন মাত্রা
আর্টিকেলটি পড়ুন এই ভাষায়:
জলবায়ু পরিবর্তন-এই কথাটা শুনলে কেমন লাগে? আজ থেকে ৫০ বছর পর আপনার নিজের শহরের জলবায়ু কেমন হবে? জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবগুলো কেমন হবে, এটা কীভাবে বোঝা যাবে?
দ্য পুডিংয়ের জন্য করা নিজের সাম্প্রতিক প্রকল্পে ডেটা সায়েন্টিস্ট ও জিআইএস (ভূ-স্থানিক তথ্য ব্যবস্থা) বিশেষজ্ঞ ডেরেক টেইলর এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে শুরু করেন। আফ্রিকায় জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে করা তাঁর আগের কাজটিকে আরও বাড়িয়ে টেইলর এবার বৈশ্বিক পরিসরে শহরগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনের চিত্রটা আগামীতে কেমন হবে জানার চেষ্টা করেন।
ফলাফল, ইন্টারঅ্যাকটিভ স্টোরি ক্লাইমেট জোনস। যেখানে বিশ্বের পাঁচটি আলাদা জলবায়ু অঞ্চল—শুষ্ক, ক্রান্তীয় অঞ্চল, নাতিশীতোষ্ণ, শীত প্রধান এবং মেরু অঞ্চলের ওপর ভিত্তি করে ৭০টি শহরের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো ডেটা চিত্রায়নের (ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন) মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। ২০২৩ সালের জলবায়ু সংক্রান্ত পরিসংখ্যানকে ২০৭০ সালের পূর্বাভাসের সাথে তুলনা করে তৈরি করা এই ডেটাসেটে। টেইলর দেখিয়েছেন—সময়ের সাথে সাথে এ অঞ্চলের শহরগুলোর জলবায়ু কীভাবে নাটকীয় কায়দায় বদলে যাবে।
তাঁর কাজ কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে চলমান আলোচনাকে একটি নতুন দিকে নিয়ে যেতে পারে—সেসব নিয়ে টেইলরের সাথে কথা বলেছে স্টোরিবেঞ্চ।
প্রশ্ন: জলবায়ু পরিবর্তনকে এভাবে তুলে ধরার কথা কেন ভাবলেন?
ডেরেক টেইলর: জলবায়ু নিয়ে আমি যেসব প্রতিবেদন আর লেখা পড়েছি, সেগুলোর বেশিরভাগই ছিল জটিল বৈজ্ঞানিক শব্দে ভরা। আর এমন সব ডেটা পয়েন্ট দিয়ে তৈরি, যা সাধারণ পাঠকের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন। যদি বলা হয় সমুদ্রের গড় তাপমাত্রা বেড়েছে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস—কথাটা কিন্তু মানুষকে খুব একটা আলোড়িত করে না। তাই আমার কাছে অনেক কিছুই খুব বিমূর্ত মনে হচ্ছিল। অথচ বাস্তবে এর প্রভাব হতে পারে ভয়াবহ।
আমার চিন্তার শুরুটা হয়েছিল মূলত এ ভাবনা থেকে যে, শহরগুলোতে আমাদের কেমন লাগে। মানুষ কীভাবে জলবায়ুকে নয়, মূলত আবহাওয়াকেই অনুভব করে। আমি ভাবছিলাম ভবিষ্যতের আবহাওয়া ঠিক কতটা বদলাতে পারে, আর তাপমাত্রা পরিবর্তনের বিষয়টি বোঝানোর যুতসই উপায় কী হতে পারে। আমি তুলনামূলক পরিবর্তন নিয়েও চিন্তা করেছি। তাই নিউ ইয়র্ক শহর উষ্ণ হয়ে উঠবে—এভাবে না বলে বরং বললাম, ২০৭০ সালে নিউ ইয়র্ক শহরের মানুষ ২০২৩ সালের স্পেনের বার্সেলোনা শহরের মানুষের মতো বা তার চেয়ে খানিকটা বেশি গরম অনুভব করবে।

ডেরেক টেইলর একজন ডেটা সাংবাদিক ও জিআইএস বিশেষজ্ঞ। ছবি: টেইলরের সৌজন্যে
প্রশ্ন: জলবায়ু পরিবর্তন একটা বৈশ্বিক সংকট। ডেটা চিত্রায়নের মাধ্যমে তুলে ধরে এমন কী কিছু করা যায়, যা শুধু পরিসংখ্যান দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়?
ডি টি: আমি মনে করি, এটা ডেটার মতো খটোমটো বিষয়কে কিছুটা সহজ বা সাধারণ মানুষের কাছে বোধ্য করে তোলে। তাই সুর্নিদিষ্ট পরিসংখ্যান তুলে ধরার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবেই এখানে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছে। যদিও এখানে দেখতে পাবেন, ‘এক্স’ শহরের তাপমাত্রা পাঁচ ডিগ্রি ফারেনহাইট বেড়ে যাবে— সেটাই এই প্রতিবেদনের মূল বার্তা নয়। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—২০৭০ সালে শহরগুলোর তাপমাত্রার সঙ্গে এখনকার শহরগুলোর তাপমাত্রা তুলে ধরা। এর ফলে ভবিষ্যত ও বর্তমানের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পার্থক্যগুলো সহজেই তুলে ধরা যায়।
প্রশ্ন: জলবায়ু গবেষণার ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে করা শ্রেনি বিভাগ কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল?
ডি টি: আমি কিন্তু শুরুতেই এই ডেটাসেটটি খুঁজে পাই। এমনকি আবহাওয়া ও অনুভূতি নিয়ে ভাবার আগেই আমি এমন একটি ডেটাসেট হাতে পাই যেখানে বিভিন্ন শহরের ২০২৩ এবং ২০৭০ সালের পার্থক্যগুলো দেখানো ছিল। বৈশ্বিক এই ডেটাসেটটিতে শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী জলবায়ু এবং অঞ্চলগুলোও চিহ্নিত করা ছিল। ভীষণ আগ্রহ নিয়ে আমি তা দেখতে থাকি। কারণ আমার মনে হতে থাকে আমি যেখানে থাকি সেই স্যাক্রামেন্টোর তাপমাত্রা যদি ৯০ ডিগ্রি হয়, আবার বোস্টনের তাপমাত্রাও যদি ৯০ ডিগ্রি হয়, সেক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অনুভূত হতে পারে। কেননা বিষয়টা কেবল তাপমাত্রা নয়। জলবায়ুর এই শ্রেণিবিন্যাস অন্যান্য আরও কিছু বিষয়ও ব্যাখ্যার সুযোগ এনে দেয়। সুনির্দিষ্ট জায়গাগুলোতে একই তাপমাত্রা হলেও আমরা কেন ভিন্ন ভিন্ন আবহাওয়া অনুভব করবো।

ছবি: দ্য পুডিং-এর সৌজন্যে
প্রশ্ন: ডেটা চিত্রায়নের জন্য শহরগুলোকে কীভাবে বাছাই করেছেন?
ডি টি: প্রথম লক্ষ্য ছিল—বিভিন্ন জলবায়ু অঞ্চল থেকে সমভাবে শহর নির্বাচন। বাস্তবতা হলো, বিশ্বের বেশিরভাগ শহরই নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। কারণ মানুষের বসতি এ ধরনের জায়গায় গড়ে উঠেছে। আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল—প্রতিটি ভিন্ন শ্রেণিবিন্যাস থেকে এমন কিছু শহর বেছে নেওয়া, তুলনা করার সময় যেগুলো প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। দ্বিতীয়ত—এমন শহর বেছে নেওয়া, মানুষের মানসপটে যার ছবি আছে। কেউ হয়তো নিজে কখনও নয়া দিল্লি যাননি, কিন্তু নয়া দিল্লির কোনো না কোনো ছবি নিশ্চয়ই দেখেছেন। ফলে যখন বলা হবে, ২০৭০ সালে লস অ্যাঞ্জেলেসের জলবায়ু হবে অনেকটা নয়া দিল্লির মতো, তখন এই তুলনাটা মানুষের মনে একটি দৃশ্যপট তৈরি করে।
প্রশ্ন: আপনি এই ডেটানির্ভর গল্পটি তৈরির জন্য কোন কোডিং টুল ব্যবহার করেছেন এবং প্রক্রিয়াগুলো কেমন ছিল?
সব ধরনের ডেটা বাছাই ও প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে পাইথন (Python) বা পোস্টগ্রেস (Postgres) ব্যবহার করে। তবে এই প্রকল্পের ডেটা সম্পর্কিত অংশটা ছিল সবচেয়ে সহজ। আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই ডেটাসেট প্রস্তুত করে, বাছাই করে তা সাজিয়ে ফেলেছিলাম। সবচেয়ে বড় পরিশ্রমের জায়গা ছিল ভিজ্যুয়ালাইজেশন টুল এবং গল্প নির্মাণ। দ্য পুডিংয়ে ব্যবহার করা হয় স্ভেল্ট (Svelte) নামের একটি জাভাস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরি। ওয়েবসাইটের ফ্রন্টএন্ডটাই তৈরি হয়েছে জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে, বিশেষ করে স্ভেল্ট ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে।
প্রশ্ন: আমি দেখেছি, আপনি এর আগে আফ্রিকা নিয়ে একই ধরনের প্রকল্পে কাজ করেছিলেন। এ কাজটি কী ক্লাইমেট জোনসের কাঠামো তৈরিতে সাহায্য করেছে? শেষমেশ আপনি কতটা সম্পাদনা বা পরিবর্তন করেছেন?
ডি টি: আমি আমার ওই কাজটিই পিচ হিসেবে দ্য পুডিংয়ে জমা দিই। অনেকটা আমার ধারণার প্রমাণ হিসেবে। তখন আমি থ্রিডিতে আফ্রিকার মানচিত্র তৈরি করেছিলাম। মানচিত্রের ওপরে একটি ডেটাসেট বসানো ছিল। তারপর ভাবলাম, এর ওপর আরেকটি ভিন্ন ডেটাসেট বসিয়ে দেখলে কেমন হয়।
প্রথমে বড় স্বপ্ন নিয়ে কাজ শুরু করি—প্রতিটি মহাদেশ নিয়ে একটি করে ডেটা-নির্ভর প্রতিবেদন করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পরি, এটা অনেক বড় একটা কাজ হয়ে যাবে। যা একা সামলানো কঠিন। সেই কারণে পুরো ধারণাটাকে একটু ছোট করে, সীমিত করে ফেলতে হয়েছে।
ছবি: দ্য পুডিং-এর সৌজন্যে
প্রশ্ন: কাজটিতে ডেটা সায়েন্স প্রসঙ্গে আপনার মধ্যে নতুন কী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে?
ডি টি: খুব বাস্তব ও ব্যবহারিকভাবে বলতে গেলে, এখন আমি প্রতিদিন স্ভেল্ট (Svelte) ব্যবহার করি। অনেক বেশি ওয়েবসাইটের দৃশ্যমান অংশ তৈরি আর ডেটা চিত্রায়নের কাজ করি, যা আমার অনেক উপকারে এসেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ছিল—গল্পটিকে যতটা সম্ভব সহজভাবে উপস্থাপন করা এবং প্রতিটি ধাপে নিজেকে প্রশ্ন করা: পাঠক এই গল্প থেকে মূলত কী জানবে বা কী মনে রাখবে। কোন বিষয়গুলো ভিজ্যুয়ালাইজ করতে হবে এবং কীভাবে তা করতে হবে—একটু পেছনে গিয়ে ভাবলে আপনার কাছে অনেক কিছুই পরিষ্কার হয়ে উঠবে। শেষ পর্যন্ত আপনাকে এমন একটা প্রকল্প দাঁড় করাতে হবে যা প্রযুক্তিগতভাবে শক্তিশালী, একইসাথে যেখানে অকেজো চটকদার উপাদানের উপস্থিতি নেই।
প্রশ্ন: প্রকল্পটির মাধ্যমে আপনি সাধারণ মানুষকে কী বোঝাতে চেয়েছেন?
ডি টি: আমার প্রত্যাশা—পাঠকরা যেন জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পান, যা আরও বাস্তবিকভাবে তাদের কাছে পৌঁছায় এবং জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিবেদন পড়ার তুলনায় এটি যেন তাদের মনে আরো বেশি দাগ কাটতে সমর্থ হয়।
সম্পাদকীয় নোট: এই সাক্ষাৎকারটি প্রথম প্রকাশিত হয় নর্থইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের ওয়েবসাইট স্টোরি বেঞ্চে। তাদের অনুমতি নিয়ে এখানে পুনঃপ্রকাশিত হলো।
 ড্যারিন জুলো নর্থইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী; সাংবাদিকতা ও ইংরেজিতে মেজর এবং ফটোজার্নালিজমে মাইনর করছেন। বর্তমানে তিনি বোস্টনডটকম-এর কো-অপ কর্মসূচির অধীনে সাধারণ প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করছেন। এর আগে তিনি দ্য নিউজের ডেপুটি লাইফস্টাইল এডিটর এবং ডেপুটি ফটো এডিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
ড্যারিন জুলো নর্থইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী; সাংবাদিকতা ও ইংরেজিতে মেজর এবং ফটোজার্নালিজমে মাইনর করছেন। বর্তমানে তিনি বোস্টনডটকম-এর কো-অপ কর্মসূচির অধীনে সাধারণ প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করছেন। এর আগে তিনি দ্য নিউজের ডেপুটি লাইফস্টাইল এডিটর এবং ডেপুটি ফটো এডিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।