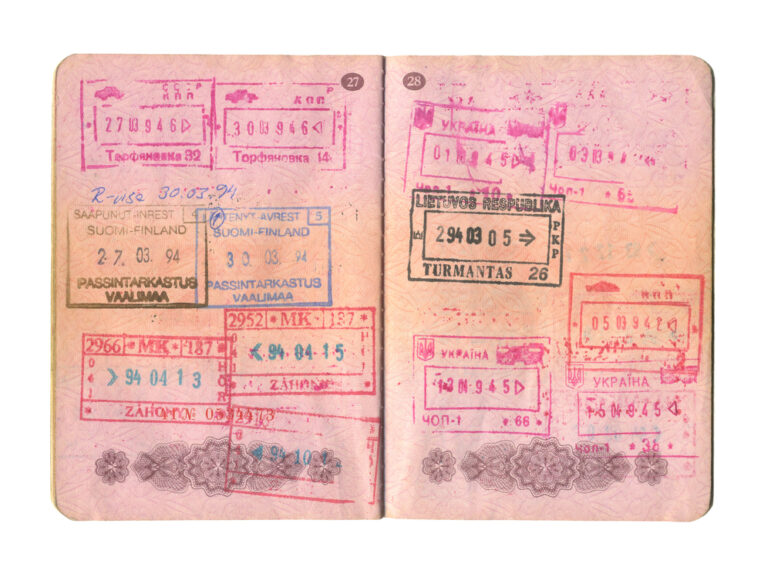আসছে “ডিপ ফেইক” ভিডিওর জোয়ার, মোকাবেলা করবেন কীভাবে?
“ডিপ ফেইক” শব্দটি নিয়ে কথাবার্তা সম্ভবত এরইমধ্যে আপনার কানেও কিছুটা গেছে। অভিনব এই প্রযুক্তি সাম্প্রতিক সময়ে, “আমরা সত্যিই ফ**ড্ ” এবং “ডিপ ফেইক: জাতীয় নিরাপত্তা, গণতন্ত্র এবং গোপনীয়তার জন্য ক্রমবর্ধমান সংকট,” এমন শিরোনামের লেখা জন্ম দিয়েছে।
ডিপ ফেইক ভিডিওতে একজনের মুখ অন্যের শরীরে বসিয়ে দেয়া হয়। যদিও তত্ত্বটি নতুন নয়, কিন্তু হালের ডিপ ফেইক আশ্চর্যরকমের বিশ্বাসযোগ্য। এমন ভিডিও তৈরির যে সফটওয়্যার, তার ব্যবহারও বাড়ছে দ্রুত গতিতে, যা উপরের মত শিরোনামকে উৎসাহিত করছে।
কিছুদিন আগে একটি ভিডিও ব্যাপক আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ভুয়া খবর সম্পর্কে একটি পাবলিক সার্ভিস এনাউন্সমেন্ট বা জনসচেতনতামূলক ঘোষণা দিচ্ছেন। বার্তাটি আসলে চলচ্চিত্র নির্মাতা জর্ডান পিল-এর, শুধু সেখানে ওবামার মুখ বসিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু ভিডিওটি দেখতে একদম বাস্তব মনে হয়।
.
সম্প্রতি সাউথ বাই সাউথ ওয়েস্ট সম্মেলনের একটি প্যানেলে বক্তারা যেমনটা বলেছেন, স্থির চিত্রের তুলনায় মানব মনের অনেক গভীরে পৌঁছাতে পারে ভিডিও, তাই এর প্রভাবও হতে পারে অনেক বিস্তৃত।
ফেইকঅ্যাপ (FakeApp) এর মত ভুয়া ভিডিও তৈরির সরঞ্জাম এখনই সহজলভ্য। অচিরেই বাজারে আসবে অডিও ম্যানিপুলেশন, অর্থ্যাৎ শব্দ নিয়ে কারসাজির টুল। সিএনএন সোশ্যাল ডিসকভারি টিমের প্রযোজক ডনি ও’ সুলিভান বলছেন, এই অডিও টুল সম্ভবত পরিস্থিতিকে আরও বিপজ্জনক করে তুলবে।
“কোনও ব্যক্তি যে কথা বলেননি, তার কন্ঠে সে কথার বিশ্বাসযোগ্য অডিও যদি আপনি তৈরি করতে পারেন এবং তা পোস্ট করেন,” ও’সুলিভান জিআইজেএনকে বলেন, “তখন সেটা যাচাই করা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।”
ডিপফেইক অর্থ্যাৎ বিকৃত ভিডিও তৈরির প্রযুক্তি এতই নতুন যে, তার নাগাল পেতে, ভুয়া তথ্য যাচাইকারী সংগঠনগুলোকে রীতিমত হিমসিম খেতে হচ্ছে, বলেছেন বেলিংক্যাটের মুখ্য গবেষক এবং প্রশিক্ষক আরিক টোলার।
অবশ্য তার মানে এই নয় যে, চেষ্টার কমতি আছে।
ডিপ ফেইক ঠেকানোর উদ্যোগ যেদিকে যাচ্ছে
ডিপ ফেইক ভিডিও সনাক্ত করার মত টুল এখনও অস্তিত্বহীন বলা চলে। তবে অ্যাকাডেমিক, সাংবাদিক এবং প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গুগল ঘোষণা দিয়েছে, তারা অলটার্ড বা বিকৃত করা ভিডিও সনাক্তের জন্য একটি টুল তৈরি করছে। কিন্তু বলা হয়নি, সেটি কবে আসবে বা তার ক্ষমতা কী হবে।
মিউনিখের ভিজ্যুয়াল কম্পিউটিং ল্যাবের একটি দল তৈরি করেছে ফেস ফরেনসিকস্। প্রোগ্রামটি র’-ফরম্যাট (যে ফরম্যাটে ধারন করা) ফাইল থেকে ভিডিওর বিকৃতি সনাক্ত করতে পারে। তবে ওয়েবের জন্য সংকুচিত বা কমপ্রেস করা ভিডিওর বেলায় তারা সফল হননি।
ইতালির আরেকটি দল, এমন এক কৌশল প্রস্তাব করেছেন, যেখানে ভিডিওতে কোনও ব্যক্তির মুখমন্ডলে রক্ত প্রবাহে অনিয়ম দেখে বলে দেয়া যাবে, ছবির চেহারাটি আসল, নাকি কম্পিউটার জেনারেটেড।
.
বিড়াল এবং সেলিব্রিটিদের মজার GIF ছবি হোস্টিংয়ের জন্য পরিচিত ওয়েবসাইট, জিফিক্যাট (Gfycat)। ভুয়া ভিডিও সনাক্ত করার ক্ষেত্রে তাদের পদ্ধতিটিই সম্ভবত এখন পর্যন্ত সবচেয়ে উন্নত। নিজেদের সাইটে ডিপ ফেইক ভিডিও খুঁজতে, তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স টুল ব্যবহার করছে, যা সম্প্রতি উঠে এসেছে Wired সাময়িকীতে। তাদের একটি টুল, ভিডিও থেকে মুখ বাদ দিয়ে শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড মিলিয়ে দেখে অন্য ভিডিওর সাথে। আরেকটি টুল, কোথাও কোন সেলিব্রিটির ভালো মানের ভিডিও পেলে, নিম্ন মানের ভিডিওটিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে। যুক্তি হলো, একই ভিডিও দুই মানের পাওয়া গেলে, সম্ভবত নিম্নমানেরটি ডিপ ফেইক। প্রতিকারের এগুলোই যে সেরা অস্ত্র, তা নয়। কিন্তু প্রযুক্তির মাধ্যমে ভুয়া ভিডিও সনাক্ত করার অন্যতম উপায় তো বটেই।
অবশ্য এসব টুল শুধু অভ্যন্তরীণ কাজে ব্যবহার করছে জিফিক্যাট। তাদেরকে সবার জন্য উন্মুক্ত করার কোন ঘোষণা আসেনি প্রতিষ্ঠানটি থেকে।
আর মিউনিখের দলটি গিটহাব-এ তাদের স্ক্রিপ্ট প্রকাশ করেছে। কিন্তু সেই ডেটাসেট শুধু তাদের সাথে শেয়ার করা হবে, যারা একটি নির্দিষ্ট ব্যবহারবিধিতে স্বাক্ষর করবেন।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষতিকর ব্যবহার নিয়ে এক সাম্প্রতিক গবেষণায়, ডিপ ফেইক ভিডিও তৈরির সফটওয়্যার লাইসেন্সিংয়ের আওতায় আনা এবং তার ব্যবহার সীমিত করার প্রস্তাব দিয়েছেন একদল গবেষক। ইলেক্ট্রনিক ফ্রন্টিয়ার ফাউন্ডেশন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং অন্য সদস্যদের নিয়ে গঠিত দলটি শুধু তাত্ত্বিক দিকে মনোযোগ দিয়েছে; মূলত বিষয়বস্তুর নতুনত্বের কারণে।
মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল ভেরিপিক্সেল নামে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করছে, যা ব্লকচেইন প্রযুক্তির মাধ্যমে স্মার্টফোন ও ক্যামেরায় তোলা ছবির মূল ফাইলে একটি ‘ফুটপ্রিন্ট’ বা চিহ্ন জুড়ে দেয়।
ডেভেলপারদের একজন উইলিয়াম ফ্রাইস জিআইজেএনকে বলেন, “আপনার এমন একটি পদ্ধতি দরকার যা বলবে, হ্যাঁ, এটাই আসল ফাইল। ব্লকচেইনের সুবিধা হল, যাই ঘটুক না কেন, ফাইলের ঐতিহাসিক তথ্য ঠিক থাকে।”
কিন্তু অন্যান্য প্রোগ্রামের মত ভেরিপিক্সেল এখনও নির্মানাধীন পর্যায়ে রয়েছে।
আর এই সময়ে সাংবাদিকরা বরাবরের মতই ভরসা রেখেছেন, ক্রিটিকাল থিংকিং বা যুক্তিনির্ভর চিন্তাশীলতায়। ব্যাকগ্রাউন্ড তথ্য ও যাচাইযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রথাগত কৌশল – ডিপ ফেইক হোক বা না হোক – সন্দেহজনক উৎস যাচাই করার জন্য এগুলোই সবচেয়ে ভালো উপায়।
যতক্ষণ না কোনও ভালো টুল আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত, ডিপ ফেইকের মুখোমুখি হলে সাংবাদিকরা যেসব পদক্ষেপ নিতে পারেন:
সাধারণ অসংগতি খেয়াল করুন
১. মুখভঙ্গি এবং নড়াচড়া দেখুন
ডিপ ফেইক ভিডিও এখনও মানুষের “চোখের পরীক্ষায়” পাস করার মত যথেষ্ট নিখুঁত হতে পারেনি। এই মুহূর্তে, এটাই সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধা, বলছিলেন বেলিংক্যাটের টোলার ।
যেহেতু ডিপ ফেইকের সারমর্মই হচ্ছে, একজনের মুখ আরেক জনের শরীরে বসিয়ে দেয়া, তাই যে কোনও অসামঞ্জস্য খুঁজে বের করতে মুখের চারপাশটা ভালো করে দেখা জরুরী। সেখানটায় আলো বা ছায়া কী একটু অন্যরকম? মুখ, চিবুক বা চোয়ালের নড়াচড়া কেমন? মানুষের মতই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে?
এমন ভিডিওর নির্মাতারা এখনো চুলের নড়াচড়া পুরোপুরি নকল করতে পারেনি, জিআইজেএনকে বলেন বাজফিডের সিনিয়র প্রযুক্তি প্রতিবেদক চার্লি ওয়ারজেল। তিনি অস্বাভাবিকতা খুঁজে পেতে চুল এবং চেহারার দিকে নজর দিতে বলেন।
ডিপ ফেইক ভিডিওর মুখভঙ্গি থেকে অসঙ্গতি চিহ্নিত করার কিছু কৌশল বাতলে দেয়, “হাউ টু গিক” এর এই নিবন্ধ। সেখানে যে দিকে নজর দিতে বলা হয়েছে:
ফ্লিকার (ভিডিওতে আলোর কম্পন বা ঝিলিক) চেহারা বা মুখের দিকটায় অস্পষ্টতা (ব্লার) অস্বাভাবিক ছায়া বা আলো অস্বাভাবিক নড়াচড়া, বিশেষ করে মুখ, চোয়াল এবং ভ্রুতে ত্বকের রঙ এবং শরীরের গড়নে অসামঞ্জস্য কথার সাথে মুখের নড়াচড়ায় অমিল
২. দেখুন ফ্রেম ধরে ধরে
ওয়ারজেল একটি ভিডিওকে ধীর গতিতে অথবা থামিয়ে থামিয়ে কয়েকবার দেখার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, এটি অসামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়।
.
যেমন, বাজফিডে ওবামার সেই নকল ভিডিও, অর্ধেক গতিতে চালিয়ে দেখলে মুখ এবং চিবুকের চারপাশে অস্পষ্টতা চোখে পড়বে। কথা বলার সময় ওবামার মুখ যেভাবে এপাশ ওপাশ নড়ছিল, তা সত্যিকারের মানুষের ক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায় না।
এছাড়া, ফ্রেম ধরে ধরে ক্লিপটি দেখার পরামর্শ দিয়েছেন ওয়ারজেল – বার বার থামিয়ে অথবা ফাইনাল কাট-এর মত ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যারে নামিয়ে।
সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন
১. দেখুন কারা-কীভাবে শেয়ার করছে
যদি ভিডিওটি কারিগরী দিক দিয়ে উৎরে যায়, ও’সুলিভান বলেন, তাহলে অনলাইন থেকে এর অন্যান্য সংস্করণ খুঁজে বের করুন। আর দশটা সন্দেহজনক ভিডিও সাংবাদিকরা যেভাবে যাচাই করেন, ডিপ ফেইকের ক্ষেত্রেও একই কৌশল ব্যবহার করতে পারেন।
উৎস খুঁজে বের করুন – ভিডিওটি কাদের ধারণ করা? কারা ওয়েবে প্রকাশ করেছে? এটা শেয়ার করা হয়েছে কার কার সাথে? একই ব্যক্তি কি বার বার শেয়ার করেছে নাকি অনেকে?
ওয়ারজেল বলেন, “ভিডিওটি যে নিছক কোনও ব্যক্তির সংগ্রহ বা শেয়ার করা খবর নয়, বরং একটি সমন্বিত প্রচার অভিযানের অংশ, অনেক সময় এখান থেকেই তা বোঝা যায়।”
২. অন্য ভিডিওর সঙ্গে মুখভঙ্গি মেলান
ওয়ারজেল বলেন, সৌভাগ্যক্রমে, এখনও ডিপ ফেইক ভিডিও তৈরি হচ্ছে, মূলত সেলিব্রিটি বা জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের নিয়ে। মুখভঙ্গি মেলানোর জন্য তাদের অন্য ভিডিও খুঁজে পাওয়া সহজ। মনে রাখবেন, অনেক সময় দাঁতের মত ক্ষুদ্র জিনিসও, জালিয়াতি ধরার জন্য যথেষ্ট।
ভিডিওর পটভূমি জানুন
জিআইজেএন এর ভিডিও যাচাই নির্দেশিকায় অনুসন্ধানের বেশ কিছু পদ্ধতি রয়েছে। যেমন:
১. ইউটিউব ডেটা ভিউয়ার বা ইনভিড
ইউটিউব ডেটা ভিউয়ার আপনাকে জানাবে ভিডিওটি কোন সময় আপলোড করা হয়েছে। দেখাবে ইউটিউবের তৈরি করা থাম্বনেইলও (ভিডিওরে বিভিন্ন অংশ থেকে নেয়া ছোট ছোট স্থিরচিত্র)। আরেক বিকল্প ইনভিড (inVid) ভিডিও এবং ছবি, দুটোতেই কাজ করে।
.
এই ক্লিপে দাবি করা হয়েছে, এটি হারিকেন হার্ভে চলাকালীন সময়ে কারো বাড়ীর ড্রাইভওয়ের টাইমল্যাপস (সময়-সংকোচন করা) ভিডিও। সেখানে একটি তারিখও দেয়া হয়েছে: “আগস্ট ২৭, ২০১৭।” ডেটা ভিউয়ার বলছে, ক্লিপটি ওই বছর ৩১ আগস্ট তারিখে আপলোড করা হয়েছে। আবার বিভিন্ন খবর-সূত্র অনুযায়ী, ঘূর্ণিঝড় হার্ভে আগস্টের শেষ দিকেই আঘাত হেনেছে। অর্থাৎ, আপলোডার যা দাবি করেছেন, তা ভুল প্রমাণ করার মত কিছু পাওয়া যায়নি।
যদি সোর্স দাবি করে ভিডিওটি গত সপ্তাহের কোনও ঘটনার, কিন্তু দেখা যায়, সেটি ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছে কয়েক বছর আগে, তা হলে আপনি উত্তর পেয়ে গেছেন। সেরকম না হলে, পরবর্তী পরীক্ষায় যেতে পারেন।
২. ছবি দিয়ে ছবি খোঁজা
ডেটা ভিউয়ার আপনাকে এমন একটি টুলের লিঙ্ক দেবে, যার নাম রিভার্স ইমেজ সার্চ। এটি লিখিত শব্দের বদলে ছবি দিয়ে গুগলে অনুসন্ধান চালিয়ে, ছবি খুঁজে বের করে।
বন্যার ভিডিওর থাম্বনেইল দিয়ে রিভার্স ইমেজ সার্চ করে, শিকাগো ট্রিবিউন এবং হিউস্টন ক্রনিকলের খবর পাওয়া যায় – দুটোই মায়ারল্যান্ড এলাকার বন্যা সম্পর্কে। এই দুটি ডেটা পয়েন্টও আমাদের ভিডিওর সাথে মেলে। তার মানে, এ পর্যন্ত সবই ঠিক আছে।
৩. গুগল করুন
বোকার মত শোনাতে পারে, কিন্তু শুরু করুন গোড়া থেকে – গুগল সার্চের মাধ্যমে – যা দারুণ ফলাফল এনে দিতে পারে আপনাকে। যেমনটা টোলার বলেছেন, ভিডিও যাচাই নিয়ে এই লেখায়। সেখানেে একটি ভিডিওর উদাহরণ দেয়া হয়, যাতে একটি গাড়ীর বহর দেখিয়ে বলা হচ্ছিলো, সেটি লিথুয়ানিয়ায় সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গুগলে “প্রশিক্ষণ” এবং “রাত” শব্দ দিয়ে সার্চ করে দেখা গেল, একইরকম ছবি বেরিয়ে এসেছে। তখন (সামরিক সরঞ্জামের বহর দাবি করা) সেই ভিডিও নিয়ে সন্দেহ দেখা দিল।
হারিকেন হার্ভের সেই টাইমল্যাপসের ক্ষেত্রে, “হার্ভে”, “বন্যা,” “ড্রাইভওয়ে,” “টাইমস্টপ” এবং “টাইমল্যাপস” এর মত শব্দ দিয়ে গুগলে অনুসন্ধান চালালেও একই কাজ হবে। ইউটিউব, ভিমিও এবং জিফিক্যাটের মতো ভিডিও রিপোজিটরিগুলোও চেক করে দেখতে পারেন।
৪. গুগল স্ট্রিট ভিউ
বেশীরভাগ ডিপ ফেইকে, একজন ব্যক্তির কথা বলার দৃশ্য দেখানো হয়। সুতরাং সেখানে কোনও স্বতন্ত্র ব্যাকগ্রাউন্ড না-ও থাকতে পারে। তবুও ব্যাকগ্রাউন্ড বা লোকেশন, ক্রস-চেক করে নিতে পারেন গুগল স্ট্রিট ভিউ নামের টুল দিয়ে।
বন্যার ফুটেজের আপলোডার, “মায়ারল্যান্ড” এলাকার কথা বলেছেন। আমরা গুগল করে পেয়েছি, সেটি দক্ষিণ-পশ্চিম হিউস্টনে। গুগল ম্যাপে মায়ারল্যান্ড খুলুন এবং যেই রাস্তায় যেতে চান সেখানে, ম্যাপের কমলা রঙের মানুষটিকে (ডান দিকে, নীচে থাকা একটি আইকন) টেনে এনে বসিয়ে দিন। তাকে যেখানে বসাবেন, সেখানকার রাস্তার দৃশ্য দেখতে পাবেন।
এই ক্ষেত্রে আমরা হালকা ধূসর পেভমেন্ট, ঘাস ছাঁটা লন এবং সাইডওয়াক ও রাস্তার মধ্যে ঘাসের সরু ফালি দেখতে পাই। যা আপলোডারের বক্তব্যকে সমর্থন করে।
রাস্তার দৃশ্য মিলে যাওয়া মানেই ভিডিওটি খাঁটি, তা নয়। তবে ভিডিওটি মিথ্যা কিনা তা যাচাইয়ের এটি আরেকটি উপায়। আপনি গুগল আর্থ দিয়ে একই পরীক্ষা করে দেখতে পারেন – অঞ্চলটি পাহাড়ী, ঘাসে ঢাকা, অথবা সমতল কিনা।
৫. ভিডিও মেটাডেটা
আপনি হয়তো EXIF তথ্য সম্পর্কে জানেন। এই মেটাডেটা ছবির অবস্থান, ক্যামেরার ধরণ এবং অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করে। ভিডিওর ক্ষেত্রে একই তথ্য পেতে, আগে ক্লিপটি কম্পিউটারে ডাউনলোড করে, তারপর Exiftool দিয়ে চালান। এই পরামর্শ দিয়েছেন, পয়েন্টার ইনস্টিটিউটের ফ্যাক্ট-চেকিং প্রতিবেদক ড্যানিয়েল ফাঙ্কে।
কিন্তু, সব মেটাডেটার বেলায়ই, আপনাকে সতর্ক হতে হবে: কারণ ক্লিপটি সম্পাদনা বা ঘষামাজা হয়ে থাকতে পারে। হতে পারে অন্য ভিডিওর রেকর্ডিংও। কিন্তু এই সব টুল দিয়ে আমরা তালিকা ধরে, ভিডিওর একেকটি ফ্যাক্টর যাচাই করতে পারি।
ভিডিও যাচাইয়ের আরও টিপসের জন্য: জিআইজেএনের ভিডিও যাচাই অ্যাডভান্সড গাইড এবং ফার্স্ট ড্রাফট নিউজ গাইড দেখুন।
সামান্থা সান, থাকেন লুইসিয়ানার নিউ অরলিনসে, কাজ করেন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে। মূলত ডেটা এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তার আগ্রহ। তিনি সারা বিশ্ব জুড়ে সাংবাদিকদের ডিজিটাল টুলস সম্পর্কে শিক্ষা দেন এবং ‘টুলস্ ফর রিপোর্টার্স’ নামে একটি নিউজলেটার প্রকাশ করেন।